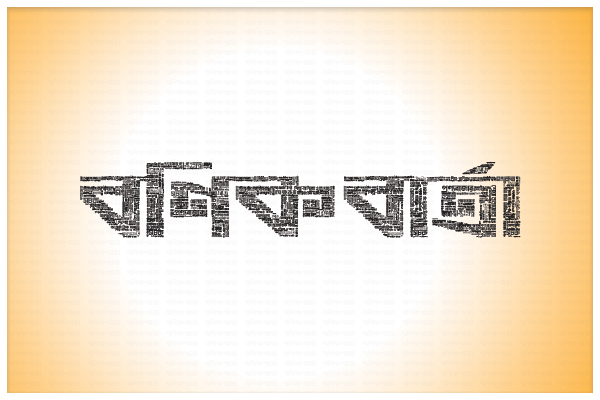ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা বর্তমান সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা, রিজার্ভের অবস্থা, বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতার অবস্থা ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিস্থিতি—সবকিছুকে সামনে রেখেই ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটটি করা হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এর চেয়ে বড় বাজেট সম্ভব ছিল না।
দেশে বর্তমানে দুটি মূল সমস্যা বিদ্যমান। একটি হলো, দেশের রিজার্ভ সংকট কাটছে না। আরেকটি হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি বাড়তি অবস্থায় স্থিতিশীল রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে স্বীকার করেই বাজেটটি করা হয়েছে।
আমরা কভিড সংকট ভালোভাবেই মোকাবেলা করেছি। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্ব মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেল। তেল, খাদ্যপণ্যসহ সব পণ্যের মূল্য বেড়ে গেল। আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ল। ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতির চক্রে পতিত হলো। আমরা এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম না। এরপর থেকেই ক্রমান্বয়ে রিজার্ভ কমছিল। রিজার্ভ কমে আসার ফলে সরকার এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় চেষ্টা করেছে। যার কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিভিন্ন শর্ত মেনে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ চুক্তি করেছে সরকার। এ ঋণের মাধ্যমে সরকার চেয়েছিল আর্থিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে সক্রিয় রাখতে। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা এবং ডলারের সঙ্গে টাকার অবমূল্যায়ন করতে হলো। টাকার অবমূল্যায়ন মূল্যস্ফীতিতে যুক্ত হলো। অর্থাৎ টাকার অবমূল্যায়নের কারণে আমদানীকৃত পণ্যের দাম এমনিতেই বেড়ে যায়। সাধারণত মূল্যস্ফীতি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মূল্যস্ফীতির ধরন চাহিদা তাড়িত ছিল না। চাহিদার কারণে মানুষ বেশি ক্রয় করছে বা শিল্পায়নের জন্য শিল্পপতিরা বেশি ক্রয় করছে—সেটা নয়। এ সময়ে চাহিদা তো বাড়েইনি, বরং মূল্যস্ফীতির কারণে ভোগ কমে গেল। আবার সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় দেশে বিনিয়োগ কমে গেল।
বাজেট তো হয় এক বছরের জন্য। চাইলেই তো সবকিছু এক বছরের মধ্যে সামাল দিতে পারা যায় না। কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়া মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করা সম্ভব না। শিল্প, কৃষি ও সেবা—এ তিন খাতেই উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ কমাতে পারলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
প্রথাগতভাবে যে পদ্ধতিগুলো নেয়া হয়েছিল আমদানি নিয়ন্ত্রণে সেখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি আরো বেড়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্ষয় ঠেকাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক উৎপাদন উপকরণ ব্যয়ও বেড়ে গেল। এছাড়া মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কিছুটা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে উৎপাদনও ব্যাহত হয়েছে। সব মিলিয়ে বাজেটে উৎপাদন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি—অনেকগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে বা কমানোর কথা বলা হয়েছে। কৃষি উপকরণেও আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়, আমদানি শুল্ক কমানোয় শিল্পায়নে কিছুটা সহায়তা করবে। কারণ অনেকগুলো ক্ষেত্রেই আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
অর্থমন্ত্রী গাড়ি আমদানিতে সংসদ সদস্যদের যে আইনের মাধ্যমে শুল্ক সুবিধা দেয়া হচ্ছিল সেই আইনটি পুনর্বিবেচনা করে আইনটি বিবেচনার কথা বলেছেন। যাতে আবার পুনরায় শুল্ক আরোপ করা যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন কিনা জানি না, তবে এটি বাস্তবায়ন করা উচিত। এটি এ বাজেটের ভালো একটি দিক। অর্থমন্ত্রী এ বিষয় অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।
সরকারের আলু ক্রয় ও বিক্রয় করা উচিত নয়। আলু একটি পচনশীল পণ্য এবং এর বিকল্প পণ্য রয়েছে। কারণ এটি ব্যক্তি খাতে উৎপন্ন হয় এবং ব্যক্তি খাতে সরবরাহ করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকারের উচিত হবে বাজারে যাতে সিন্ডিকেট তৈরি না হয় এবং মূল্যকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে সেদিকে সরকারের নজর রাখা। তবে এ খাতে বরাদ্দ কমলেও তাতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। গম ও চাল খাদ্যপণ্য ও মৌলিক পণ্য। এ পণ্যের কোনো বিকল্প পণ্য নেই। যেহেতু দেশে দুর্যোগ, বিশেষ করে বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয় তাই এ দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারকে শুধু খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ দুর্যোগে জাতিকে খাবার দিতে হবে। তাই সরকারকে এ খাদ্যপণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে এটুকু সরকারের করা উচিত। এছাড়া ব্যক্তি খাতে যারা এসব পণ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ করতে চায় তাদেরও সরকারের সহায়তা করা উচিত।
উৎপাদনের পাশাপাশি কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতে কৃষকদের সহায়তা করা উচিত। সেচ ব্যবস্থাপনা, সার ও বীজের ক্ষেত্রে কৃষকের খরচ যেন কমিয়ে আনা যায় সে ব্যবস্থা করা উচিত। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ ও কৃষকদের প্রশিক্ষণে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া সরকারের কাজ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের নীতি সরকার বাস্তবায়ন করতেও পারে না। সেদিকে না গিয়ে উৎপাদন উপকরণ কীভাবে সাশ্রয়ে সরবরাহ করা যায়, আমদানি ব্যয় কীভাবে কমানো যায়, উন্নত প্রযুক্তি আনা যায় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। কৃষিতে উৎপাদন বাড়াতে দক্ষতানির্ভর ও প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে। জমি বাড়িয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নেই। বরং আমাদের জমি দিন দিন কমছে। দ্রুত মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।
আমাদের অর্থনীতির সংকটের মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে। রফতানি আয়ে বৈচিত্র্য ও রফতানি আয় বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ছাড়া তো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় না। এবার যেহেতু ছোট বা মধ্যম মানের বাজেট হচ্ছে, তাই সরকারি বিনিয়োগ সহসাই বাড়ানো যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ উজ্জীবিত করা ছাড়া তো কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। বেসরকারি বিনিয়োগ উজ্জীবিত করতে হলে সুদের হার যাতে নেমে আসে সে ব্যবস্থা করতে হবে। সুদের হার কমিয়ে আনতে আমাদের পলিসি রেট নিয়ে চিন্তা করতে হবে। মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়ানো ও ব্যয় কমানো জরুরি। নীতি সুদহার যাতে আর না বাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। উচ্চ সুদে বিনিয়োগ করে মুনাফা করা কঠিন। উচ্চ সুদহারে বিনিয়োগ স্তিমিত হয়ে যাবে এবং এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে না। আর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকার তো সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে না। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে হবে, ভালো প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে। কারিগরি শিক্ষা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের উচিত কারিগরি শিক্ষার প্রসারে বেসরকারিও খাতকে উৎসাহিত করা।
কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য এ বাজেটে সরাসরি কোনো বরাদ্দ বা মনোযোগ নেই। অবশ্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের বড় কিছু করার থাকে না। আমাদের ৮২ শতাংশের মতো কর্মসংস্থান কিন্তু বেসরকারি খাতে। বেসরকারি খাত যদি পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে বিদ্যমান সংকট যেমন বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব বাড়বে—এটাই স্বাভাবিক। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ ও প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকর্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমানে দেশের বাজারে যাদের বিনিয়োগ আছে তারা যাতে মুনাফা নিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু রিজার্ভ সংকটের কারণে এক্ষেত্রে আমরা জটিলতার মধ্যে আছি। ভৌত অবকাঠামো নিয়ে আমাদের উদ্বেগের দিন শেষ হয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ সন্তোষজনক, ওয়ান-স্টপ সার্ভিস চালু হয়েছে। কিন্তু আমরা নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারছি না। এখন যারা বিনিয়োগ করছেন তারা পুরনো বিনিয়োগকারী এবং সাধারণত পুনর্বিনিয়োগ করছেন। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা যে অভিযোগ করছেন সেটা হলো অর্জিত মুনাফা তুলে নিতে পারছেন না। বিনিয়োগ আকর্ষণের বিষয়গুলো হয়তো সরাসরি বাজেটে থাকে না কিন্তু নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।
এখন সবাই একমত, মূল্যস্ফীতি কমানো দরকার। সরকার যেমন চায় তেমনি বেসরকারি খাতও চায়। আশা করা যায়, কয়েক মাসের মধ্যে মূল্যস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসবে। কারণ আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং সূচক বেড়েছে, কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে বোরোর ভালো ফলন হয়েছে। এটা যদি অব্যাহত থাকে আশা করা যায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে আসবে। এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যেখানে কৃষিপণ্যের ঘাটতি প্রতীয়মান হয় সেখানে যেন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হয়, যাতে বাজারে দাম বেড়ে না যায়। সহজে আমদানির সুযোগ দিতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের চেয়ে কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স ২ বিলিয়ন ডলার বেশি পেয়েছি। একই চিত্র দেখতে পাই রফতানির ক্ষেত্রে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের রফতানি হয়েছে ৪৫ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মে মাস নাগাদ রফতানি হয়েছে ৪৭ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার। এখানেও কিন্তু আমাদের আয় প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। আমরা গত অর্থবছরের চেয়ে আমদানি ব্যয় কমিয়েছি প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার। সাময়িকভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণমূলক ঠিক হলেও এখন আমাদের এর থেকে বের হয়ে আসা উচিত। এখন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি করতে দেয়া উচিত। আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে যাতে আবার ব্যয় বাড়িয়ে না দিই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির দিকে কিন্তু মনোযোগ বাড়াতে হবে। ক্রমান্বয়ে যদি বিনিয়োগ কমে যায় তাহলে কর্মসংস্থানের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। এতে বড় একটা শ্রেণী বেকার ও ছদ্ম বেকার হয়ে যাবে।
গত ২৯ মের সর্বশেষ উপাত্তে দেখা গেছে, আইএমএফের হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৮ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার। সরকারি হিসাবে ২৩ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। আমি মনে করি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল হয়ে আসবে। তবে রিজার্ভ হ্রাসের মূল কারণটা ধরতে হবে। রিজার্ভ হ্রাসের মূল কারণ বিদেশে অর্থ পাচার। যেভাবেই হোক, আমাদের দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়েছে। এ কারণেই আমরা ডলার সংকটে পড়েছি। যেকোনো নির্বাচনী বছরেই দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য টাকা বিদেশে চলে যায়। ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের এক-দেড় বছর আগে থেকেই অর্থ পাচারের একটা প্রবণতা দেখা গেছে। অর্থ পাচার ঠেকাতে আমাদের বিশেষ মনোযোগ জরুরি। হুন্ডি বা অন্য কোনো উপায়ে যাতে ডলার বিদেশে পাচার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তা না হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল করা কঠিন হবে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ থেকে রেকর্ড পুঁজি দেশের বাইরে চলে গেছে।
ইতিবাচক দিক হলো, আমাদের কর আহরণ বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে কর আহরণ। সব মিলিয়ে বলা যায়, অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে, আমাদের ভীত বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, অর্থ পাচার প্রতিরোধে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হয়, তাহলে আমরা পূর্বের প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরে আসতে পারি। অনেক অর্থনীতিবিদই বলছেন, আমাদের খেলাপি ঋণের একটা বড় অংশই দেশের বাইরে চলে গেছে।
বাজেটে সাধারণত আয়-ব্যয়, বরাদ্দ ইত্যাদি উপাত্ত দেয়া হয়ে থাকে। স্রেফ আয়-ব্যয়ের উপাত্ত দিয়ে কিন্তু কোনো সরল সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। এখানে নীতির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে—অর্থ পাচার বন্ধ করা, ব্যাংক ও আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা, তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা। এখানে আরেকটি নীতিগত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, ক্রমান্বয়ে আমাদের ভর্তুকি কমানোর পথে কিন্তু হাঁটতে হবে। ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পর আমরা এত ভর্তুকি দিতে পারব না। রফতানি পণ্যে সহায়তা কিংবা প্রণোদনার পথও বন্ধ হয়ে যাবে তখন।
বাজেটে যেটা আসেনি বলে মনে হচ্ছে সেটা হলো, তৈরি পোশাক খাতে (আরএমজি) প্রণোদনা ধীরে ধীরে বন্ধের কোনো পলিসি না থাকা। চার দশকের আমাদের যে গার্মেন্ট খাত, সেখানে প্রণোদনা আগের মতো রাখতে হবে কেন? যেহেতু তারা বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা পাচ্ছে সেহেতু সহজেই আরএমজিতে প্রণোদনা কমিয়ে আনা যায়। চার দশকে যথেষ্ট পরিণত হওয়া আরএমজি খাতে প্রণোদনার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জায়গা রয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের কথা মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের সে পথে হাঁটতে হবে।
আরেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক সেটা হলো, বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। যত সুন্দর বাজেট করা হোক বা ভালো প্রকল্প নেয়া হোক—সময়মতো বাস্তবায়ন করতে না পারলে সবকিছুর খরচ বেড়ে যায়। কাজেই বাজেট বাস্তবায়নে মনোযোগ ও দৃষ্টি দিতে হবে। যে প্রকল্পই নেয়া হোক সেটা যেন যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা হয়। সামগ্রিকভাবে যে বাজেট হওয়ার কথা সে হিসেবে এটি সাহসী বাজেট। অনেকগুলো বিষয়ে আমদানি শুল্ক কমানো হয়েছে, আবার অনেকগুলো বিষয়ে আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। তবে আমদানি শুল্ক বাড়ানোয় তা স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। এ বাজেট মোটাদাগে জনগণের চাহিদা মেটাতে পেরেছে। আমাদের অর্থনীতিকে আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে আগের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারায় নিয়ে যেতে হবে। অর্থনীতিকে আগের প্রবৃদ্ধির ধারায় নিয়ে যেতে হলে আমি অর্থনীতির যে নীতিগুলোর কথা বলেছি সেগুলো বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ে জোর প্রচেষ্টা নিতেই হবে। ব্যাংক খাতকে শৃঙ্খলায় আনতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আরো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই প্রত্যাশা। তাহলেই ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।
ড. শামসুল আলম: অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ও সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী