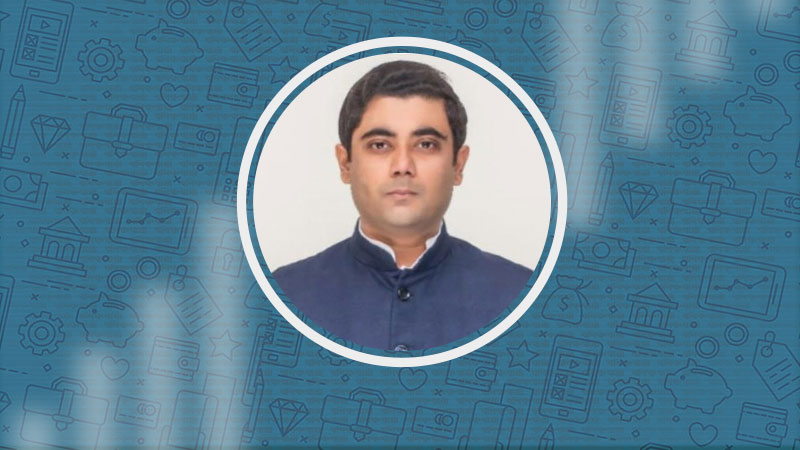 ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা দুই শতাব্দীরও বেশ কিছু আগে, কার্ল মার্ক্স ১৮১৮ সালের ৫ মে পশ্চিম জার্মানির ট্রিয়ার নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে লন্ডনে তার নীরব মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যেই মার্ক্সবাদী ঝড় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।
বার্লিন প্রাচীরের পতন হয় ১৯৮৯ সালে। অতঃপর সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রায় সব পূর্ববর্তী সমর্থক মার্ক্সবাদের মূল অর্থনৈতিক নীতিগুলোকে পরিত্যাগ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে পুঁজিবাদের বিজয় শুধু অনিবার্যই ছিল না, বরং সম্পূর্ণই মনে হয়েছিল। মার্ক্সের মৃত্যুর সময় মানুষের দুর্ভোগ, পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ কীভাবে মানুষের দুর্ভোগকে চিরস্থায়ী করতে পারে সে সম্পর্কে মার্ক্স কী বলতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে খুব কম লোকই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।
তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শুধু ১১ জন মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন—তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সহলেখক ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস। পুঁজিবাদের কাঠামোগত ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে মার্ক্স কী অর্জন করেছিলেন এবং কীভাবে এই ত্রুটিগুলো শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদকে নিজস্ব দ্বন্দ্বের ভেতরেই ভেঙে ফেলেছিল তা ব্যাখ্যা করার জন্য এঙ্গেলস তার বক্তৃতায় মার্ক্সের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।
এঙ্গেলসের জন্য মার্কস ছিলেন অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ডারউইন। মার্ক্স পুঁজিবাদ কীভাবে কাজ করে এবং কেন এটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং এর বিলুপ্তি থেকে একটি নতুন ব্যবস্থা উদ্ভূত হয় তা ব্যাখ্যা করার জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
তথাপি, মার্ক্স পুঁজিবাদকে একেবারেই যে খারিজ করেছিলেন এ যুক্তি দেয়াও ভুল হবে। মার্ক্স পুঁজিবাদের সম্পদ তৈরি এবং উৎপাদন সহজতর করার অবিশ্বাস্য ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেছেন, বুঝেছেন এবং তা উল্লেখ করেছেন এবং তিনি আত্মস্বার্থ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপরীতে এর দ্বৈত স্তম্ভের শক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায়গুলো হলো ব্যক্তিগত মালিকানা, যেখানে পুঁজিপতিরা একটি নির্দিষ্ট মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে, যেটা সামন্তবাদ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য রূপ। কী উৎপাদন করা উচিত, কীভাবে উৎপাদন করা উচিত এবং কার জন্য উৎপাদন করা উচিত এ প্রশ্নের উত্তর মুক্তবাজারের ওপর ছেড়ে দিয়ে এটি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা দেয়। মার্ক্স যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদে তীব্র প্রতিযোগিতা মালিকদের শ্রমিকদের মজুরি কমাতে অর্থাৎ শ্রমিকদের (সর্বহারা) থেকে ব্যবসার মালিকদের (বুর্জোয়াদের) কাছে সম্পদ স্থানান্তর করতে বাধ্য করবে এবং এটি আয় ও সম্পদের বৈষম্যের তীব্রতা বাড়াবে, যা সমাজকে এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে ঠেলে দেবে, যেখানে শ্রমিকরা তাদের মৌলিক চাহিদা আর পূরণ করতে পারবে না। এ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদীদের তাদের পণ্যের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণ করতে বাধ্য করবে, যার পরিণতি বিশ্বায়ন।
কিন্তু এমন একটি বিশ্ব যেখানে শ্রমিকরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলোর খুব সামান্যই পূরণ করতে পারে, তাদের এ ধরনের দাসত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সহ্য করার কোনো উৎসাহ থাকবে না।
সুতরাং মার্ক্সের মতে, একটি বিপ্লব অনিবার্য হবে এবং পুঁজিবাদীর ওপর সর্বহারা শ্রেণীর বিজয় একটি শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করবে, যা সর্বহারা শ্রেণীকে দুর্ভোগ ও শোষণ থেকে মুক্ত করবে।
তাহলে মার্ক্সের মৃত্যুর ১৪১ বছর পরও কেন পুঁজিবাদ তার নির্ধারিত পরিণতি ভোগ করেনি? সর্বোপরি আমরা এমন একটি বিশ্বে বাস করি যেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে তলানির ৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন মানুষের চেয়ে বেশি সম্পদ রয়েছে।
এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলোয়ও, ১৯৭৮ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ঘণ্টাপ্রতি প্রকৃত গড় মজুরি”অপরিবর্তিত রয়েছে। যেখানে ওই সময়ে এর জিডিপি তিন গুণের বেশি বেড়েছে, যা নির্দেশ করে যে আয় ও সম্পদ উভয়ই মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক বর্ণনায়”টপ (শীর্ষ) ১ শতাংশ” হিসাবে পরিচিত। এটি এক শতাব্দী আগে করা মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সঙ্গে মিলে যায়। তাহলে কোন শক্তি একটি বিপ্লব হওয়া থেকে বিরত রাখছে? তাহলে কি মার্ক্স ভুল বুঝেছেন? নাকি পুঁজিবাদীরা মার্ক্সের সতর্কবাণীকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন এবং পুঁজিবাদের পতন এড়াতে সমস্যাগুলো সমাধান করার উপায় খুঁজে বের করেছিলেন?
ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পুঁজিবাদের সহনশীলতায় অবদান রেখেছে। সেগুলো হলো: কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উত্থান, শ্রমিকের জন্য ভালো কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, বৃহৎ আকারে ঋণ ও গৃহনির্মাণ ঋণের ব্যবহার এবং পরিচয়ের রাজনীতির (যেমন জাতি, জাতীয়তা, ধর্ম ভিত্তি করে রাজনীতি) চিরস্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা।
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রবক্তারা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং কীভাবে এটি খুব অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে সম্পদকে কেন্দ্রীভূত করেছে তা জানেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে পুঁজিবাদের আরো মানবিক সংস্করণ সম্ভব যদি সরকার সম্পদ পুনর্বণ্টন করতে এবং সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। অতএব যা প্রয়োজন তা হলো একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা গণতন্ত্র, কল্যাণ ও পুঁজিবাদকে একই সঙ্গে বিদ্যমান রাখে এবং এর উন্নতি করতে দেয়।
আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, যা আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন ও বেকারত্ব সুবিধা প্রদান করে, আংশিকভাবে এ শঙ্কা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে দরিদ্রদের জন্য এ সুরক্ষাগুলো ছাড়া, উন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলোয় একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠবে। আর এ কারণেই এ অর্থনৈতিক প্রস্তাব এমনকি কিছু বুর্জোয়ারাও গ্রহণ করেছিল যারা চেয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্র যেন প্রবেশ না করে।
ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতা ক্লেমেন্ট অ্যাটলি (১৯৩৫-১৯৫৫) যিনি ১৯৪৫ সালে একটি অপ্রত্যাশিত নির্বাচনে জয় পেয়ে উইনস্টন চার্চিলের স্থলাভিষিক্ত হন, তিনিও রাশিয়ান কমিউনিজম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এটিকে কার্ল মার্ক্স এবং ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের অবৈধ সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।
কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটেন আর তার সাম্রাজ্যবাদী পন্থা চালিয়ে যেতে পারবে না এবং একটি নতুন আর্থসামাজিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যেমনটি ১৯৪২ সালের নভেম্বরে বেভারিজ রিপোর্ট দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল, যা যুক্তরাজ্যে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছিল এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের এ উত্থানই ব্যাখ্যা করে কেন পুঁজিবাদ পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ মানুষের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। কারণ এখন উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদ শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের কাছেই যায় না, বরং একটি রাজনৈতিক শ্রেণী সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরির জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে কর আরোপ করে এবং সম্পদের পুনর্বণ্টন করে। এটা কোনো অবাক করা ঘটনা নয় যে নরডিক দেশগুলোর আয়ের বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের হার বিশ্বের সবচেয়ে কম।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক কল্যাণের ওপর দৃষ্টিপাত বাড়ানো, নতুন নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হওয়ায় শ্রমের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এ পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসে বর্ণিত অত্যন্ত কঠোর শ্রমের অবস্থা নামক পরিবেশ থেকে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজকে মুক্তি দিয়েছে।
যাই হোক, কেন পুঁজিবাদ একটি শক্তিশালী কল্যাণরাষ্ট্র ছাড়া এমন জায়গায় বড় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়নি এটি তা ব্যাখ্যা করে না। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে বৈষম্য বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে (টপ ১ শতাংশ) ধনী ১ শতাংশ মানুষ এখন নিচের (বটম ৯০ শতাংশ) ৯০ শতাংশের সমান সম্পদের মালিক। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এ ব্যবধান ১৯৭০-এর দশকের শেষ থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বেড়েছে।
এমনকি যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মতো কিছু ইউরোপীয় দেশেও, আয়ের বৈষম্য এবং শীর্ষ ১ শতাংশ দ্বারা সৃষ্ট আয় ১৯৯০-এর দশকে বাড়তে থাকে, এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্বণ্টন ক্ষমতাকে নিরাশ করে। ‘ইংল্যান্ডের মালিক কে?’ গ্রন্থে গাই শ্রাবসোল বলেছেন যে অর্ধেক ব্রিটেনই ১ শতাংশের কম মানুষ দ্বারা পরিচালিত।
তাহলে পশ্চিম ইউরোপ কেন তাদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার প্রতি প্রতিশ্রুতি কমিয়ে দিয়েছে? এবং কেন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া (মার্ক্সবাদী অর্থে) এত কম হয়েছে? বর্ণনার একটি অংশ হলো, ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অনিবার্য মনে হচ্ছিল এবং পূর্ব ইউরোপের শোচনীয় জীবনযাত্রার অবস্থা আর কমিউনিস্ট প্রতিশ্রুতির ইউটোপিয়ার সঙ্গে মেলেনি, তখন পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী ও রাজনৈতিক অভিজাতরা তাদের সীমান্তে কমিউনিস্ট বিপ্লবের উত্থানে আর হুমকি অনুভব করেনি। এতে তারা রাজনৈতিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছিল এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের হুমকি প্রশমিত করতে সম্পদ পুনর্বণ্টনের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল তা কমে গিয়েছিল। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে নিম্ন স্তরের লোকদের ঋণ দানের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে তারা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে ঋণ নিয়ে সুস্থ জীবনযাত্রা বজায় রাখতে কিছুটা পেরেছিল। এতে তাদের উপার্জন ক্ষমতা কোনো মৌলিক পরিবর্তনের মুখোমুখি না হলেও ক্রমবর্ধমানভাবে ভালো জীবনযাপন করার সুযোগ তারা কিছুটা পেয়েছিল।
এ ধরনের ব্যবস্থা পুঁজিবাদের স্থপতিদের হাতে সময় দিয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ পুনর্গঠন করা যায় এবং এর লভ্যাংশ ক্রমেই কয়েকজনের হাতে যাচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সীমিত, যেখানে ক্রমেই কয়েকটি সত্তা অর্থনৈতিক ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে, কারণ মার্ক্স যা বিশ্বাস করতেন অর্থাৎ বিশ্ব দুটি মৌলিক পরিচয়ে (সর্বহারা ভার্সাস বুর্জোয়া) বিভক্ত ছিল আসলে তা নয়।
বিশ্বজুড়ে রাজনীতি যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট, বুর্জোয়া ও সর্বহারা উভয়ই আরো বিভক্ত হয়েছে—জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা ও রাজনৈতিক প্রেরণায়। সুতরাং এটা কোনো অবাক করা ব্যাপার নয় যে যখন মার্ক্সবাদী বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারা বলিভিয়ায় গিয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করতে এবং বিপ্লব ঘটাতে, তখন অনেক শ্রমিক তাকে সর্বহারা শ্রেণীর নায়ক হিসেবে দেখেনি, বরং একজন আর্জেন্টাইন সন্ত্রাসী হিসেবে দেখেছিলেন।
পরিচয়মূলক রাজনীতি এবং এর বিভিন্ন প্রকাশ শ্রমিক শ্রেণীর সম্মিলিত কণ্ঠকে দুর্বল করে এবং বিশ্বব্যাপী ঐক্যকে বাধা দেয়, যা মার্ক্স বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কতদিন টিকতে পারে যখন আমরা জানি যে পুঁজিবাদের মধ্যে ফাটলগুলো ক্রমবর্ধমান? ১৯৯৭ সালের এশীয় আর্থিক সংকট, ২০০১ সালের ডটকম সংকট এবং ২০০৮ সালের আর্থিক সংকট প্রমাণ করে যে জল্পনা এবং সস্তা ঋণের ভিত্তিতে কৃত্রিম প্রবৃদ্ধি কখনই অর্থনীতির শক্তিকে বশীভূত করতে পারে না, যখন অন্তর্নির্মিত অসংগতি তীব্র হয়ে ওঠে।
সামগ্রিকভাবে মার্ক্সের দীর্ঘস্থায়ী তাত্ত্বিক প্রভাব এ কারণে নয় যে তিনি দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখেছেন বা শ্রমিক বিপ্লব থেকে তিনি একটি সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবুও মার্ক্সের উত্তরাধিকার টিকে থাকবে কারণ তিনি পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন, যা একদিকে প্রচুর সম্পদ এবং অন্যদিকে সম্পদের অসমতা তৈরি করেছে। মার্ক্স স্পষ্টতই এবং সম্ভবত ভুলভাবে প্রস্তাব করেছিলেন যে পুঁজিবাদের পরবর্তী রূপান্তর হলো সমাজতন্ত্র। যেমন পুঁজিবাদ উদ্ভূত হয়েছিল সামন্তবাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে। তবুও কেবল ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদরাই চূড়ান্ত রায় দিতে পারবেন যে তিনি ভুল ছিলেন কিনা বা ঠিক ছিলেন কিনা এ যুক্তিতে যে পুঁজিবাদ মানবজাতির উন্নত জীবনের লক্ষ্যে চালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ হবে না। এমন একটি বিশ্ব যেখানে সংগঠিত লোভ, সমৃদ্ধি এবং মানব দুর্ভোগের কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি নয় সেক্ষেত্রে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যদি থাকে) কী ধরনের হবে যা পুঁজিবাদের চেয়ে ভালো কাজ করতে পারবে? সম্ভবত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের নতুন একজন কার্ল মার্ক্সের প্রয়োজন।
ড. আশিকুর রহমান: মুখ্য অর্থনীতিবিদ, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)







