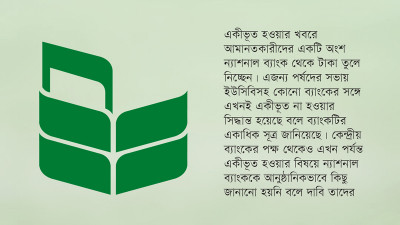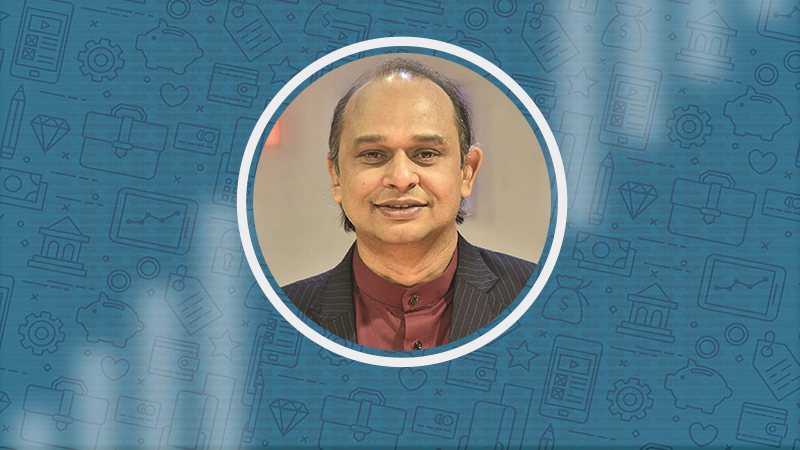
ইতিহাসের নিরিখে উপনিবেশোত্তর উন্নয়নশীল বিশ্বের বিকাশ
বিশ্লেষণে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চলকগুলোর একটি নিজস্ব আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলা
দরকার। এ বিকাশ বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নিয়ে বিতর্ক আছে। কোনোটাকে বলা হয়েছে
পুরোপুরি পশ্চিমা কায়দার, কোনোটা পশ্চিমা প্রভাবিত, কোনোটা বা প্রাচ্য বা
উপমহাদেশীয় বয়ান বা বুনন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রক্রিয়াগত পার্থক্যও বিদ্যমান।
কেউ আরোহী পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলেছেন। অনেকে জোর দিয়েছেন অবরোহী পদ্ধতির ওপর।
কেউ কেউ আবার উপলব্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে গঠনবাদী পদ্ধতির ওপর গুরুত্বরোপ
করেছেন।
রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যকার সম্পর্ক ও কার্যকারণ নিরূপণের
জন্য বিশ্লেষণী চলকগুলো নিয়ে আলোচনা জরুরি। অর্থনীতির চলকগুলো—পুঁজি,
শ্রম, ভূমি, প্রযুক্তি—সহজে নির্ধারণ করা গেলেও রাজনীতির বিষয়গুলোর
প্রতিনিধিত্বকারী চলক নির্ধারণ জটিল। এখানে রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলো—ক্ষমতা, শ্রেণী, আনুষ্ঠানিক
ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের আলোকে রাজনীতিকে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।
অনুরূপভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক ফলাফলকে পর্যালোচনা করতে হলে প্রয়োজন দেশটির
রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিশ্লেষণ। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিশ্লেষণ করে এবং একইভাবে
অর্থনৈতিক চলকের আলোকে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের রূপ অনুসন্ধান আবশ্যক। তার
আলোকে অর্থনৈতিক ফলাফল আলোচনা করা যাবে।
পুঁজির চরিত্র তথা অর্থনীতিতে কীভাবে পুঁজি তৈরি হচ্ছে,
কীভাবে পুঁজির বণ্টন হচ্ছে, কারা পুঁজি এবং পুঁজি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ
করছে ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যাবে অর্থনৈতিক ফলফলের ধরন। পুঁজিকে কেন্দ্র
করে কীভাবে রাজনীতি তথা ক্ষমতা, শ্রেণী, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান
আবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্লেষণের মধ্যেই নিহিত আছে
রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের চেহারা। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এখানে বিশ্লেষণী
কাঠামো। রাজনৈতিক বন্দোবস্ত হলো ক্ষমতার বণ্টন। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো এবং
বিভিন্ন নীতি-কৌশলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বুঝতে হলে ক্ষমতার বণ্টন বোঝা
দরকার। এখানে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত একটি দর্পণ, যা ক্ষমতার বণ্টন ও ক্ষমতা
কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যম। এখানে শ্রেণী প্রশ্নও জড়িত। মূলত ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক ফলাফল বণ্টনের ভিত্তিতে উৎপত্তি হয় বিভিন্ন শ্রেণী। বিভিন্ন শ্রেণী আবার
বিভিন্ন উপায়ে ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফলকে প্রভাবিত করে। পুরো প্রক্রিয়াটি
জটিল ও সূক্ষ্ম
আবর্তে গাঁথা। প্রতিটি চলক বিশ্লেষণ এবং একে অন্যের সঙ্গে
সম্পর্ক, কার্যকারণ,
মিথস্ক্রিয়া, ছেদ, নির্ভরশীলতা নির্ণয়ের মাধ্যমেই বোঝা যাবে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ও
অর্থনৈতিক ফলাফল। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে অর্থনৈতিক চলকগুলো
বিশ্লেষণে যেমন রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলো জানা দরকার হবে, তেমনি
রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলো বুঝতে অর্থনৈতিক চলকগুলো গুরুত্ব বহন করে। এখানে
রাজনীতি ও অর্থনীতির মধ্যকার জটিল ও সূক্ষ্ম সম্পর্ক অনুধাবনের
প্রয়াস নেয়া হয়েছে।
রাষ্ট্র বিনির্মাণ অ্যাডহক সংস্কার ও
কাঠামোগত সমন্বয় নয়। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কের
বিনির্মাণই রাষ্ট্রের বিনির্মাণ। রাষ্ট্র কার্যকরী হওয়ার জন্য মধ্যক ভোটারের
হাতে ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। জনসমাজ বা পাবলিক সোসাইটির উত্থান ঘটে যখন ক্ষমতা মধ্যক
বা অধিকাংশ জনসংখ্যার মধ্যে থাকে। যদিও ক্ষমতা বণ্টনের চরম ডানে থাকা ব্যক্তিরাই
ব্যবহার করে চলেছে এবং ক্ষমতা ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আদর্শ জনসমাজ দিয়ে গঠিত
রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানসহ গণদ্রব্য
বিতরণ বা পাবলিক প্রভিশনিংয়ের মাধ্যমে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করে। অন্যদিকে
নাগরিকরা করের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে তহবিল সরবরাহ করে। সুতরাং রাষ্ট্র ও নাগরিকের
মধ্যে একটি দেয়া-নেয়া
সম্পর্ক তৈরি হয়।
জনসমাজ রীতি, রেওয়াজ ও মূল্যবোধের
আন্তঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রভাবিত করে। জনসমাজ ও
গণদ্রব্য বিতরণের
মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি নির্দিষ্ট সমাজের নাগরিকদের অধিকার দাবি
করার ক্ষমতা, মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরণ এবং অধিকার বিধান সেই নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের
প্রকৃতি ও স্বরূপ দিয়ে নির্ধারিত হয়। একটি রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি করা
জনসমাজ বা পাবলিক সোসাইটির অস্তিত্ব এবং কার্যকারিতার মাত্রার ওপর
নির্ভর করে।
একদিকে যেমন উৎপাদনের উপকরণ তথা ভূমি, পুঁজি,
শ্রমশক্তি, প্রযুক্তির গতিপ্রকৃতি ও পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে হবে; পাশাপাশি
রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক, যথা—জনগণ কী ধরনের রাষ্ট্র
চেয়েছে, রাষ্ট্র আসলে কী ধরনের রূপ নিয়েছে এবং কার দ্বারা ও কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে
তা বিবেচনার দাবি করে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের আন্তঃসম্পর্কে কী ও কীভাবে
পরিবর্তন ঘটেছে এবং রাজনীতি, ক্ষমতা, পুঁজি এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোর
মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বোঝা যাবে রাষ্ট্রটি কেমন হতে চেয়েছিল;
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেমন হয়েছে।
আলোচনাগুলোয় আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব
পেলেও অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে।
এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে যেমন সংবিধান, আইন, সম্পত্তির অধিকার, বিচারিক বিধিনির্দেশ
ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক নিয়ম বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে, তেমনি
অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রথা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, রীতি,
রেওয়াজকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের ও রাষ্ট্রের
সম্পর্ক সম্পদের বণ্টন, সুযোগ-সুবিধা, প্রণোদনা, সীমাবদ্ধতা, বিধিনিষেধ ইত্যাদি
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এ সম্পর্ক শুধু আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই
নির্ধারিত হয় না, অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোও সম্পর্ক নির্ধারণ করে। তাই সামাজিক
পরিবর্তন বুঝতে গেলে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়েও আলোচনা করা জরুরি।
প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিশাস্ত্রে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিষ্ঠানের
ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। এ ধারা দেখিয়েছে, যেসব দেশে
প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ও কার্যকর আছে, সেসব দেশেই টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন
হয়েছে। শক্তিশালী ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা পশ্চিমা উন্নত দেশ ও পূর্ব
এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূলে আছে। অন্যদিকে যেসব দেশ
স্থায়িত্বশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে বা সাময়িক
উচ্চপ্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হলেও একটা সময় তা বজায় রাখতে পারেনি। ফলে
টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়নি, তার অন্যতম প্রধান কারণ
ভঙ্গুর ও অকার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা।
এ আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রবণতার একটি বয়ান
তুলে ধরা হয়েছে। মনে রাখা দরকার উন্নয়নশীল দেশগুলো সমজাতীয় নয়। তাদের ইতিহাস,
উন্নয়নের পর্যায় এবং নীতি নির্দেশনার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। বিশদ দেশভিত্তিক কেস
স্টাডির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ তা অনুধাবনযোগ্য। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গতিপথের
মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা রূপান্তরের পথনকশা এবং পরিবর্তনের জন্য চলক নির্ধারণে
সহায়ক। অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ এবং এজেন্ডা-সেটিংয়ের জন্য দরকারি
পরামর্শ পরিবেশন করা জরুরি কাজ। এ সীমাবদ্ধতাগুলো এ নিবন্ধের রয়েই গেল।
২.
মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মানবিক সামাজিকতা থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে এবং এ ব্যক্তিমানুষ কেবল
পুঁজির মধ্যেই নিজেকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ব্যক্তিনিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তিস্বার্থের এ উৎকট
রূপ মানুষকে ক্রমাগত পরিবার থেকেও বিচ্ছিন্ন করছে। পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে যে
আন্তঃসম্পর্ক ছিল, সেই আন্তঃসম্পর্কের বিচার ও বিবেচনা বোধগুলো পুঁজির সঙ্গে
সম্পর্কিত হয়ে পুঁজিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের মধ্যে সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতার
অভাব তৈরির ফলে ব্যক্তি তার নিজস্ব বোধ, বুদ্ধি ও বিচারকে পুঁজির মধ্যেই সমর্পিত
করছে। আত্মসমর্পণের এই যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া, এর ফলে ব্যক্তি
যেমন তার পরিবারকে ভেঙে ফেলছে, একই কায়দায় অর্থের মধ্যে নিজের মুক্তি খোঁজার
প্রাণান্তকর চেষ্টার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলছে।
অর্থের পেছনে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা একটি ব্যবস্থাগত
বিষয়। সমাজও এভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। এ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষ
হিসেবে নিজেকে আবিষ্কারের প্রবণতার বাইরে অর্থের মাধ্যমে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি
খুঁজে নিচ্ছে। পুঁজিও ক্ষমতার সমার্থক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। পুঁজির মাধ্যমে যেমন
ক্ষমতায় আরোহণ করা যায়, তেমনি ক্ষমতার মাধ্যমে সহিংসতা নিশ্চিত করা যায়। সহিংসতার
মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে মনুষ্যত্বহীন মানুষ বা কঙ্কালসার
মানুষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ পুঁজি, ক্ষমতা ও তার মানদণ্ড এক ধারায়
প্রবহমান। ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সমাজে
বিচ্ছিন্নতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এটি এমন একটি রাষ্ট্র তৈরি করছে, যা ক্রমাগত সহিংস
হয়ে উঠছে এবং এ সহিংসতার ক্ষমতা আসছে পুঁজির সর্বগ্রাসী রূপ থেকে। এদের মধ্যে একটি
দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিরাজমান। অর্থাৎ পুঁজি থাকলে ক্ষমতা থাকে, আবার ক্ষমতা থাকলে
সহিংসতা সৃষ্টিরও ক্ষমতা থাকে। ফলে মানুষের মধ্যে অধিকারহীনতার একটি সংস্কৃতি তৈরি
হয়েছে। অর্থাৎ পুঁজির সর্বগ্রাসী রূপটাই মরিয়া হয়ে অধিকারহীনতা রূপে আবির্ভূত
হচ্ছে। অধিকারহীনতা ও সহিংসতা বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে রাষ্ট্র ও
রাষ্ট্রযন্ত্র। ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রের রোধন প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা
হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের প্রবণতা তৈরি না হয়ে
রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী সহিংসরূপে আবির্ভূত হচ্ছে এবং সেভাবেই রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে
চালিত করছে। এভাবে নতুন ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চালু
হচ্ছে। এ রাজনৈতিক বন্দোবস্তে মানুষ নিঃসঙ্গ। এ রাজনৈতিক বন্দোবস্তে মানুষটা
কীভাবে গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে অর্থ গ্রাস করবে, তার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। এ সর্বগ্রাসী প্রক্রিয়ার
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ছে। আমলাতান্ত্রিকতার সঙ্গে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক
বাস্তবতা এবং আইনপ্রণেতাদের সংশ্লেষের মাধ্যমে ‘ক্ষমতা-অর্থ-ক্ষমতার’ বিষাক্ত
চক্র তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ ছিটকে পড়ছে। অধিকাংশের টিকে থাকা কঠিন থেকে কঠিনতর
হচ্ছে। আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছে কেউ কেউ। বেঁচে থেকেও জীবন্মৃত হতে বাধ্য হচ্ছে।
সর্বগ্রাসী নিপীড়ন ও টিকে থাকার সংগ্রাম সামাজিক মমত্ববোধ থেকে বিতাড়িত করে
ঔদাসীন্য, অনীহা, অনাকাঙ্ক্ষা কাতর নির্জীব, নিস্তরঙ্গ, জড় পদার্থে পরিণত করতে
বাধ্য করছে।
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিস্বার্থ রূপে পর্যবসিত
হয়েছে। এখানে তথাকথিত এনলাইটেনড সেলফ ইন্টারেস্ট বিরল। বরং
তা ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির খোলসে পরিণত হয়েছে। মানুষের মধ্যে মানবিক সামাজিকতা,
সংগ্রামী আকাঙ্ক্ষা বা সর্বজন সমাজ তৈরির আকাঙ্ক্ষা, যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভালোবাসা
বা মনুষ্যত্বের বিকাশ, এ সর্বজনীন সত্তাকে তিরোহিত করার উদগ্র চেষ্টা চলছে।
মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে। মানুষ প্রাণী হলেও
প্রাণী হিসেবে অন্যান্য জীবের থেকে মানুষের প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য
পার্থক্যকারী প্রথম দিক মানুষের সঙ্গে মানুষের তথা সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে নিজেদের
মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক। এ সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। এ ফাটলকে ত্বরান্বিত করেছে
অধিকারহীনতা ও পুঁজি সংগ্রহের সর্বগ্রাসী তৎপরতা।
মানুষের অনন্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৃজনশীলতা।
এটি মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করে। অর্থাৎ মানুষ সৃজনশীল কায়দায় নানা সমস্যা থেকে
উত্তরণের জন্য বিভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি ও মাধ্যম তৈরি
করেছে। এর মাধ্যমে সে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছে। এভাবে সমাজের মধ্যে
প্রতিষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত সংগ্রাম তৈরির মাধ্যমে ক্রমাগত সহিংসতাগুলোকে প্রশমিত করা
হতো। সহিংসতা কমিয়ে ফেলার এ প্রক্রিয়াটা নিঃশেষ হয়ে
যাচ্ছে। ফলে মানুষ ক্রমাগত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে জনতুষ্টিবাদের দিকে
ঝুঁকছে। জনতুষ্টিবাদ ক্রমে তাকে নিঃসঙ্গ করছে। পুঁজিতে পর্যবসিত হচ্ছে। মানুষ
তার নিজস্বতাকে কমিয়ে আনা, নিজেদের মধ্যে সংঘাতকামী যন্ত্র বা প্রযুক্তি
আবিষ্কার ও ব্যবহারে বুঁদ হলেও সৃজনশীল মুক্তির সত্তা নির্মাণে নিয়োজিত হতে পারছে
না।
মানবপ্রকৃতির তৃতীয় বা বড় বৈশিষ্ট্য তার ক্ষমতা
অর্থাৎ মানবিক সত্তা এবং সম্পর্কযুক্ত সত্তার মাধ্যমে প্রযুক্তি তৈরি করে প্রগতি
নিশ্চিত করা। কিন্তু সেই প্রগতির মধ্যেও ছেদ ধরছে। কারণ প্রযুক্তি এক ধরনের
দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি করছে। মানুষ নিজেকে নিঃসঙ্গ করে প্রযুক্তির ওপর হাল ছেড়ে
দিচ্ছে, যা পরবর্তী সময়ে ভয়ংকর পুঁজির চরিত্র নিতে পারে। ঠিক একই কায়দায় দেখা
যাচ্ছে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সহিংস হয়ে উঠছে, তেমনি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো
ক্রমাগত এর কার্যক্রম পালন করা থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো
ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো এমন কিছু ভূমিকা পালন করছে, যার ফলে সামনের দিকে অগ্রসর
না হয়ে ক্ষমতা ও পুঁজির কাছে সমর্পিত হচ্ছে। সমর্পণের এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে
রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরি হচ্ছে তা ক্রমাগত এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছে, যার
মাধ্যমে মানুষ নিঃসঙ্গ হচ্ছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ বজায়
রাখছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে কতকগুলো
গোষ্ঠীর মধ্যে পর্যবসিত হচ্ছে। সংকোচনের এ প্রক্রিয়াটা এতটাই দ্রুতগতির
যে এটি রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সমঝোতা অর্থাৎ সংবিধান বা সামাজিক চুক্তির সঙ্গে
পুরো মাত্রায় সম্পর্কবিহীন হয়ে ক্রমে অতিকায় দানবীয়
গোষ্ঠীতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। একদিকে অধিকারহীনতা প্রকট হচ্ছে, অন্যদিকে
রাষ্ট্র দানবীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে এবং এ দানবীয় চরিত্রকে টিকিয়ে রাখছে অচলায়তনিক
সংবিধান।
কালের পরিক্রমায় প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে মানুষকে
আত্মকেন্দ্রিক এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থপর হিসেবে দেখানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে মানুষের মধ্যে স্বভাবজাতভাবে সামাজিকতার চর্চা বিদ্যমান। মানুষ শুধু নিজের
জন্য চিন্তা করে না। সমাজের নানা স্তরে একেকটি দলে বা উপদলে বিভক্ত মানবসমাজের
মাঝে সহায়তা এবং বন্ধনের সম্পর্ক বিদ্যমান। এ বৈশিষ্ট্য
তাকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করে। সমাজে বাস করতে গিয়ে নানা আচার-আচরণ, সহানুভূতি,
সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে পরস্পরের দেখভাল করে। সহায়তার ধর্ম
যেমন সমাজে বিরাজ করে, তেমনি একটা বড় অংশের মাঝে অপরাধের প্রবণতাও রয়েছে। এ ভালো
এবং মন্দের মাঝে সাম্যাবস্থা তৈরির জন্য সমাজে নানা নীতি, বিচার ব্যবস্থা,
নৈতিকতা এবং নিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজেরই একটি বর্ধিত রূপ হিসেবে
ভূমিকা পালন করে। যে রাষ্ট্রে সঠিক বিচার ব্যবস্থা এবং সাম্যের বিধান ও প্রয়োগ
রয়েছে সেখানে অপরাধের সুযোগ কম, বৈষম্যের ব্যাপকতাও থাকে না। বিভিন্ন শ্রেণীর
স্বার্থ এবং চাহিদার রকমভেদ থাকলেও সেই চাহিদার সাম্যের ভিত্তিতেই সমাজ চলে।
ন্যায়বিচার, সাম্য ও মানবিক মর্যাদা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। অন্যের প্রতি
সহমর্মিতার শিক্ষা পরিবার থেকেই আসে। তাই পরিবারকে সমাজের একক বলা যায়।
অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানব আচরণের মৌলিক ভিত্তি গড়ে দেয়। যেমন একটি শিশু
পরিবার থেকে কেমন শিক্ষা পেল তার ওপর নির্ভর করে তার
ভবিষ্যতের পথ চলা এবং অন্যের প্রতি আচরণের রূপ। যে পরিবারে সহিংসতা বেশি সে
পরিবারের সন্তান পরবর্তীকালে সঠিক পরিবেশ না পাওয়ার দরুন সহিংস হয়ে ওঠার আশঙ্কা
থাকে। সহিংসতার মাত্রা দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে। নারী ও
শিশুদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তরুণদের ওপরও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে
চলেছে। সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কগুলো ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে। সহমর্মিতা লোপ
পাচ্ছে। পরিবারগুলো ক্রমাগত ভাঙনের মুখে। বর্তমানকালের রাষ্ট্রের যে সহিংস রূপ
দৃশ্যমান তা অনেকাংশেই অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নেতিবাচক
পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়। রাষ্ট্র একচেটিয়াভাবে তার পুঁজিবাদী এবং লুটেরা মনোভাব
প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে মানুষ সামাজিকতার বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত
হয়ে এককেন্দ্রিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সম্পদের সিংহভাগ দখল করে আছে ধনিক শ্রেণী। গরিবের
সংখ্যা বড়। তাদের বড় একটি অংশ এক বেলা খাওয়ার পর পরের বেলা খাওয়া জুটবে কিনা সেই
অনিশ্চয়তায় দিনাতিপাত
করছে। অন্যদিকে
কেউ দেশের ভেতর যেমন সম্পদের পাহাড় গড়ছে, তেমনি দেশের বাইরেও সম্পদ
পাচার করছে। সম্পদ পাচারকারীরা আবার দেশের ভেতরে কোনো উৎপাদনশীল খাতে অর্থও
বিনিয়োগ করছে না। বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে অর্থ বিনিয়োগ করলে কর্মসংস্থানের পরিধি
বাড়ত। বেকারত্ব যুবসমাজকে অপরাধের দিকে ধাবিত করছে। যুবসমাজের বিশাল অংশ ক্ষমতার
পদলেহন সংস্কৃতির শিকার। বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতার
অভাবে অপরাধ করেও এখন পার পাওয়া যায়। তাদের আশ্রয় দেয় প্রতাপশালী কোনো
নেতা। প্রসঙ্গত, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা বা ন্যায়বিচারের অভাব অপরাধের প্রবণতা
বাড়ায়। অপরাধী তখন অপরাধ করতে ইতস্তত করে না। শাস্তি এড়ানোর কৌশল তার জানা থাকে।
অতীতে যে তরুণ সমাজের বজ্রকণ্ঠে রাজপথ কম্পিত হয়েছে, যাদের ন্যায়সংগত
আন্দোলনে একচেটিয়া রাষ্ট্র ভীত হয়েছে, সেই তরুণের কণ্ঠে তোষামোদের সুর।
প্রথাগত অর্থশাস্ত্রে ধারণা করা হয় যে মানুষ মাত্রই
যুক্তিযুক্তভাবে তার প্রয়োজন মেটায় এবং তার উপযোগ বৃদ্ধি করে। সমাজের প্রত্যেক
ব্যক্তি এরূপ যুক্তিযুক্ত উপায়ে নিজ নিজ উপযোগ তথা ভোগ, সুবিধা ও লাভের আকার বড়
করার মাধ্যমে এক ধরনের সাম্যাবস্থা বা স্থিতাবস্থা তৈরি হয়। বাস্তব অবস্থাটা এমন নয়।
রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে এবং অন্যের ভোগের ওপর বাধা আরোপ না করে নিজের
উপযোগ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতো তাহলে বৈষম্য এবং
গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রকটতা বৃদ্ধি পেত না। প্রকৃতপক্ষে সমাজের নানা নিয়ম-কানুন,
রীতিনীতি বা কনভেনশনের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। মানুষ সংঘবদ্ধ এবং
সামাজিক প্রাণী। আবার এ কথাও সত্যি যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মাঝে অন্যায়
করার মানসিকতা রয়েছে। তাই তার অন্যায় করার সুযোগ সীমিত করার জন্য কিছু রীতিনীতি,
নিয়মের উদ্ভব হয়েছে। ইতিহাস ঘাঁটলেও এর সত্যতা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সাম্যাবস্থা
নিশ্চিত করতে হলে সমাজে আইন-কানুন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরি। আর এটিই হতে
পারে জনআকাঙ্ক্ষার প্রজাতন্ত্রের মৌল ভিত্তি।
আধুনিক পুঁজিবাদের তত্ত্বে মানব আচরণের যে
আত্মকেন্দ্রিক ধারণা দেয়া হয় তা মানুষের প্রকৃতগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে
অসামঞ্জস্যপূর্ণ। গোষ্ঠীতন্ত্রের বিরূপ বিস্তারে মানুষের মাঝে একটা বিশেষ শ্রেণী
ক্রমাগত লাভবান হচ্ছে, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটাচ্ছে। গণমানুষ তার ন্যায্য প্রাপ্তি
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কালো ছায়া তাদের স্খলন ঘটাচ্ছে। কীভাবে
অন্যকে বঞ্চিত করে, অন্যের অংশকে লুটে নিয়ে নিজের ভাগের অর্থ বৃদ্ধি করা যায় সেই
চেষ্টার একটা প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দৃশ্যমান।
৩.
সর্বজন সমাজ তৈরির যে আকাঙ্ক্ষা গণমানুষের মাঝে কাজ করে
তার অধিকার রাষ্ট্র দিতে চায় না। রাষ্ট্র কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়। জনগণ, সরকার,
ভূখণ্ড, বিচার ব্যবস্থা,
সামাজিক রীতিনীতি সবকিছু নিয়েই রাষ্ট্র। সরকার যখন রাষ্ট্রের ধারণাকে নিজেকে ঘিরে
কেন্দ্রীভূত করে এবং জনগণকে তার অধিকার প্রাপ্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
থেকে বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ক্ষমতার অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে, তখনই বৈষম্য
হয়, নাগরিক অধিকার হরণ হয়। জনগণের জন্যই রাষ্ট্র এবং তার জন্মগত নাগরিক অধিকার
সরকারের কোনো দান নয়। জনগণ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা দলগুলোকে তার অধিকার প্রাপ্তির
নিশ্চিতকরণের জন্যই সাংবিধানিকভাবে দায়িত্বের আসনে বসায়। কোনো ব্যবস্থা সর্বজনীন
এবং সর্বজনের না হলে বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে না, যদিও সে ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে
বৈষম্যনাশের জন্যই। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক সুরক্ষা নীতির আওতায় নির্দিষ্ট কিছু
মানুষকে লক্ষ করে নেয়া ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যকে দূর করতে সক্ষম হচ্ছে না। এ
ব্যবস্থা সর্বজনীন নয়। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলোয় সবার সমান,
সর্বজনীন সুযোগ থাকার কথা। বর্তমানের সামাজিক নিরাপত্তার জালের বদলে সর্বজনীন
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য,
নিরাপদ সুপেয় পানিসহ অন্যান্য জনদ্রব্যের অধিকার ধনী-গরিবের। জনদ্রব্যের সর্বৈব
প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে রাষ্ট্রে বৈষম্য দূর হয়। সঙ্গে
সঙ্গে
শ্রম দক্ষতা ও উৎপাদন
ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়।
সর্বজন সমাজ সৃষ্টির জন্য জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা
রয়েছে। উদাহরণে দেখা যায় যে যখনই নাগরিক অধিকার বিশেষ করে জনদ্রব্যের প্রাপ্তিকে
রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে তখনই সংগ্রাম হয়েছে। সমাজের নানা স্তরের মানুষ যার যার
জায়গা থেকে নিজ নিজ নাগরিক কর্তব্য পালন করেছে। অধিকার আদায়ে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ
করার সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রও অতীতের একচেটিয়াত্ব ও
একক সহিংসতার অবয়বে সদর্পে দণ্ডায়মান।
সর্বজন সমাজ তৈরির মাধ্যমে জনগণের নাগরিক অধিকার
নিশ্চিত করা যায়। সর্বজন সমাজ সৃষ্টি কোনো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়।
রাষ্ট্রের ধর্মই হলো
একচেটিয়া প্রভাব খাটানো ও বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা। রাষ্ট্রকে
জবাবদিহিমূলক সংস্কৃতির ধারায় আনতে হলে জনগণের সংগ্রাম, প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতে
হয়। এ সংগ্রাম নানা উপায়ে এবং নানা স্তর থেকে সংগঠিত হয়। অতীত ইতিহাস থেকে দেখা
যায়,
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া নিজ
নিজ অবস্থান থেকে সংগ্রাম করেছে এবং রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছে। এ চাপ
সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার সুযোগ সংকুচিত হয়ে গেছে। ফলে
স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার আরো বিকট রূপ প্রতীয়মান হচ্ছে।
নাগরিক অধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে।
একইভাবে দেখা যায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতেও বড় রকমের
ক্ষত তৈরি হচ্ছে। রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা এবং রাষ্ট্র তার দায়িত্ব
পালন করতে না পারার ফলে জনবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে
দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটছে এবং অনেক রাষ্ট্রেই তা প্রকটতর পর্যায়ে চলে
গেছে। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে হিংসা-হানাহানি বেড়েছে। অনেক জায়গায় যুদ্ধ শুরু হয়েছে।
পরিণতিতে লাখ লাখ মানুষ শরণার্থী। যুদ্ধের
কারণগুলো প্রশ্নবিদ্ধ থেকেছে। কেতাবি কায়দার গণতান্ত্রিক পীঠভূমি তথা ইউরোপে
দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছে। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ইউরোপ থেকে বের হয়ে
যাওয়া তথা ব্রেক্সিটের মতো ঘটনাও ঘটেছে। সেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের বড়
ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে।
জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র পরাশক্তি
হিসেবে থাকলেও নেতৃত্ব প্রদানে প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ হচ্ছে। যদিও উদীয়মান শক্তি
চীন আন্তর্জাতিকতার পক্ষে কথা বলছে, তবুও এখনো উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় নিজের
অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রক্ষা তথা বাণিজ্যিক লাভালাভের মধ্যেই নিজেকে আবর্তিত
করছে। আঞ্চলিক ক্ষমতাধররাও প্রতিবেশীর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের কারণে ওই
দেশগুলোর জনমানসে স্থান করে নিতে পারেনি। ফলে আস্থাহীনতা ও
অবিশ্বাস বেশি হারে বাড়ছে। কোথাও তা চাপা ক্ষোভ হিসেবে বা ওই আঞ্চলিক ক্ষমতাধরদের
বশংবদদের থেকে ক্ষমতার পালাবদল ঘটছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান।
অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত
সংস্থা জাতিসংঘের ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পেয়েছে। বহুপাক্ষিকতাকে জলাঞ্জলি দিতে
হচ্ছে। আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষি দ্বিপাক্ষিকতানির্ভর হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা
নৈতিক বৈধতাহীন সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনস্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে। ভয়ের
সংস্কৃতি ও অধিকারহীনতা বড় ধরনের বিষয় হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অধিকারহীনতা
রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি সমাজের সর্বস্তরে বিরাজ করতে শুরু করেছে।
রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্যের প্রক্রিয়া ক্রমে
নিঃশেষিত হচ্ছে এবং অতিকায় জনতুষ্টিবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের সহিংস
চরিত্রগুলো দিন দিন বিভিন্নভাবে প্রকাশ হয়েছে এবং রাষ্ট্র আইনি প্রক্রিয়ার
মাধ্যমেই নিষ্পেষণ
ও জনঅধিকারহীনতার বাহন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের চুক্তি অকেজো
হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত
হচ্ছে। ফলে সমাজের আশানুরূপ পরিবর্তন কার্যত ব্যাহত হচ্ছে।
রাষ্ট্রীয় স্বৈরশাসন প্রণালির জন্য নতুন নতুন আইনগত
বৈধতা তৈরি করা হচ্ছে। অতীতে ভিন্নমত ও সব ধরনের বিরোধিতা-সমালোচনা দমনের
লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্বাভাবিক আইনগুলো রদ করে জরুরি অবস্থা জারি
করত। কিন্তু বর্তমানে তার দরকার পড়ে না, রাষ্ট্র এখন নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে
‘স্বাভাবিক’ পরিস্থিতি বজায় রেখে নাগরিকের সক্রিয়তা-বুদ্ধিজীবিতা-স্বৈরতন্ত্রের
বিরোধিতা দমন করছে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্র আরো প্রবল, আরো
নিরঙ্কুশ আইনি এখতিয়ার ভোগ করছে। সরকারের সমালোচনা করলেই ‘রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি’
ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে গণ্য করে আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। এসব আইনে ব্যবহৃত ‘রাষ্ট্রের
সুনাম’, ‘রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা, ‘মিথ্যা ও অশ্লীল’ ইত্যাদি শব্দবন্ধকে
সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। সম্ভবত এসব শব্দবন্ধ
অস্পষ্ট রাখাই এ আইনগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এসব
শব্দবন্ধকে যখন যেভাবে খুশি ব্যাখ্যা করে অপব্যবহার করছে। ভয়াবহ নিবর্তনমূলক আইন
প্রণয়নের পেছনে রাষ্ট্রের প্রণোদনা কী? রাষ্ট্র কেন এ
ধরনের আইন
প্রণয়নকে অনিবার্য মনে করছে? নাগরিকের নিরাপত্তাহীনতা ও ক্রমাগত সংকট উৎপাদন করা
রাষ্ট্রের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে
প্রতিষ্ঠিত করতে নাগরিকের মনোজগতে সংকটকে স্থায়ী করে তোলা হয়েছে। সমাজে
নিরাপত্তাহীনতা, ভয় ও ত্রাস পদ্ধতিগতভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। সর্বব্যাপী নজরদারির
জাল বিস্তারের মাধ্যমে নাগরিকের সব কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের
নাগালের মধ্যে আনা হচ্ছে। একদিকে রাষ্ট্র সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা দিতে পারছে
না, ন্যায়বিচার প্রলম্বিত হচ্ছে, অন্যদিকে ক্রমে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত
হয়েছে। ভিন্নমতকে ক্রিমিনালাইজ করে তোলার লক্ষ্যে আইন তৈরি হচ্ছে। ভিন্নমত কেবল
একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় নয়, একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ
গঠনের লক্ষ্যে ভিন্নমত অধিকতর দরকারি শর্ত। ভিন্নমত ছাড়া মানুষ
‘ব্যক্তি’ হয় না। ভিন্নমত ছাড়া সমাজ হয় না। কিন্তু একটা সর্বাত্মকবাদী
রাষ্ট্রপ্রণালি তা যদি এমনকি ‘বিপ্লবী’ রাষ্ট্র দাবিদারও হয়, ভিন্নমতকে নির্মূল
করার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ব্যয় করে এবং গোটা সমাজকে মনোলিথিক তথা একজাতীয় সমাজে
পরিণত করতে চায়; সেখানে ‘সত্য’ মানে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় বয়ান, ‘মিথ্যা’ মানে
সরকারবিরোধিতা, সরকারের সমালোচনা—এটাই একচেটিয়াতন্ত্র।
প্রতিটি আইন ও আইনগত পদ্ধতির একটি আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক
দিক আছে। এটি প্রয়োজনীয় শর্ত। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আইনের মান্যতা। অর্থাৎ
আইনকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা এবং সমাজ মেনে নিয়েছে কিনা। এ মান্যতা আসে
অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান থেকে। একে বলা হয় ‘নর্ম’, যা রীতি বা রেওয়াজ ধারণ করে।
প্রতিটি আইন ও আইনগত পদ্ধতিকে নর্ম ধারণ করতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন তৈরির
প্রতিষ্ঠান তথা সংসদ আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, আইনটি মূল্যবোধ, রীতি বা রেওয়াজ দিয়ে
সিদ্ধ হতে হবে। এ দুই শর্ত পূরণ করলেই প্রায়োগিকভাবে মানুষের মনে অনুমোদিত আইন
সম্পর্কে সহজাত মান্যতা তৈরি করবে। ফলে অনুমোদিত আইনের মূল উদ্দেশ্য মানুষের আচরণ
কী হবে, কীভাবে অর্জিত হবে। কিন্তু যখন অবৈধ হস্তক্ষেপ বা লঙ্ঘনের কারণে বেআইনি
কার্যকলাপকে আইন হিসেবে মান্য করতে বাধ্য করানো হবে, তখন তা আর আইন থাকবে না। তখন
ওই শাসন ব্যবস্থাকে
আইনের শাসন ব্যবস্থা
বলা যাবে না। ওই ব্যবস্থাকে আইনের নামে দুঃশাসন বলা যেতে পারে।
যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে, রাষ্ট্রই একমাত্র বৈধ
সহিংসতার অধিকারী এবং তত্ত্বগতভাবে বলা হয়ে থাকে, এটাই একমাত্র বৈধতা বা
লেজিটিমেসি দিতে পারে। ফলে কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ, এটা রাষ্ট্রই ঠিক করে দেবে।
জাতিরাষ্ট্র নিজেই একচেটিয়াভাবে বৈধ সহিংসতার কর্তৃত্ব গ্রহণের চেষ্টা করে। অবশ্য বৈধ
সহিংসতার ধারণা মৌলিকভাবে আইনি সূত্রকাঠামোয় নির্ণীত হয়। এ সূত্রকাঠামোয় সর্বজন
তার স্বাধিকারের একটি অংশ জনপ্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রক্ষমতাকে দিয়ে দেয়। প্রত্যেক নাগরিকের
স্বাধীনতার অংশবিশেষের ছাড়টি এ অনুমিতি থেকে করা হয় যে প্রাপ্ত ক্ষমতাটি সম্মিলিত
ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করবে। এখান থেকেই মূলত সহিংসতার একচেটিয়াত্বের এ বিশেষ বৈধতা
লাভ করে। তবে দরকারি শর্ত হচ্ছে, এ একচেটিয়াত্ব সম্মিলিত ইচ্ছা ও জনপ্রতিনিধিত্বের
মাধ্যমে সমর্থিত হতে হবে। এখানে বৈধ বলতে বেঁধে দেয়া কিছু মাপকাঠি বোঝানো হচ্ছে,
যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ইচ্ছা ও একচেটিয়া সহিংসতা প্রয়োগ করা হয় আইনি ক্ষমতার
দোহাইয়ে, এর বাইরে গিয়ে নয়। অর্থাৎ সম্মিলিত স্বার্থ রক্ষার জন্যই বৈধ
সহিংসতার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এ বৈধতা গৃহীত হয় নানা ভিত্তি থেকে, যেগুলো
রাষ্ট্রের ধারণা তার প্রকৃতি ও কাঠামোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ফলে রাষ্ট্রের
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যেমন ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, তেমনি রোধন ও সমন্বয়ন করা হয়।
এ ‘রোধন ও সমন্বয়ন’ সংবিধান দিয়ে গ্যারান্টিযুক্ত একটি
মৌলিক নীতি। এ অলঙ্ঘ্য মৌলিক নীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিটি শাখা অন্য শাখার ওপর
প্রভাব রাখার এবং অন্য শাখার ক্রিয়াকলাপ ও পদ্ধতিগুলোকে জবাবদিহি, দায়বদ্ধ ও রোধ
করার মাধ্যমে ভারসাম্য বজায় রাখে। ভারসাম্যহীনতা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের
সহিংসতার একচেটিয়াত্বের বৈধতা খারিজ হয়ে যায়। রাষ্ট্র ও সংবিধান সম্মিলিত ইচ্ছা ও
নাগরিকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হলে গণমানুষের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত
স্বার্থের দিকে লক্ষ রাখতে না পারলে ‘বৈধ সহিংসতার’ ওপর রাষ্ট্রের একচেটিয়া
কর্তৃত্বের ধারণা সাধারণ সহিংসতায় পরিণত হয়। এভাবেই কর্তৃত্বকামী যেকোনো ধরনের
সক্রিয়তাই ‘অবৈধ সহিংসতা’ হয়ে ওঠে। বৈধতার ভিত্তি হলো নাগরিক শাসন ব্যবস্থার
আদর্শিক সম্মতি। শাসন ব্যবস্থায় সম্মতি আসে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন থেকে। এছাড়া
নাগরিকের সম্মতি গ্রহণের বিকল্প কোনো পথ নেই।
দৃষ্টিভঙ্গিও বাঁধাধরা কিছু গতে ঘুরপাক খাচ্ছে।
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিজের
কুক্ষিগত করতে পারে না। রাষ্ট্র যদি চিন্তাশীলতাকে নিজের কুক্ষিগত করে সম্পূর্ণ
নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চালায় এবং নিজেকে সমাজের চিন্তা, বিবেক, শিক্ষা, আদর্শ
ইত্যাদির একমাত্র নির্ধারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাহির করতে চায়, তাহলে তা আর
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকে না। প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার, কথা
বলার ও সমাবেশ করার অধিকার আছে। প্রতিবাদ করার অধিকার নাগরিকের সর্বজনীন অধিকার।
মানুষের সে অধিকারগুলো যখন কোনো সংগঠিত গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের
চেষ্টা করে,
তখনই বিপত্তি দেখা দেয়। এ কুক্ষিগতকরণের সংস্কৃতি সর্বব্যাপী। উদাহরণস্বরূপ এ
একচেটিয়া সংস্কৃতি মুক্তচিন্তাচর্চার সূতিকাগার হিসেবে পরিগণিত
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে। একচেটিয়াতন্ত্র সর্বদা নতুন চিন্তা ও
জ্ঞানবিমুখ এবং সর্বদা সাফাই সাক্ষ্য, উঞ্ছবৃত্তি, লেজুড়বৃত্তি, চাটুকারিত্ব
ও দাসত্ব বিস্তৃতিতে উৎসাহিত। একই প্রক্রিয়ায় নাগরিক
সমাজের অনেক অংশীজন গোষ্ঠীতন্ত্রের মাঝেই নিজেদের লাভজনক অবস্থান খুঁজে নিয়েছেন।
অনেকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, সহিংসতার মুখে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন।
সামগ্রিকভাবে নাগরিক সমাজ ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে
পড়েছে। পুঁজির অবাধ সরবরাহ এক্ষেত্রে বড় ধরনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।
রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রচণ্ডভাবে
সর্বজনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। রাষ্ট্র জনতার প্রতিষ্ঠান। দিন দিন প্রতিষ্ঠানগুলো
ভেঙে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বন্দোবস্ত গোষ্ঠীতন্ত্রের কবলে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের
সঙ্গে অধিকাংশ জনতার ‘সামাজিক চুক্তি’ ঢিলে হয়ে পড়ছে। জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক
ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার কোনো বিকল্প নেই। এ মৌলিকে ফিরে যাওয়াই
প্রধানতম কাজ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে যদি টেকসই ও বজায়মান
প্রবৃদ্ধির ধারায় টেনে আনতে হয়, তাহলে আদিম পুঁজি সঞ্চয়ের পন্থা, যেমন—দুর্নীতি,
অপকর্ম, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন প্রভৃতি অবলম্বনের পরিবর্তে উৎপাদন খাতকে গতিশীল
করার কৌশল অনুসরণ জরুরি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকারের
অভাব, আইনের শাসন ও জবাবদিহির প্রতি অবজ্ঞা, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এবং
ক্ষমতাশালীদের মাধ্যমে অর্থনীতিকে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার মারাত্মক প্রবণতা দৃশ্যমান।
ধনিক শ্রেণীর
সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু করদাতার সংখ্যা বাড়েনি। এটি এলিট শ্রেণী গঠনের
কাঠামোগত দুর্বলতা এবং তাদের গোষ্ঠীতান্ত্রিক চরিত্রকেই নির্দেশ করে।
রাষ্ট্রকে সর্বজনের ও সর্বজনীন না করতে পারলে রাষ্ট্র শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গুটিকয়েক গোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল করবে। সবার অংশগ্রহণ ও সর্বজনীন মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র তখন সত্যিকার অর্থেই জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়। একটি ভারসাম্যভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাই রাষ্ট্রকে সর্বজনের ও সর্বজনীন হতে হয়। নির্বাহী বিভাগ নিজেকে রাষ্ট্র মনে করা শুরু করেছে। বিচার বিভাগ তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে। রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের শাসন, তাদের কার্যাবলি এবং সিদ্ধান্তের প্রতি নাগরিক সমর্থন এবং ঐকমত্য এবং একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি মূলত আদর্শিক বৈধতার ওপর নির্ভর করে। সর্বজনের সম্মতিমূলক আদর্শিক বৈধতা বা নরমেটিভ লেজিটিমেসি প্রধানত রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং কাঠামো থেকে আসে। সম্মতিমূলক আদর্শিক বৈধতা চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। নাগরিকের ধারণাগত উন্মেষ এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্মতিমূলক আদর্শিক বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আদর্শিক বৈধতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণ এবং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। যদি ক্ষমতার বণ্টন এবং কার্যাবলি নিয়ে নাগরিক ঐকমত্য এবং পারস্পরিক সহায়তার পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে স্থিতাবস্থা আসবে এবং জনমঙ্গলকারী বৃদ্ধির পথও সুগম হয়। মানুষ মাত্রই পস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। এ আন্তঃনির্ভরশীলতার সম্পর্কে সহযোগিতার পরিবেশ তখনই সুসংহত হয় যখন বৈধতা তথা আদর্শিক বৈধতার ব্যাপারে সামাজিকভাবে ঐকমত্য তৈরি হয়।
৪.
সমানতালে লক্ষ করা গেছে, অনেকগুলো দেশের জাতীয় আয় বা
মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ঘটছে এবং বৈষম্যের মাত্রা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে।
এ সংখ্যাতত্ত্বের গভীরে গেলে দেখা যায়, কোন শ্রেণীর মানুষ কতটুকু সম্পদ
সংগ্রহ করেছে, কতটুকু লাভবান হয়েছে এবং কী ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়েছে তা গণনা করা
হচ্ছে না। পরিসংখ্যানগুলো ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে, টেকসই
স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ধরনের পথ গ্রহণযোগ্য কিনা।
সারা পৃথিবীতে হাতেগোনা কিছু মানুষের তল্পিতে সম্পদ
কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। অধিকাংশ মানুষই বড় রকমের বৈষম্যের শিকার। আয় বণ্টন ও
অর্থনীতির কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গত ২০০ বছরে মূলত দুই ধরনের চিন্তাকাঠামো গড়ে
উঠেছে। উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এ
চিন্তাধারা উদারনীতিবাদের
কারণে দ্রুত সম্পদ ও আয়ের কেন্দ্রীভবন হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকলেও তারা মনে
করেন,
পুঁজিপতিরা ভোগ করার জন্য নয়, সঞ্চয় করার জন্য পুরস্কৃত হয়। অর্থাৎ সংযমের জন্য।
দ্বিতীয় চিন্তাধারা ‘ক্ষমতা’কে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তাদের তাত্ত্বিক কাঠামো
নির্মাণ করে। ক্ষমতা পুঁজির ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। শ্রমজীবীদের ওপরও
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এ ধারা নজর দিয়েছে কী কারণে ক্ষমতা সৃষ্টি হয়, কীভাবে তা বজায়
রাখা ও শক্তিশালী করা হয়। এর সঙ্গে যোগ করে বলা যেতে পারে, ক্ষমতার একচেটিয়া
নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বৈষম্য বৃদ্ধির মৌলিক কারণ।
বৈষম্য বাড়ার অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে রয়েছে
আয়বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য। সমস্যার মৌলিক জায়গায় জোর দিতে হবে।
দেখা যাচ্ছে, শ্রমিক যে ধরনের মজুরি পাচ্ছেন, তার তুলনায় পুঁজিপতির
প্রাপ্তির পরিমাণ কয়েক গুণ বেশি। ক্ষমতা খাটিয়ে আদিম সঞ্চয়নের মাধমে সম্পদের
কেন্দ্রীকরণ করছেন।
অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষ সম্পদ তৈরি করার সক্ষমতার বাইরে থাকছে।
বৈষম্য নিয়ে নানা তত্ত্ব দেয়া হয়। নীতিনির্ধারকরা
বৈষম্যকে উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপের সহজাত অংশ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এ
তত্ত্ব অনেক আগেই অসার প্রমাণ হয়েছে। মূলত ক্ষমতাই বৈষম্যের মূল ভিত্তি এবং
ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বৈষ্যমের হার চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা
স্বযংক্রিয়ভাবে
স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ
বাস্তবায়ন স্তরেও নীতিগুলোকে অকার্যকর করে তোলে। ফলে বৈষম্যকে আরো প্রশস্ত এবং
দারিদ্র্য হ্রাসের হারকে ধীরগতি করে তোলে। এ পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ববাদ সত্তা
অন্যায্য সমাজ তৈরির দিকে পরিচালিত করে থাকে। যখন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বেশির ভাগ
লোকের হয় না, তখন ‘ক্লায়ন্টেলিজম’ বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রাধান্য পায়। গোষ্ঠীতন্ত্র
অনর্জিত সম্পদ (রেন্ট) সংগ্রহ করে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে
আদিম কায়দায় সম্পদ কেন্দ্রীভুবন চলতে থাকে। সম্পদনির্ভর সিন্ডিকেট
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যবস্থায়
নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো নাগরিকদের পরিষেবা সরবরাহ করতে
ব্যর্থ হয় এবং নাগরিক-রাষ্ট্রের ধারণাটি একটি দূরের আত্ম চিৎকারে পরিণত হয়।
আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম মূল কারণ
রেন্টিয়ার শ্রেণীগুলো বা উপস্বত্বজীবীদের অর্থের লালসা এবং অর্থের প্রবাহে নিয়ন্ত্রণ।
উৎপাদনশীল খাতগুলোয় রেন্টিয়ার শ্রেণী বা উপস্বত্বজীবীদের দাপটের
কারণে অর্থ শুধু একদিকে যাচ্ছে। অর্থের সুষম বণ্টন না থাকায় এবং ক্ষেত্রভেদে
শ্রমের মজুরির ব্যাপক তারতম্য হওয়ায় বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। নতুন শিল্প
তৈরি হচ্ছে না কিন্তু জিডিপির আকার বাড়ছে। রেন্টিয়ার শ্রেণীর বিপুল অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে
সঙ্গে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। রাঘববোয়াল
ঋণখেলাপিদের ঋণ পরিশোধে কড়াকড়ির বদলে নানা সুবিধা দিয়ে আরো ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা
হচ্ছে। অথচ যেই জনগণের টাকা নিয়ে ব্যাংক থেকে এ ধনিক শ্রেণীকে টাকা দেয়া হচ্ছে
তাদের বেলায় ব্যাংক কোনো ছাড় দিচ্ছে না। ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর
উদ্যোক্তাকে দেয়ার মতো অর্থ ব্যাংকের কাছে থাকে না আর থাকলেও কঠিন নিয়মের
মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বড় বড় প্রকল্পেও নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারি
প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে
প্রকল্পগুলোর খরচও বাড়ে, সময়ও অপচয় হয়। অন্যদিকে সাধারণ জনগণের
প্রাপ্তি শুধু ভোগান্তি আর আর্থসামাজিক সংগ্রামের নিত্যনতুন রূপের সঙ্গে
প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি।
অতিমারী শুরুর আগ থেকেই উন্নয়নশীল বিশ্ব কাঠামোগত
চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। কভিড অতিমারী পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই
রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এবং সর্বোপরি জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় নিম্নমুখী চাপ
বাড়িয়েই চলছে। নভেল করোনাভাইরাস অতিমারী প্রান্তিক গোষ্ঠীর সদস্য, বিশেষত নিম্ন ও
নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ, মহিলা, শিশু, বযস্ক, বেকার ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের
জীবন ও জীবিকায় মারাত্মক অভিঘাত ফেলেছে। স্বল্প ও নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারগুলো মারাত্মকভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতের মজুরি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায়
জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়েছে। মূল মজুরি কমে যাওয়ায় অধিকাংশ
মানুষ নিজেদের সঞ্চয় ভেঙে ব্যয় করছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ নিজেদের দৈনন্দিন
খরচের জন্য ধার-দেনা করছে। ক্রমাগত মূল্যস্ফীতির চাপে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার
অনুপস্থিতিতে অনেককে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমাতে বাধ্য করেছে। ফলে
সার্বিকভাবে পুষ্টি গ্রহণের মাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। কেউ কেউ চিকিৎসা ও শিশু শিক্ষার
ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন। বহিঃস্থ চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে যখন পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর
স্বজনতোষী রাজনীতি ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতা তৈরি ও অধিকাংশ জনগণকে বঞ্চিত করে
ক্ষমতাসীন মহলের সুবিধা আদায়ের প্রবণতায় জরাগ্রস্ত হয়ে থাকে।
সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার শর্ত পূরণ না হওয়ায় কভিড
অতিমারী থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার গতিপথের চেহারা ইংরেজি ‘কে’ অক্ষরের মতো হয়েছে। ‘কে’
অক্ষর দিয়ে বোঝানো হচ্ছে—একদিকে বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর
সম্পদ বেড়েই যাবে, অন্যদিকে অধিকাংশ মানুষের আয় কমবে। প্রণোদনা
প্যাকেজগুলো মূলত বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিতদের স্বার্থই
রক্ষা করেছে। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, দরিদ্র, ঝুঁকিপ্রবণ এবং সমাজের
পিছিয়ে পড়া বিশাল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের হার বাড়ার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য ও মেরুকরণ
বৃদ্ধি অর্থনীতির পুনরুদ্ধার একটি ইংরেজি ‘কে’ অক্ষরের মতো বৈষম্যমূলক
পুনরুদ্ধার পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
পরিমাণগত নয়, প্রবৃদ্ধির গুণগত মান এবং রূপান্তরযোগ্যতা
নিয়েই আলোচনা করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ বাড়লেও ঝরে পড়ার সংখ্যা
বাড়ছে। মাধ্যমিক স্তরে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। চতুর্থ
শিল্প বিপ্লবের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কথা বলা হলেও
প্রযুক্তি খাতে
নিরেট আমদানিনির্ভরই রয়ে গেছে। এখন দরকার গবেষণা ও উদ্ভাবন সক্ষমতা
বাড়ানোর প্রয়াস। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হলে শিক্ষিত বেকারত্বের বোঝা ব্যাপক কমে
যাবে। কলা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়াসহ সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম ছাড়া মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়
না। শিক্ষা খাতে
জ্ঞান সৃষ্টি এবং জ্ঞানচর্চার অভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।
অনেক সময় ‘উৎপাদনমুখী বা কর্মসংস্থানমুখীন শিক্ষা’র
মতো একটি ভ্রান্ত ধারণার কথা বলা হয়। এটি মনে রাখতে হবে, শিক্ষার মৌলিক অর্থ
মানবিক মর্যাদা ও মনুষ্যত্ব তৈরি। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নাগরিক মানুষ হিসেবে গড়ে
তোলা এবং জ্ঞান সৃষ্টি ও চর্চার মানসিকতার উন্মেষ ঘটানো। নাগরিক শিক্ষা প্রদান
করতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বৃদ্ধি পাবে।
তারা কর দেবে, দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, রাজনীতি সচেতন হবে এবং সমাজ ও
অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে।
চিকিৎসাসেবা নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে চলে
যাচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতে ব্যক্তি খাতে খরচ বেড়েছে ঢের বেশি।
অন্যদিকে
স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মানে রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা সাধারণ
মানুষের হাতের নাগালের বাইরেই রয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর
মানুষের অধিকার নয়। দেশের প্রতিটা নাগরিকের জন্মগত অধিকার এবং একই সঙ্গে
প্রয়োজনীয়তা। স্বাস্থ্যসেবা খাতের বৈষম্য দূর করার জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার
প্রচলন সময়ের দাবি। এ মৌলিক অধিকারগুলোকে চ্যারিটি হিসেবে ভাবলে ভুল হবে। এটাকে
অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভেদ করলেও সঠিক হবে না।
রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে প্রতিটা নাগরিককে এ মৌলিক সেবাগুলো দিতে রাষ্ট্র বাধ্য।
বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা জাল কাজ করছে
না। প্রয়োজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বস্তরে জীবনব্যাপী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
যে জনমিতিক পরিবর্তন হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, শিশু, যুবা, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের
পাশাপাশি বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। যেহেতু বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে,
অথচ যদি যথেষ্ট পরিমাণের আয় না থাকে, সেই আয় থেকে বাঁচিয়ে সঞ্চয় না থাকে, তাহলে
প্রবীণকালে মর্মান্তিক জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে। তাহলে আয়ু বাড়লেও সে ক্রমাগত একটি
দরিদ্র অবস্থার মধ্যেই জীবনযাপন করবে। এ অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির
মাধ্যমে পেনশন ব্যবস্থা
চালু করা দরকার। এর
সঙ্গে প্রয়োজন মাতৃভাতা ও শিশুকল্যাণ ভাতা চালুর ব্যবস্থা নেয়া। যদি আগামীর দিকে
এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে গোটা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি
হাতে নিতে হবে। এ সর্বজনীন কর্মসূচি নিতে হবে শিশুর জন্য, মায়ের জন্য, বৃদ্ধ ও
কর্মমুখী সর্বজন মানুষের জন্য। পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বলে,
সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য টার্গেটকেন্দ্রিক কর্মসূচি উদিষ্ট লক্ষ্য সম্পন্ন
করতে পারেনি।
অন্তর্ভুক্তির নামে অনেক তথাকথিত উদ্ভাবনীমূলক টার্গেটকেন্দ্রিক অনেক
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েও জেনারেশনের পর জেনারেশনকে এখনো মানবেতর জীবনযাপন করতে
হচ্ছে। সর্বজনের জন্য সৃজনশীল সর্বজনীনতাই পরীক্ষিত পথ।
সামষ্টিক অর্থনীতিতে সাম্যাবস্থা তৈরি করতে হলে অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে। চাহিদা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রকে চাহিদা উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। জনগণের চাহিদানুযায়ী পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং জনগণের তা ভোগ করার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। কর্মসংস্থানের পরিবেশ উন্নত করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া আয় হবে না, ক্রয়ক্ষমতা তৈরি হবে না এবং চাহিদা বাড়বে না। সর্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত হবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, বহুমুখীকরণ ও জনদ্রব্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে পারলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে, রাষ্ট্রও লাভবান হবে।
৫.
শ্রমিকই সবচেয়ে বড় পুঁজি। শ্রমিক নিয়োজনের মাধ্যমে
প্রবৃদ্ধির চাকা ঘোরানো
নতুন কিছু নয়। এটি ক্লাসিক্যাল। জনমানুষ গ্রাম থেকে শহরে ও বিদেশে শ্রমিক হিসেবে
গেছে। আয়ের প্রায় পুরোটাই গ্রামে পাঠিয়েছেন, দারিদ্র্য কমেছে এবং ভোগ ব্যয় বেড়েছে।
ভোগ ব্যয় বাড়ায় জিডিপির পরিসর বেড়েছে। অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠিয়ে যে প্রবৃদ্ধি
অর্জন সম্ভব হয়েছে শ্রমিকদের দক্ষ করা গেলে আরো বেশি অর্জন হবে।
কর্মশূন্য প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। কর্ম সৃষ্টিকারী
প্রবৃদ্ধি কৌশলের দিকে যেতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার। সংগত
প্রশ্ন—কী
উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে? কর্মসংস্থান তৈরিবিহীন প্রবৃদ্ধি? বর্তমানে
অসংখ্য তরুণ বেকার। তাহলে ‘জনমিতিক লভ্যাংশ’ অর্জন না করতে পারায় একটি প্রজন্ম কি
হারিয়ে যাবে? বিনিয়োগনির্ভর প্রক্রিয়া ছাড়া ভোগ বাবদ ব্যয় থেকে আসা উন্নয়ন কখনই
টেকসই নয়। এ রকম ভোগনির্ভর অর্থনীতিতে আমদানি চাহিদা বেশি থাকে এবং যেকোনো বহিঃস্থ
চাপ তৈরি হলে সার্বিক বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যকে ঝুঁকিতে ফেলে। ভোগ বাবদ ব্যয় থেকে
উৎসারিত প্রবৃদ্ধি সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানোর জন্য অধিক ভোক্তা ব্যয়ের
ওপর নির্ভর করে। অন্যদিকে বিনিয়োগ নেতৃত্বাধীন প্রবৃদ্ধি নতুন
উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি করে। ফলাফল হিসেবে আরো বেশি কর্মসংস্থান এবং অধিক চাহিদা তৈরি
হয়।
একটি উন্নয়নশীল
দেশ ভোগ বাবদ ব্যয়কেন্দ্রিক দেশে পরিণত হলে আমদানি চাহিদা সর্বদা বেশি থাকে।
কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রবৃদ্ধিতে ধীরতা আসে।
ধরে নেয়া হচ্ছে, প্রবৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে
হবে। তাহলে কৃষি খাতের
প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস রোধ করতে হবে। শিল্প খাতের পরিমাণ বাড়ছে না ও
বহুমুখীকরণ হচ্ছে না। শিল্প খাতে নেতিবাচক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে
বিশিল্পায়নের যাত্রা। বিশিল্পায়নের ফলে দীর্ঘমেয়দি প্রবৃদ্ধিতে ঋণাত্মক
প্রভাব পড়বে। অনানুষ্ঠানিকীকরণ বিশিল্পায়ন থেকে উদ্ভূত। উন্নয়নশীল বিশ্বে
অনানুষ্ঠানিক খাতের আধিপত্য রয়েছে। আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা,
বিশেষ করে শিল্প খাতে ঋণাত্মক কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিশিল্পায়ন অকালে
শুরু হয়েছে। রফতানি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অর্থনীতিকে ঝুঁকিতে ফেলেছে।
পক্ষাঘাতগ্রস্ত নীতি প্রক্রিয়া আরো প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের সম্প্রসারণ ও
বৈচিত্র্যময় করার জন্য বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বাড়াতে পারেনি। শিল্প
খাতে উৎপাদনের বৃদ্ধি টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এ অকালীন বিশিল্পায়ন যাত্রাপথ
মোকাবেলা ও রূপান্তরকারী পরিবর্তনের পথনকশাযুক্ত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রয়োজন।
শিল্পায়নের
জন্য, শিল্পায়নে
কর্মসংস্থানের স্তর ও অনুপাতের পরিবর্তন এবং জিডিপিতে শিল্পায়নের অংশ বাড়ানোর জন্য
কার্যকরী নীতিকাঠামো ও বাস্তবায়নযোগ্য দিকনির্দেশনা ওই কৌশলগত পরিকল্পনায় থাকতে
হবে।
অটোমেশন আসবে, অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমবে, তাহলে
দক্ষতা যেমন বাড়াতে হবে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সমর্থ নতুন শ্রমঘন শিল্প
স্থাপনাও লাগবে। যদি ঠিকভাবে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে এবং
উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ে, তাহলে জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন করতে পারবে। এক পণ্যনির্ভর কৃষি
বা শিল্প অবকাঠামো খাতে যে এক ধরনের কেন্দ্রীকরণ হয়েছে, সেখান থেকে কীভাবে
বহুমুখীকরণ করা দরকার। যে স্থানিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে অর্থাৎ কতগুলো
জায়গায় শিল্প-কারখানার কেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, তার থেকে উত্তরণ ঘটানো দরকার। একদিকে
যেমন পণ্যের একমুখীকরণ বা কেন্দ্রীকরণ হয়েছে, তেমনি কর্মসংস্থান তৈরির ক্ষেত্রেও
এটি ঘটেছে। কর্মসংস্থানের স্থানিক কেন্দ্রীকরণের ফলে উচ্চমাত্রায় নগরায়ণ হচ্ছে
এবং নগরের ওপর চাপ বেড়েই চলছে। এ প্রক্রিয়া থেকে বের হতে নতুন
ধরনের শিল্প ও অবকাঠামোগত নীতি দরকার, যার মাধ্যমে প্রতিটি এলাকায় নিজস্ব কায়দায়
শিল্প ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেসব সড়ক বা রেলকাঠামো
রয়েছে, তার পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে
একদিকে যেমন ইউটিলিটি ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে,
তেমনি এর পাশে শিল্প-কলকারখানা ও সেবাপ্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে দেশব্যাপী শিল্প-কারখানা
বিস্তৃত করার সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে। সৃজনশীল ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে
একদিকে যেমন নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে, তেমনি পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোয় বড়
ধরনের নীতিগত ও আর্থিক প্রণোদনা দেয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের স্থানিক বিকেন্দ্রীকরণ
করা যেতে পারে। ফলে একদিকে যেমন জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগবে, অন্যদিকে উন্নয়নের
যে বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তা বিস্মৃত হবে। প্রবৃদ্ধিকে স্থানিক পর্যায় থেকে
সর্বব্যাপী করতে নতুন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। নিজস্ব কায়দায় সৃজনশীলতার
পরিচয় দিতে হবে। এগুলো ব্যতীত বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে না।
দক্ষতার অভাব অন্যতম সমস্যা। দক্ষ মানুষ তৈরির জন্য
একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার
কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, তেমনি প্রয়োজন কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা স্তরে ঝরে পড়ার হারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন
হয়নি।
বিশেষ করে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার আগের মতোই রয়ে গেছে। অন্যদিকে
গ্রামে ও শহরে শিক্ষা দানের পদ্ধতির মধ্যেও ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। উন্নত
দেশগুলোতে প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ
দেয়া হয়। তাদের ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ব-কর্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয় এবং বিভিন্ন
দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কাজে যুক্ত করা হয়। ফলে একজন শিক্ষার্থী আগে থেকেই বুঝতে পারে
সে কোন বিষয়ে বা কাজে দক্ষ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে এ চর্চা খুব জরুরি। যিনি
কাঠমিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করছেন, সামাজিকভাবে তার কাজকে সম্মানজনক
পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। ‘সকল কর্মই সম্মানের’—সমাজে এ বোধ এখনো জাগ্রত
হয়নি। এটা নিয়ে সামাজিক আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের উপানুষ্ঠানিক বৃত্তির
মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একদিকে যেমন প্রণোদনা দিতে হবে, তেমনি
তাদের কাজগুলো যে সম্মানের, সে বিষয়টিও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাষ্ট্রকে এমন একটি
মজুরিকাঠামো ঠিক করতে হবে, যার মাধ্যমে মানুষ শোভন জীবন যাপন করতে পারে। এর মানে
কর্মসংস্থানের সার্বিক প্রক্রিয়াকে ঢেলে সাজাতে হবে। অর্থাৎ ‘গড় নয় মধ্যক’ হোক
পরিমাপের মাপকাঠি, তাহলেই সর্বজনের নিশ্চিতি হবে।
কোনো জাতির মেধার গুণগত বিকাশ ও
মননশীলতার নিয়মিত চর্চা সেই জাতিকে তার স্বীয় মর্যাদায় বলিষ্ঠ করে তোলে। একটি দেশ
বা জাতিকে বিশ্বের দরবারে ইতিবাচকভাবে পরিচিত করার অন্যতম উপায় হলো তার
সাংস্কৃতিক পরিচয় ও বৈচিত্র্যকে মেলে ধরা। শৈশব থেকেই নাগরিক শিক্ষা প্রদান দেশের
মানুষের মাঝে নিজ দেশসহ অন্য দেশের ইতিহাসকে জানার আগ্রহবোধ জাগ্রত করতে শহর এলাকায় ওয়ার্ডে
ওয়ার্ডে এবং গ্রামাঞ্চলে পাঠাগারের চল জরুরি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে
আবাসন সংকটের সমাধান করার জন্য খেলার মাঠগুলোতে বাড়ি-ঘর গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের
অবৈধ দখলে নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ মেটানোর চেষ্টা পুরোদমে চলে। ফলে শিশুরা
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে তাদের মেধার বিকাশ হচ্ছে না, আরেকদিকে শারীরিক শ্রমের
জায়গাটা প্রযুক্তি দখল করে নিচ্ছে।
সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর্মের প্রতি বাঁধাধরা দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ধরে নেয়া হয় রান্নাবান্না শুধু নারীর কাজ, বৈদ্যুতিক বাতি নষ্ট হয়ে গেলে তা শুধু ইলেকট্রিশিয়ানই ঠিক করবে বা বই বাঁধাই করতেও দোকানে যেতে হবে। জীবন দক্ষতার প্রশিক্ষণ ব্যক্তির সক্ষমতা বাড়ায়। প্রত্যেক ব্যক্তির টিকে থাকার জন্য খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় কাজগুলোতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করতে পারলে একদিকে তার সক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ে, আরেকদিকে কর্মসংস্থানেও এগিয়ে থাকা যায়।
৬.
সামনে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।
উন্নয়নশীল বিশ্ব প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অনেক বেশি পিছিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে উদ্ভাবনী
ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা প্রকট। গোটা বিশ্বে প্রযুক্তি খাতে বর্তমানে
একচেটিয়াতন্ত্র বিরাজ করছে। অর্থনৈতিক পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো প্রযুক্তিগত দিক থেকেও
নিজেদের বৈশ্বিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কেন্দ্র বানিয়ে ফেলতে সম্ভব হয়েছে।
ইন্টারনেট বা অন্তর্জালের জগতে আধিপত্যের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও আধিপত্য
বিদ্যমান। খেয়াল করলে দেখা যাবে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তির বাজারের
লাগাম ধরে আছে। এমতাবস্থায় বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কীভাবে এই একচেটিয়াতন্ত্রেও
প্রযুক্তি বাজারে নিজের শক্তিশালী অবস্থান টিকিয়ে রাখবে। শুধু বৈশ্বিক পণ্যের
বাজার ধরলেই হবে না, একচেটিয়া প্রযুক্তি বাজারে স্বকীয় সত্তা তৈরির জন্য
কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। মেধা আছে, সৃজনশীলতা আছে। রাষ্ট্রকে ভূমিকা নিতে
হবে। তবেই তথ্যপ্রযুক্তিকেন্দ্রিক চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পাওয়া
যাবে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকেন্দ্রিক ‘ডিজিটাল বিপ্লব’ নিয়ে কতগুলো বিভ্রান্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ বিপ্লব মানুষের কাজের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। যেহেতু প্রযুক্তির কল্যাণে কাজের পরিমাণ কমে যাবে সেহেতু মানুষের স্বাধীনতা এবং আত্মসিদ্ধি অর্জন হবে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ডিজিটাল বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে কাজের পরিমাণ কমাচ্ছে না। বেতনভুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা হিসাব করলে দেখা যাবে অল্পসংখ্যক বেতনভুক্ত লোকবল নিয়ে এ বিপ্লব বেড়ে উঠছে। আবার তথ্যপ্রযুক্তির বড় বড় কোম্পানি বা টেক জায়ান্টগুলো নিজেদের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের বাইরে পারিশ্রমিক ছাড়াই অনেককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অল্প কিছু বেতনভুক কর্মচারীদের তুলনায় বিনা পারিশ্রমিকের এ অঘোষিত কর্মীদের সংখ্যা অগণিত। এরা ওই সব প্রতিষ্ঠানের সেবা ব্যবহারকারী। প্রতিষ্ঠানগুলো এদের ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হলেও এদের পেছনে কোনো অর্থই ব্যয় করতে হয় না। ডিজিটাল বিপ্লব বিরাটসংখ্যক মানুষের কার্যক্রমের ওপর নির্ভর করলেও এদের ন্যায্য প্রাপ্তিকে স্বীকার করছে না। এভাবে অধিকাংশ মানুষ শোষণের শিকার হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, যন্ত্র বা প্রযুক্তিই মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রকাশ। তাই যতই প্রযুক্তি ও যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে ততই শ্রমিকের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া কমে যাচ্ছে। কিন্তু ডিজিটাল বিপ্লব যে অবকাঠামো এবং কারিগরি যন্ত্রপাতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সেখানে অসংখ্য মানুষের শ্রম জড়িত। শ্রমিকদের অবদান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়া এ বিপ্লব কল্পনাও করা যায় না। দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ব্যবস্থা গুটি কয়েক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য অধিক মুনাফা অর্জন।
৭.
পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের
কারণে প্রতিনিয়ত মানুষের জীবন ও সম্পদহানি ঘটছে। উন্নত বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের
জন্য দায়ী গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
অভিযোজনের ব্যর্থতায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর প্রান্তিক
জনগোষ্ঠী। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতিকে বিশ্বসম্প্রদায় এখনো
পরিপূর্ণভাবে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে না। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বেও
জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমছে না। উন্নয়নের অধিকার প্রয়োজনীয় হলেও উন্নয়নশীল
বিশ্বে প্রাকৃতিক পরিবেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি তৈরির নানা রকম
উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন করতে হলে প্রাণ-প্রকৃতি ও
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিকল্প নেই। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে
নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষ যেমন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল,
তেমনি পরিবেশও
মানুষের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ পরস্পর নির্ভশীলতার আন্তঃসম্পর্ককে
নষ্ট করছে পুঁজি। প্রাকৃতিক সম্পদকে কেবল অর্থকরী
সম্পদ হিসেবে
বিবেচনা করার কারণে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরস্পর
নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে
গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। মানুষ নিজেকে পরিবেশের অংশ হিসেবে
বিবেচনা করছে না।
এভাবে সে পরিবেশের সঙ্গে একধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি করছে। এ বিচ্ছিন্নতার
কারণে পুঁজি বা অর্থ সংগ্রহের আদিম বাসনায় তাড়িত হয়ে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে
নিছক পণ্য হিসেবে দেখছে। পুঁজিপতিরা বাজারে যে পণ্যের দাম বেশি পায় স্বাভাবিকভাবেই
সে পণ্যের সরবরাহ বেশি করে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদকে নিছক পণ্য হিসেবে
দেখার কারণে দামের ক্রমানুসারে প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যমান নির্ধারণ করা
হচ্ছে। এভাবে বাজারের দামে সবচেয়ে দামি প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করা হচ্ছে সবচেয়ে
বেশি পরিমাণে। পুঁজিতাড়িত এবং অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রহের কারণে জীববৈচিত্র্য নষ্ট
হচ্ছে। ফলে পরিবেশের উপাদানসমূহ যথা: উৎপাদক, খাদক, জৈব ও অজৈব
উপাদানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। তৈরি হচ্ছে ‘মেটাবলিক রিফট’।
এভাবে নষ্ট
হচ্ছে পরিবেশের টেকসইযোগ্যতা।
মানুষ পরিবেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার মানুষের প্রচেষ্টাতেই পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রথমত, মানুষ নিজেকে পরিবেশের বাইরের কিছু মনে করলেই ভুল করবে। মানুষ নিজেও পরিবেশেরই অংশ। মানুষ ও পরিবেশ উভয়ের ভালো থাকা নির্ভর করবে একে অন্যের যত্ন নেয়ার ওপর। যেসব মানবসৃষ্ট কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মেটাবলিক রিফট তৈরি হচ্ছে সেসব কার্যক্রম বন্ধ বা উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেজন্য শক্তিশালী ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে বনজীবী বা স্থানীয় জনগণের চিরাচরিত অধিকারসমূহ এবং ঐতিহ্যগত রীতিনীতি, নিয়ম, রেওয়াজগুলোকে সংযুক্ত করতে হবে। পরিবেশ রক্ষার চিরাচরিত জ্ঞান ও চর্চাগুলো পরিবেশকে নিছক পণ্য বা অর্থকরী সম্পদ হিসেবে দেখে না। বরং এসব চর্চা ও রীতিনীতিতে পরিবেশকে নিজেদের জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়। এ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ও মানুষের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হলে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধিশালী হবে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং মানুষ ও পরিবেশ উভয়েরই ভালো থাকা নিশ্চিত হবে। পরিবেশ থেকে শুধু লাভজনক উপার্জন বা নিরবচ্ছিন্ন সুবিধাপ্রাপ্তিকে টেকসইযোগ্যতা মনে করা এক ধরনের ভ্রান্তি। বরং উভয়ের ভালো থাকা, সহাবস্থান, পরস্পরনির্ভরশীলতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতাই প্রকৃত টেকসইযোগ্যতা।
৮.
একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের
অর্থই হওয়া উচিত
জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। সমতাভিত্তিক সম্পর্ক না হলে এবং
সম্পর্কে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা হলে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক
থাকলেও তা জনগণকে কাছে টানতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে মানুষের চেতনায় অধিকার প্রীতি
ও স্বাধীনতা প্রীতি লক্ষ করা গেছে। সংকটকালীন সাহায্যের হাত বাড়ালে
যেমন কৃতজ্ঞ থাকে, তেমনি কেউ নিয়ন্ত্রণ বা খবরদারির উদ্দেশ্যে জেঁকে বসলে, তারা
বেঁকে বসে। মানুষের এ নিজস্বতার কারণেই কেউ সম্পর্কের হাত বাড়ালে তাকে স্বাগত
জানায়। কিন্তু এ স্বাগত জানানো স্থিতিশীল হবে তখনই যখন জনগণের সঙ্গে
জনগণের সম্পর্ক
প্রতিষ্ঠা করা যাবে। অর্থাৎ নাগরিকের কাছ থেকে সামাজিক অনুমোদন ও আদর্শিক সম্মতি
নেয়া গেলেই কেবল আন্তর্জাতিকভাবে একটি স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।
আন্তর্জাতিকতা ও বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকল্প
নেই। নিজস্ব সমস্যার সমাধান না করে সমস্যাগুলো বহির্মুখী রূপ দিচ্ছে, আপাত
জনতুষ্টির ফল লাভে সচেষ্ট হচ্ছে। এ ধরনের রাষ্ট্রগুলো দ্বিপক্ষীয়
(বাই-লেটারাল) সম্পর্কে থাকতে চায়, সম্পর্কের বিভিন্ন রকম ফর্ম বা রূপ
তৈরি
করে। এ ধরনের
ফর্মে বহুপাক্ষিকতার ওপর প্রাধান্য না দিয়ে আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক বিষয়ে আগ্রহ
দেখায়। কিন্তু নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান না করায় আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এ
ধরনের সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী হয়। এ ধরনের সহযোগিতার সম্পর্ক কাজ করে না এবং
ব্যাপক অস্থিরতা লক্ষ
করা যায়।
বিশ্বব্যাপী বহুত্ববাদের বিপরীতে জনতুষ্টিবাদ,
আন্তর্জাতিক সত্তা ও বিশ্বজনীনতার বিপরীতে উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার
বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সহাবস্থানের বদলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে
খণ্ডীকরণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ ধরনের হিংসাত্মক ও বিধ্বংসী মূল্যবোধের প্রসারে
প্রযুক্তির নেতিবাচক ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এ প্রবণতাগুলো বিশ্বকে ক্রমশ
সংঘর্ষের
দিকে ধাবিত করছে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক এ ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অবস্থান কী
হবে তা নিয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা জরুরি। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে
শক্ত অবস্থান তৈরি করতে না পারলে দেশীয় অর্থনীতির ভিত মজবুত হয় না।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে পুঁজিবাদী রূপান্তর বা উন্নয়নের টেকসই রূপান্তর ঘটেছে, তাদের সঙ্গে আগের উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাতে গোনা গুটিকতক রাষ্ট্রের টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে কতগুলো রাষ্ট্রের কোনো কোনো সময় মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বেড়েছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বিপর্যয় ঘটেছে এবং ফলে বিপরীতমুখী পরিবর্তন হয়েছে। এসব দেশ টানা অগ্রগতির মাধ্যমে স্থিতিশীলতা অর্জন করেনি। অর্থাৎ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হলেই চলবে না, টেকসই হয়ে স্থিতিশীল ও বজায়মান হতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর টেকসই অর্থনৈতিক বিবর্তন অর্জনকারী দেশগুলোয় সক্রিয় রাষ্ট্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। টেকসই রূপান্তরে রাষ্ট্র শুধু নিজেকে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির মধ্যে সীমিত করেনি। রাষ্ট্র যেমন একদিকে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনা প্রদান করেছে, তেমনি যখন পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রণোদনার অপব্যবহার হয়েছে, রাষ্ট্র কঠোর হাতে পুঁজিপতিদের দমন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। অত্যন্ত প্রভাবশালীরাও এ দুই হাতের সাম্যাবস্থা বজায় রাখতে বাদ পড়েনি। টেকসই অর্থনৈতিক বিবর্তন অর্জনকারী দেশগুলো সৃজনশীলতারও পরিচয় দিয়েছে। ইতিহাসলগ্নতায় নিবিষ্ট থেকে দেশোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করেছে।
৯.
সবচেয়ে বড় ক্ষমতা মানুষের সংগ্রামবোধ ও অধিকারবোধ,
মানুষের সৃজনশীলতা ও পরাধীনতা অতিক্রমের প্রচেষ্টা। উল্লেখ করা দরকার, যেকোনো
দেশের অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত সক্রিয় নাগরিকত্ব। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের
সম্পর্ক।
নাগরিক অধিকার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। পৃথিবীর উন্নয়নের ইতিহাস বলে, উন্নয়ন
শুধু রাষ্ট্র বা বাজারের বা পুঁজির বিষয় নয়। মৌল বিষয় হলো প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা।
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুটোই রয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা না বাড়লে জনগণ উন্নয়নের প্রকৃত সুফলভোগী হবে না।
নিষ্কাশনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রসার ঘটার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক
প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিসর সংকীর্ণ হওয়ায় অর্থনৈতিক রূপান্তর
বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থনীতির পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন সুদূরপরাহত হয়।
‘উন্নয়ন প্রথমে’ ও ‘গণতন্ত্র পরে’—এ ধরনের
একটা তাত্ত্বিকতাও লক্ষণীয়। এ ধরনের একটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বিশ্ব চলছে।
এক্ষেত্রে বড় পরিসরে মৌলিক প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে যে তাহলে রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের
সম্পর্ক কী হবে? পুঁজি কীভাবে বিনিয়োজিত হবে? মানুষের আর্থিক সম্পদ সংগ্রহের জন্য
মরিয়া হয়ে ওঠার প্রবণতাটাই প্রধানতম মাপকাঠি বা নির্ধারক হবে কিনা? সমাজ ও
পরিবারের মধ্যের সম্পর্কগুলো ঠুনকো হতে হতে ভেঙে যাবে কিনা? এক কথায় বলতে গেলে,
এখন মৌলিক প্রশ্ন বা প্রধান দ্বন্দ্বের প্রধান দিক হলো রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক
তথা গণতান্ত্রিকতা, সাংবিধানিকতা এবং এর বিপরীতে একচেটিয়াতন্ত্র।
রাশেদ আল
মাহমুদ তিতুমীর: অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান,
উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ স্মারক বক্তৃতা ২০২৩)