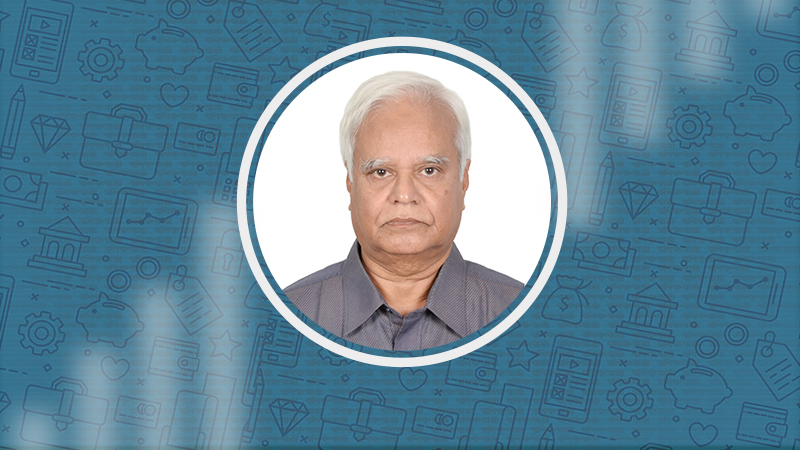 ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা জিডিপি ও জিএনআই প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচক তিন দশক ধরে সন্দেহাতীতভাবে জানান দিয়ে চলেছে যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি যেহেতু একটি গড় সূচক তাই মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশে আয়বণ্টনে বৈষম্যও বাড়তে থাকে তাহলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর কাছে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে। ফলে নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রবৃদ্ধির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। অতএব আয়বৈষম্য ক্রমে বাড়তে থাকার প্রবণতাকে দেশের জন্য মহাবিপৎসংকেত বললে অত্যুক্তি হবে না। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো আশির দশক থেকেই এ দেশে আয় ও সম্পদবৈষম্য ক্রমেই বাড়তে বাড়তে এখন বাংলাদেশ একটি ‘উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে’ পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিমাপ করার জন্য নানা পরিমাপক ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে লরেঞ্জ কার্ভ ও জিনি সহগ অন্যতম। কোনো অর্থনীতির জিনি সহগ যখন দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ০.৫-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায় বা ০.৫ অতিক্রম করে তখন নীতিনির্ধারকদের বোঝার কথা যে আয়বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের খানা আয়-ব্যয় জরিপে জিনি সহগ নির্ধারিত হয়েছে ০.৪৮৩। ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে জিনি সহগ পৌঁছে গেছে ০.৪৯৯-এ।
এ ধনাঢ্য সৃষ্টিকারী ও ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর দখলে জিডিপির ক্রমবর্ধমান অংশ পুঞ্জীভূত হতে দেয়ার বিপদ সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর কৌশল কী ফল প্রসব করতে পারে তা আরো নাটকীয়ভাবে ধরা পড়েছে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হেডলাইন সংবাদ ‘বিশ্বে ধনকুবেরের সংখ্যা প্রবৃদ্ধির হারের শীর্ষে বাংলাদেশ’-এর মাধ্যমে। ওই খবরে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ‘ওয়েলথ এক্স’-এর প্রতিবেদন ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট ২০১৮ মোতাবেক ২০১২ সাল থেকে ২০১৭—এই পাঁচ বছরে অতিধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে এক নম্বর স্থানটি দখল করেছে বাংলাদেশ। ওই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ১৭.৩ শতাংশ হারে। ওই গবেষণা প্রতিবেদনে ৩০ মিলিয়ন বা ৩ কোটি ডলারের (৩৫০ কোটি টাকা) বেশি নিট সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের ‘আল্ট্রা-হাই নেট-ওয়ার্থ’ (ইউএইচএনডব্লিউ) ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণ জনগণের কাছে বোধগম্য যেসব বিষয় এ বিপদটার জানান দিচ্ছে সেগুলো হলো: ১. দেশে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ১১ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে মাতাপিতার বিত্তের নিক্তিতে সন্তানের স্কুলের ও শিক্ষার মানে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে; ২. দেশে চার ধরনের মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে; ৩. দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুরোপুরি বাজারীকরণ হয়ে গেছে; ৪. ব্যাংকের ঋণ সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে এবং ঋণখেলাপি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে; ৫. দেশের জায়গা-জমি, অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট, ফ্ল্যাট, মানে রিয়াল এস্টেটের দাম প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে; ৬. বিদেশে পুঁজি পাচার মারাত্মকভাবে বাড়ছে; ৭. ঢাকা নগরীতে জনসংখ্যা ২ কোটি ৩০ লাখে পৌঁছে গেছে, যেখানে আবার ৪০ শতাংশ মানুষ বস্তিবাসী; ৮. দেশে গাড়ি, বিশেষত বিলাসবহুল গাড়ি আমদানি দ্রুত বেড়েছে; ৯) বিদেশে বাড়িঘর, ব্যবসাপাতি কেনার হিড়িক পড়েছে; ১০. ধনাঢ্য পরিবারগুলোর বিদেশ ভ্রমণ বাড়ছে; ১১. উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রবাহ বাড়ছে; ১২. উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য ঘন ঘন বিদেশে যাওয়া বাড়ছে; ১৩. প্রাইভেট হাসপাতাল ও বিলাসবহুল ক্লিনিক দ্রুত বাড়ছে; ১৪. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছে; ১৫. দেশে ইংলিশ মিডিয়াম কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট স্কুল, পাবলিক স্কুল এবং ও লেভেল/এ লেভেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মচ্ছব চলছে; ১৬. প্রধানত প্রাইভেট কারের কারণে সৃষ্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রাফিক জ্যাম নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করছে এবং ১৭. দেশে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি বেড়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে পদে পদে। দুর্নীতিলব্ধ অর্থের সিংহভাগ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।
ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য সমস্যা মোকাবেলা করা দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয়। রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সদিচ্ছা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ আয় ও সম্পদ পুনর্বণ্টন খুবই কঠিন রাজনৈতিক নীতি-পরিবর্তন ছাড়া অর্জন করা যায় না। সমাজের শক্তিধর ধনাঢ্য গোষ্ঠীগুলোর কায়েমি স্বার্থ আয়-পুনর্বণ্টন নীতিমালাকে ভণ্ডুল করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেই। দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, গণচীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, ইসরায়েল ও শ্রীলংকায় রাষ্ট্র নানা রকম কার্যকর আয় পুনর্বণ্টন কার্যক্রম গ্রহণ ও সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জিনি সহগ বৃদ্ধিকে শ্লথ করতে বা থামিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বিশ্বে জিনি সহগ কমানোর ব্যাপারে কিউবা ছাড়া অন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশকে তেমন একটা সাফল্য অর্জন করতে দেখা যাচ্ছে না। এ দেশগুলোর মধ্যে কিউবা, গণচীন ও ভিয়েতনাম এখনো নিজেদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবি করে, বাকি দেশগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসারী হয়েও শক্তিশালী বৈষম্য নিরসন নীতিমালা গ্রহণ করে চলেছে। ওপরের বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে সফল ভূমি সংস্কার এবং/অথবা কৃষি সংস্কার নীতিমালা বাস্তবায়িত হয়েছে। নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির মতো ইউরোপের কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রীয় নীতি অনেক বেশি আয়-পুনর্বণ্টনমূলক, যেখানে অত্যন্ত প্রগতিশীল আয়কর এবং সম্পত্তি করের মতো প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে জিডিপির ৩০-৩৫ শতাংশ সরকারি রাজস্ব হিসেবে সংগ্রহ করে ওই রাজস্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা (প্রধানত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর পেনশন, খাদ্যনিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও আবাসন), পরিবেশ উন্নয়ন, নিম্নবিত্ত পরিবারের খাদ্যনিরাপত্তা, গণপরিবহন, বেকার ভাতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা হয়। এ রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা বাহিনী, সিভিল আমলাতন্ত্র ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর জন্য সরকারি ব্যয় জিডিপির শতাংশ হিসেবে খুবই অনুল্লেখ্য। এ কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোয় এবং বৈষম্য-সচেতন উন্নয়নশীল দেশগুলোয় যে কয়েকটি বিষয়ে মিল দেখা যাচ্ছে সেগুলো হলো:
১. রাষ্ট্রগুলোয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল লেভেলের শিক্ষায় একক মানসম্পন্ন, সর্বজনীন, আধুনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে; ২. রাষ্ট্রগুলোয় অত্যন্ত সফলভাবে জনগণের সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু রয়েছে; ৩. রাষ্ট্রগুলোয় প্রবীণদের পেনশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে; ৪. রাষ্ট্রগুলোয় সর্বজনীন বেকার ভাতা চালু রয়েছে; ৫. এসব দেশে নিম্নবিত্ত জনগণের জন্য ভর্তুকি মূল্যে রেশন বা বিনামূল্যে খাদ্যনিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে; ৬. প্রবীণ জনগণের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্য অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা উন্নত-উন্নয়নশীল নির্বিশেষে এসব দেশে চালু রয়েছে; ৭. এসব দেশে গণপরিবহন সুলভ ও ব্যয়সাশ্রয়ী এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হয়; ৮. এসব দেশে রাষ্ট্র ‘জিরো টলারেন্স অগ্রাধিকার’ দিয়ে দুর্নীতি দমনে কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা চালু করেছে; ৯. এসব দেশ ‘মেগা-সিটি’ উন্নয়নকে সফলভাবে নিরুৎসাহিত করে চলেছে এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসনে খুবই মনোযোগী; ১০. দেশগুলোয় ‘ন্যূনতম মজুরির হার’ নির্ধারণ করে কঠোরভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা চালু রয়েছে; ১১. নিম্নবিত্তদের আবাসনকে সব দেশেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে; ১২. এসব দেশে কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান তার জন্যে কার্যকর সরকারি নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে; ১৩. ব্যক্তি খাতের বিক্রেতারা যেন জনগণকে মুনাফাবাজির শিকার করতে না পারে সেজন্যে এসব দেশে রাষ্ট্র কঠোর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।
এক্ষেত্রে ভারতের কেরালা মডেল বাংলাদেশের জন্য অনুসরণীয় মডেল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। সত্তর দশক থেকেই কেরালা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে উন্নয়নের ‘কেরালা মডেলের’ জন্যে। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অনন্য নজির ‘কেরালা মডেলের’ প্রধান ডাইমেনশনগুলো নিচে উল্লিখিত হলো: ক্রয়ক্ষমতার সাম্য (পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি) ভিত্তিতে মাথাপিছু জিডিপি, সাক্ষরতার হার, শিক্ষার সব পর্যায়ে অভিগম্যতার হার এবং জনগণের গড় প্রত্যাশিত আয়ুর ভিত্তিতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) কর্তৃক প্রকাশিত মানব উন্নয়ন সূচকের স্কোরে কেরালা ভারতের সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে এইচডিআই প্রথম প্রকাশিত হওয়ার বছর ১৯৯০ সাল থেকেই এবং প্রথম থেকেই অনেক উন্নত দেশের চেয়ে কেরালার র্যাংকিং ছিল উঁচুতে। শিশুমৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, জন্মহার, মৃত্যুহার, মোট প্রজনন হার, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার, সকল পর্যায়ের শিক্ষিতের হার, মৌল স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা, ভর্তুকি দামে খাদ্য-রেশন ও ফিডিং ব্যবস্থা, চিকিৎসক-জনসংখ্যা অনুপাত—এ ধরনের তাবত সামাজিক সূচকেও কেরালা অনেক উন্নত দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। আড়াই দশক আগেই কেরালার জনসংখ্যা প্রতিস্থাপন (রিপ্লেসমেন্ট) লেভেলে পৌঁছে গেছে। কেরালার জনগণ প্রায় শতভাগ মৌল স্বাস্থ্য সুবিধা ও চিকিৎসা সুবিধার আওতায় চলে এসেছে, রাজ্যে ২৭০০-এর বেশি সরকারি ক্লিনিক/হাসপাতাল রয়েছে। এক লাখ জনসংখ্যার জন্যে কেরালায় ৩০০ হাসপাতাল বেড রয়েছে, যা ভারতে সর্বোচ্চ। কেরালার নিম্ন আয়ের মানুষ বিপুল ভর্তুকি দামে রেশনের চাল কিনছে। কেরালার সব প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের আওতায় চলে এসেছে। কেরালার সব প্রবীণ কৃষক মাসিক পেনশন পান। কেরালার গ্রামীণ পরিবারের ৮৫ শতাংশ পাইপলাইনের পানি সরবরাহের আওতায় এসেছে। আরো চমকপ্রদ হলো মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মানব পুঁজি রফতানির ক্ষেত্রে কেরালা ভারতে চ্যাম্পিয়ন। কেরালার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রবাসীদের ক্রমবর্ধমান রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাও কেরালার আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকেও কেরালাই ভারতের পথিকৃৎ।
মাথাপিছু জিডিপি বেশি না হলেও যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতের মতো একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশেও ঈর্ষণীয় জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, কেরালার জনগণ তৃতীয় বিশ্বে তার সফলতম নজির সৃষ্টি করেছে। ন্যায়বিচার সমুন্নতকারী প্রবৃদ্ধি (ইকুইট্যাবল গ্রোথ) মডেলের এক অনন্য নজির কেরালা। আয় ও সম্পদবৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখে জনগণের মাথাপিছু জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে দ্রুত বাড়িয়ে চলেছে রাজ্যটি। কেরালায় পরমতসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের মাধ্যমে এই দুটো জোট পালাক্রমে ক্ষমতায় এলেও কোনো সরকারই পূর্ববর্তী সরকারের গণমুখী পরিবর্তনগুলোকে ছুড়ে ফেলে না, নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। ১৯৬৯ সালে একটি কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন সরকার কেরালায় ‘লাঙল যার জমি তার’ নীতির ভিত্তিতে ভূমি মালিকানার ব্যাপক পুনর্বণ্টনের লক্ষ্যাভিমুখী কৃষি সংস্কার আইন পাস করে, যার প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ছিল: ১. কোনো পরিবারকে আট হেক্টরের বেশি জমির মালিকানা রাখতে না দেয়া, ২. বর্গাচাষী ও বর্গাদার কৃষকদের তাদের চাষকৃত জমির প্রকৃত মালিকে পরিণত করা, ৩. মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাত, ৪. কৃষি জোতের একত্রীকরণ এবং ৫. তৃণমূল জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের কৃষি সংস্কারের কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ। কেরালার কৃষি সংস্কারমালা খেতমজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে এবং গ্রামীণ শ্রমজীবী জনগণের সংগঠন জোরদারকরণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পেরেছে, যার ফলে তৃণমূল গণতন্ত্র ও ‘কল্যাণ অর্থনীতি’ প্রতিষ্ঠায় কেরালা মডেল অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।
২০১০ সালে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আবার রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা ২০১১ সালের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এখনো ‘মুক্তবাজার অর্থনীতির’ অহিফেনের মৌতাতে ডুবে রয়েছে সরকার। অনেকেই এখন বর্তমান সরকারকে প্রধানমন্ত্রী ও জনাকয়েক ধনকুবের ব্যবসায়ীর ‘অলিগার্কি’ বলে অভিহিত করছেন। একটি উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য এ রাষ্ট্রচরিত্রই দায়ী। অথচ সমাজতন্ত্রকে ‘বাত্ কা বাত্’ বানিয়ে না রেখে ওপরে উল্লিখিত নীতিমালা এবং বিশেষত কেরালাকে অনুসরণ করলে বাংলাদেশ ক্রমেই আয়বৈষম্য নিরসনের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে।
ড. মইনুল ইসলাম: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়







