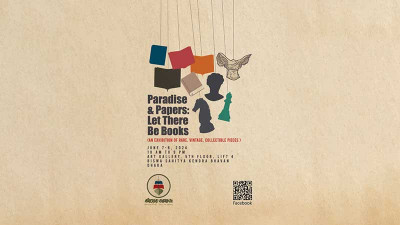ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা কীটপতঙ্গ প্রকৃতির সম্পদ। এরা আমাদের প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। মানুষের জন্য উপকারী ও অপকারী দুই ধরনেরই কীটপতঙ্গ রয়েছে। উপকারী কীটপতঙ্গ সাহায্য করে পরাগায়নে কিংবা মানুষের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বসতি তৈরির কাজে। মৌমাছি গড়ে তোলে মৌচাক; রেশম পোকা তৈরি করে রেশমি সুতার পুত্তলি, আর প্রবাল কীটগুলো মরে গিয়ে প্রবালদ্বীপ হয়ে জেগে ওঠে সাগরের বুকে। আবার অপকারী পোকা ফুল-ফল, সবজি বাগান ও ফসলের ক্ষেতের জন্য বিপদ ডেকে আনে। এরা প্রকৃতির সাজানো বাগান আর মানুষের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা ফসলের মাঠকে বিরান করে দিতে পারে। পঙ্গপালের আক্রমণ একটা দেশের ফসলকে ধ্বংস করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। আবার মশা-মাছি, ছারপোকা এসব কীটপতঙ্গ বহন করে নানা রোগজীবাণু।
আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে মানুষ ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে কীটপতঙ্গ দমনে নানা উপায় খুঁজতে শুরু করে। শুরুতে তারা এ কাজের জন্য ব্যবহার করতে থাকে গবাদিপশুর মূত্র বা তামাকপাতাসহ নানা প্রাকৃতিক উপাদান। কিন্তু ‘কীটনাশক’ বলতে আজ কেবল রাসায়নিক কীটনাশককে বোঝায়। ‘কীটনাশক’ ছড়ানোর পর তা গাছের কাণ্ড ও পাতায় লেগে থাকে। কিছু কীটপতঙ্গ সেসব গাছের কাণ্ড বা পাতার রস চুষে খায়। তখন কীটনাশকের সূক্ষ্ম কণাগুলো কীটপতঙ্গের দেহে প্রবেশ করে এদের মৃত্যু ঘটায়। আবার যেসব কীটপতঙ্গ গাছের কাণ্ড বা পাতা খায় না কিন্তু সংস্পর্শে আসে, তাদের লোমকূপ দিয়ে কীটনাশক ঢুকে পড়ে; ফলে পতঙ্গগুলো মারা যায়। রাসায়নিক কীটনাশক দীর্ঘ সময় কাজ করে বলেই পোকার বারবার আক্রমণের মুখেও গাছ বা ফসলকে রক্ষা করা যায়।
কীটনাশক তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। বস্তুত এ সময় ডিডিটি ও বিএইচসি নামে দুটি রাসায়নিক কীটনাশকই বিস্ময় সৃষ্টি করে বিশ্বজুড়ে। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনে এ দুটি কীটনাশক অবিশ্বাস্য রকমের ফল দেয়। আর তাতে রক্ষা পায় বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, ফুল ও ফলের বাগান। ঘাতক মশা-মাছির হাত থেকেও রক্ষা পায় মানুষ। এতে প্রতিহত হয় নানা রোগের বিস্তার। কিছু দিনের মধ্যেই ডিডিটি ও বিএইচসি প্রাণিজগতের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিল। এসব কীটনাশকের বিষে কেবল অপকারী কীটপতঙ্গই মরেনি, মরেছে অগণিত উপকারী কীটপতঙ্গ। কীটনাশকের বিষে মরা কীটপতঙ্গ খেয়ে মরেছে পাখিরা। ধান, পাট ও গমের ক্ষেতে ছিটানো কীটনাশকের বিষ বৃষ্টি, সেচ ও বানের পানিতে পুকুর ও জলাশয়ে গিয়ে পড়েছে, ফলে মরেছে মাছ। আর সেসব মাছ খেয়ে মানুষ ভুগেছে নানা জটিল রোগে। আবার দেখা গেল ডিডিটি প্রকৃতিতে কোনোভাবেই বিনষ্ট হয় না, এদের বিষক্রিয়া থেকে যায় যুগ যুগ ধরে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ডিডিটির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পরবর্তী সময়ে ভারত ব্যতীত পৃথিবীর সব দেশ ডিডিটি নিষিদ্ধ করে।
সব ধরনের পেস্টিসাইড বা বালাইনাশক মূলত বিষ, যা ব্যবহার হয় ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড়, জীবাণু, আগাছা ও ইঁদুর মারার জন্য। বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইডের মধ্যে রয়েছে ইনসেক্টিসাইড বা কীটনাশক, ফানজিসাইড বা ছত্রাকনাশক, উইডিসাইড/হার্বিসাইড বা আগাছানাশক, মাইটিসাইড বা মাকড়নাশক এবং রোডেন্টিসাইড বা ইঁদুর মারার বিষ। বাংলাদেশে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কীটনাশক ব্যবহার হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫৬ সালে সরকার বাংলাদেশ ভূখণ্ডের জন্য দুই টন কীটনাশক আমদানি করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কীটনাশকে শতভাগ ভর্তুকি দেয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সালে ভর্তুকি পুরোপুরি প্রত্যাহার করে ১৯৮০ সাল থেকে বেসরকারি খাতে কীটনাশক আমদানির অনুমতি দেয়। শুরুর দিকে কীটনাশক ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের একটি স্লোগান ছিল—‘বোকার ফসল পোকায় খায়’। সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রচারণায় স্বল্প সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বালাইনাশকের ব্যবহার। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০—এ সময়ে বাংলাদেশে কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ে প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৮৫-৮৬ সালে ব্যবহৃত কীটনাশকের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৬৩ টন, যা ১৯৯০-৯১ সালে বেড়ে হয় ৬ হাজার ৯৪৮ টন। ১৯৯৯ সালে দেশে বালাইনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার ৩৪০ টন, যা ২০০৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৮ হাজার ৬৯০ টনে। যদিও ২০১৭ সালে এ পরিমাণ কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৩৭ হাজার ২৫৮ টনে। ওই হিসাবের বাইরে প্রতি বছর চোরাইপথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে আসছে প্রচুর পরিমাণ কীটনাশক যেগুলো পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর।
সাম্প্রতিক সময়ে সরজমিন পরিদর্শনে বাংলাদেশের কৃষিজমির জীববৈচিত্র্যের যে চিত্র উঠে আসে তা এক কথায় ভয়াবহ। কৃষিজমি বিশেষ করে ধানের জমিতে একসময় শামুক-ঝিনুক ও বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ দেখা যেত। এখন এগুলো অনেকটা অনুপস্থিত। প্রকৃতির নাঙল বলা হয় যে কেঁচোকে তাও এখন আর কৃষিজমিতে পাওয়া যায় না। ফসলের জমিতে পোকামাকড় খাওয়ার জন্য পাখ-পাখালির বিচরণ কমে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। ফসলের মাঠে ফুল থেকে মধু সংগ্রহে ব্যস্ত মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জনও কমে গেছে নানা বিষাক্ততায়। এছাড়া কৃষি পরিবেশে বিদ্যমান নানা সরীসৃপ আজ বিলুপ্তপ্রায়। এরই মধ্যে ১২ প্রজাতির সরীসৃপ ও আট প্রজাতির উভচর প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ফসলের জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অব্যাহতভাবে কমে যাওয়ায় এবং রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক ব্যবহারে মাটিতে বিভিন্ন উপকারী অণুজীব আর বেঁচে থাকতে পারছে না। অন্যদিকে অব্যাহতভাবে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের কারণে নতুন প্রজাতির পোকার জন্ম হচ্ছে, যা প্রচলিত মাত্রায় কীটনাশক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। সাম্প্রতিক সময়ে ফসলের জমিতে আগাছানাশকের ব্যাপক ব্যবহার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতিকেও হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগাছানাশকের ব্যবহারের কারণে ভবিষ্যতে নতুন প্রজাতির আগাছার উদ্ভব ঘটবে, যা কোনোভাবেই দমন করা যাবে না।
দেশে ব্যবহৃত কীটনাশকের মধ্যে কয়েকটি অতি উচ্চমাত্রায় বিষাক্ত যেগুলো মানুষ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কীটনাশকগুলো ‘ডার্টি ডজন’, ‘পপস্’ বা ‘ন্যস্টি নাইন’ নামে পরিচিত। এদের সংখ্যা ৯ থেকে ১৮টি। শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশে রেসিডুয়াল ইফেক্টের কারণে এসব বালাইনাশক নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে এর অনেকগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বে লাল তালিকাভুক্ত চরম বিষাক্ত কীটনাশকগুলো নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো অধিক মুনাফার আশায় এসব অতি ক্ষতিকর কীটনাশক আমদানি ও বাজারজাত করছে।
ব্যবহৃত কীটনাশকের ৩০ ভাগই মৌমাছির জন্য ক্ষতিকর। তবে সর্বাধিক ক্ষতিকর হলো নিওনিকোটিনয়েড গোত্রের কীটনাশকগুলো। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোসহ আরো বেশ কয়েকটি দেশ ২০১৩ সাল থেকে এ গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার সীমিত করে। পরবর্তী সময়ে মৌমাছি সুরক্ষায় ২০১৮ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিওনিকোটিনয়েড গোত্রভুক্ত তিনটি প্রধান গ্রুপ যথা: ইমিডাক্লোপ্রিড, ক্লোথিয়ানিডিন ও থিয়ামেথোক্সাম গ্রুপের সব কীটনাশকের উন্মুক্ত ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে। এগুলো পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত কীটনাশকগুলোর অন্যতম। এছাড়া পাইরিথয়েড, কার্বামেট, অর্গানোফসফেট গ্রুপের কীটনাশক এবং ক্লোরোথালোনিল গ্রুপের ছত্রাকনাশকগুলো মৌমাছির জন্য বেশ ক্ষতিকর।
নিওনিকোটিনয়েড গোত্রের কীটনাশকগুলো মৌমাছির স্নায়ুতন্ত্রে আক্রমণ করে, ফলে মৌমাছি কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মৌমাছির শরীর অবস হয়ে যায়, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। অনেক সময় মৌমাছির স্মৃতি লোপ পায়, ফলে মৌচাকে ফিরে আসতে পারে না। এছাড়া এসব কীটনাশকের কারণে মৌমাছির প্রজনন ক্ষমতা লোপ পায়, বিশেষ করে রানী মৌমাছির সংখ্যা কমে যায়। রানী মৌমাছির ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে মৌমাছির কলোনিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা নতুন কলোনি গড়ে ওঠে না। এসব কীটনাশকের ব্যবহারের কারণে আমাদের দেশে মৌমাছির কর্মক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে কর্মী মৌমাছি, যারা ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে থাকে।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ওই গোত্রের কীটনাশকগুলো নিষিদ্ধ করার জোর দাবি উঠেছে। মৌমাছি সুরক্ষায় এসব দেশে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠছে। বাংলাদেশে বহুজাতিক পেস্টিসাইড কোম্পানিগুলো উল্লিখিত নিওনিকোটিনয়েড গোত্রের তিনটি গ্রুপের কীটনাশক ব্যাপকভাবে বাজারজাত করে থাকে। ২০১৫ সালের তথ্যমতে, দেশে শুধু ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক রয়েছে ১৮০টি। অর্থাৎ দেশের প্রায় সব বালাইনাশক কোম্পানি এ কীটনাশক বাজারজাত করে থাকে।
আমাদের ফল-ফসলের অধিকাংশই পরপরাগী। অর্থাৎ পরাগায়নের জন্য কীটপ্রতঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। আর এসব কীটপ্রতঙ্গের মধ্যে পরাগায়নে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে মৌমাছি। প্রাকৃতিক নিয়মে কীটপ্রতঙ্গ খাবার সংগ্রহে ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এর মাধ্যমে ফুলের পরাগরেণু পোকামাকড়ের গায়ে লেগে এক ফুল থেকে অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় এবং পরাগায়ন ঘটায়। এতে ফুল থেকে ফল ও বীজ হয়, যা আমরা ফসল হিসেবে পেয়ে থাকি। পরাগায়ন না হলে কোনো ফসল উৎপাদন সম্ভব নয়। এজন্য গ্রিনহাউজে ফসল চাষের ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে পরাগায়ন ঘটানো হয়। পরাগায়নের হার যত কমবে ফসলের ফলনও তত কমবে। ধরুন দেশে যদি মৌমাছির সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যায়, তখন মানুষের পক্ষে কি সম্ভব হবে এ বিস্তর পরিবেশের ফল-ফসল আর উদ্ভিদের পরাগায়ন কৃত্রিম বা যান্ত্রিকভাবে করা! আর তখন ফসলের উৎপাদন খরচ কতটা বাড়বে, তাও চিন্তার বিষয়। মৌমাছি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের ফসল উৎপাদনের স্বার্থেই মৌমাছি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। পরাগায়ন ছাড়াও মৌমাছি থেকে আমরা মধু পাই, যা অনেক প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকার সূত্র।
তাহলে সমাধান কোন পথে। ফসল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার প্রয়োজন রয়েছে। তবে মৌমাছির জন্য অধিকতর ক্ষতিকর কীটনাশকগুলোর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা উচিত। মৌমাছি ফসলের মাঠে দিনের বেলা সক্রিয় থাকে। তাই বিশেষজ্ঞরা মৌমাছি সুরক্ষায় অতি ক্ষতিকর কীটনাশকগুলো ফসলের জমিতে সন্ধ্যা বা রাতে প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন। পৃথিবীর অনেক দেশে ফসলে ফুল আসার পর নিওনিকোটিনয়েড গোত্রের কীটনাশকগুলো প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের দেশেও পরপরাগী ফসলে ফুল আসার পর থেকে বীজ হওয়া পর্যন্ত ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশকগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। এতে মৌমাছির ওপর এগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কমবে।
রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার দ্বারা ফসল রক্ষা এবং অতিরিক্ত উৎপাদন হলেও এর বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ায় যে স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং পরিবেশ দূষিত হয়, তাতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি হচ্ছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই রাসায়নিক কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কৃষক সমাজ তথা সমগ্র জনগণকে অবহিত ও সচেতন করতে হবে। প্রচলিত কীটনাশকের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে ক্ষতিকর, সেগুলো চিহ্নিত করে উৎপাদন, আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া কীটনাশক সংক্রান্ত আইনের সঠিক ও বাস্তব প্রয়োগের পাশাপাশি আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা প্রয়োজন। কৃষিবিদদের মতে, রাসায়নিক বালাইনাশকের পরিবর্তে জৈব বালাইনাশক ও আইপিএম পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপায়ে বালাই দমন করা সর্বোত্তম। এতে অর্থের সাশ্রয় হবে, ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষিত হবে।
কীটনাশকের নাশকতায় উপকারী ও অপকারী দুই ধরনের কীটপতঙ্গ মরছে। মরছে সাপ, ব্যাঙ ও মাছ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে এসব প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। জীবজগতের খাদ্যশৃঙ্খলে এরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কীটপতঙ্গ দমনে একসময় ঐতিহ্যবাহী লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার করে প্রতিবেশের ভারসাম্যের কাজ সুন্দরভাবে চালানো যেত। আশার কথা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং এনজিওদের উদ্যোগে কৃষিকাজে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে কৃষকের খরচও কমবে এবং পরিবেশ ভালো থাকবে। এ লোকজ জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে—ক্ষেতে কঞ্চি ও ডালপালা ইত্যাদি পুঁতে রাখলে তাতে পাখি বসে ক্ষেতের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেতে পারে ও কুপি বা মশাল জ্বালিয়ে পোকা ফাঁদে ফেলে মারা প্রভৃতি। পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সারা দেশে সমন্বিত বালাই দমন আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই দেশ প্রতিবেশ পরিবেশ জীববৈচিত্র্য কীটনাশকতার ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।
আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ: অধ্যাপক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।