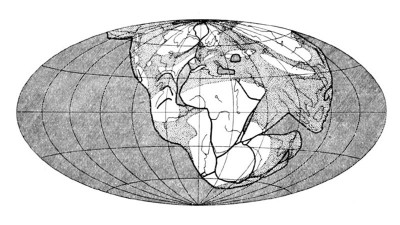মহাস্থানগড় থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোকুল গ্রামে ‘গোকুল মেড়’ নামক যে অনিন্দ্য প্রত্ন স্থাপনাটি রয়েছে—সাধারণ্যে সেটি ‘বেহুলার বাসরঘর’ নামে পরিচিত। এটি ছাড়াও মহাস্থানগড়ের আশপাশে প্রায় ছয়-সাত কিলোমিটারের মধ্যে গোকুল, পলাশবাড়ী, চিঙ্গাসপুর, চাঁদমুহা, রামশহর, শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রামে অবস্থিত বেশ কয়েকটি প্রত্ন স্থাপনার সঙ্গে বেহুলা কাহিনী জড়িয়ে আছে। এগুলো হলো মঙ্গলকোট বা পদ্মার বাড়ি, নেতাই ধোপানির ধাপ বা পাট, চাঁদ সদাগরের বাড়ি, ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি, উজানীনগর, কালীদহ সাগর, খুল্লনার ধাপ, লহনার ধাপ, যোগীর ভবন ইত্যাদি। বগুড়া জেলায়ই শুধু নয়, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মনসাসংক্রান্ত এ ধরনের তিন শতাধিক স্থান-নাম রয়েছে (আশুতোষ ভট্টাচার্য ২০০২)। মনসা বা বেহুলাসংক্রান্ত স্থাননামের এ আধিক্য সম্পর্কে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ (১৮৯৬) গ্রন্থে বলেছেন: ‘মনসার ভাসান এক সময়ে (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দ) বঙ্গীয় জনসাধারণের এতদূর প্রিয় ছিল যে এতদ্দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্তী জল্পনা করিয়া সুখানুভব করিত।’ পনেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত প্রায় সমগ্র বাংলায় মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যধারা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এ সময়ে শতাধিক কবি বাংলা, বিহার ও আসাম অঞ্চলে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন। স্থানীয় এসব কবির কাব্যকীর্তির প্রভাবে স্থানীয় জনপদে বেহুলাসংক্রান্ত অসংখ্য স্থাননাম ও মিথের সৃষ্টি হয়। উত্তরবঙ্গে মনসামঙ্গলকাব্য ধারার উল্লেখযোগ্য তিনজন কবি হলেন—মালদা-মুর্শিদাবাদের তন্ত্রবিভূতি (সতেরো শতক), কোচবিহার-জলপাইগুড়ির জগৎজীবন ঘোষাল (সতেরো শতক) এবং বগুড়ার জীবনকৃষ্ণ মৈত্র (আঠারো শতক)। শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, সমকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজেও এসব কবির কাব্যকীর্তির গভীর প্রভাব পড়েছিল। কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র আঠারো শতকের প্রথম দিকে মহাস্থানের পূর্ব পাশে লাহিড়ী পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ‘মনসার ভাসান’ বা ‘বিষহরি পদ্মাপুরাণ’ রচনা করেন। কবি দরিদ্র ছিলেন বলে স্থানীয় হাটে-বাজারে মনসার ভাসান গেয়ে এবং পুথি বিক্রি করে সংসার চালাতেন। জীবন মৈত্রের ‘পদ্মাপুরাণ’ বিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুদ্রিত হলেও প্রকাশিত হয়নি। লিপিকর কর্তৃক তার তিনটি পুথি (পুথি নং- ২৮১৭, ৩১৮০ ও ৬১১৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। বগুড়া উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরিতেও জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণের একটি পুথি আছে। অযত্ন ও অবহেলায় বর্তমানে পুথিটি প্রায় ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বগুড়ায় জীবন মৈত্র সম্পর্কে প্রচলিত একটি জনশ্রুতি এ রকম যে তিনি একবার আড়িয়া বাজারে (শাজাহানপুর উপজেলার একটি গ্রাম) মনসার ভাসান গাইতে এসেছিলেন। ভাসান গাওয়া শেষ হলে কেউ আর কবির খোঁজ নেয়নি। অভুক্ত কবি মনের দুঃখে যাওয়ার সময় গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে যান: আড়িয়া গাঁয়ের গাইরা মরদ/ মাগীর কামায় খায়। জীবন মৈত্র গাইতে আস্যা/ উবাস পার্যা যায়। (কর্ণপুরী, ১৯৬৮) মহাস্থান এলাকায় বেহুলার যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তার সঙ্গে জীবন মৈত্রের ‘পদ্মাপুরাণে’র কাহিনীর হুবহু মিল পাওয়া যায়। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জীবন মৈত্র অথবা মনসামঙ্গলকাব্যের প্রভাবে সমকালীন অনুকূল হাওয়ায় সতেরো-আঠারো শতকের দিকে মহাস্থান তথা কবির জন্মভূমির আশপাশে বেহুলাসংক্রান্ত উপর্যুক্ত স্থান-নামগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগে বৈষ্ণবীয় ও মঙ্গলকাব্যধারার (চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালীকামঙ্গল, শিবমঙ্গল প্রভৃতি) দেব-দেবীর প্রভাবে সমগ্র বাংলায় অসংখ্য স্থাননামের উদ্ভব ঘটে। মহাস্থানগড়ের আশপাশের নামগুলোও হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে মাহাত্ম্যসূচক। যেমন বৃন্দাবন (পাড়া), মথুরা, গোকুল (গোবর্ধনপুর), কৃষ্ণপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, বারানসী, গুপ্তবারানসী, গোপালবাড়ি, কালীদহ সাগর, কালিবালা, অনন্তবালা, রাধাধাম, শীলা ও নেতারপাট, চাঁদমুহা, হরিপুর প্রভৃতি। যে রাজনৈতিক কারণে বাংলা মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, সেই একই কারণে অর্থাৎ তুর্কি বিজয়ের (এখানে শাহ সুলতানের বিজয়) একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব এ ধরনের নামকরণের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল। বিজিত জাতি (স্থানীয় হিন্দু) পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে মানসিক যাতনায়—হৃত গৌরব ও ঐতিহ্যের অহংচূর্ণ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে উদ্বেলিত হয়ে—এসব স্থানিক নামের মাহাত্ম্যে ডুব দেয়। মানুষ যখন নিজের কোনো কিছু হারায় কেবল তখনই হারানো বস্তু বা বিষয়ের জন্য হাহাকার করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে তখনকার স্থানীয় হিন্দু সমাজ ধর্মীয় ঐতিহ্যে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু দেবমাহাত্ম্যসূচক একাধিক স্থান নামের উদ্ভব ঘটে। এ ধারা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের সময় (পদাবলী-মঙ্গলকাব্যধারা বিকাশের যুগ) থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে মহাস্থানগড়ের পশ্চিম প্রান্তে মঙ্গলকোটে প্রত্নখননে কিছু সর্পমূর্তির নিদর্শনপ্রাপ্তি স্থান-নামগুলোর প্রচারে ব্যাপ্তি দিয়েছে। মঙ্গলকোট উৎখননে একাধিক সর্প ফণা-ধরাযুক্ত নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ফলে এটি হয়েছে পদ্মার বাড়ি। পৃথিবীর আদিমতম পূজার একটি সর্পপূজা। জঙ্গলাকীর্ণ ও নিম্ন জলাভূমির দেশ বাংলাদেশেও প্রচলিত রয়েছে সর্পপূজা এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠেছিল মনসা মন্দির। মঙ্গলকোটের আদি প্রত্নস্থাপনার (বৌদ্ধ স্থাপত্য) ওপর পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো একসময় হয়তো মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে কারণে এখানে একাধিক সর্পমূর্তি পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের পাশেই রয়েছে কালীদহ বিল। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের কারণে এর পানি সব সময় কালো থাকত বলে সেটি হয়েছে কালীদহ সাগর। উজানী খালের কিছু অংশের জলপ্রবাহ উত্তর দিকে প্রবাহিত হতো বলে সেটি হয়েছে উজানীনগর ইত্যাদি। ১৯৩৪-৩৬ খ্রিস্টাব্দে গোকুল মেধ খননের পর চূড়ায় একটি চৌকোনা আকৃতির আবদ্ধ কক্ষ এবং তার ভেতর চার কোনায় চারটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হয়। ফলে এ কক্ষ ও ছিদ্রের কারণে এবং অত্র এলাকায় অবস্থিত বেহুলাসংক্রান্ত অন্য স্থান-নামগুলোর প্রভাবে পরবর্তীকালে লোকমুখে এটি বেহুলার বাসরঘরের স্বীকৃতি পায়। এক্ষেত্রে মিথ সৃষ্টির পেছনে সাদৃশ্যবাদী জনমনস্তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভূমিকাটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন (স্বল্প পরিসরের এ লেখায় বিষয়টি এখানে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো না)। বগুড়ার প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে কালীকমল সার্বভৌমর ‘সেতিহাস বগুড়ার বৃত্তান্ত’ (১৮৬১), ডব্লিউডব্লিউ হান্টারের A statistical Account of Bengal – Bogra District (1876), জেএন গুপ্তের District Gazetteers of Eastern Bengal & Assam - BOGRA (1910), প্রভাসচন্দ্র সেনের ‘বগুড়ার ইতিহাস’ (১৯১৩/১৯২৯), হরগোপাল দাস কুণ্ডুর ‘পৌণ্ড্রবর্ধন ও করতোয়া’ (১৯১৯) প্রভৃতি গ্রন্থে চাঁদনিয়া-চম্পাইনগর, উজানীনগর, চাঁদ সদাগর, বেহুলা সুন্দরী, লখিন্দরের কথা থাকলেও কোথাও বেহুলার বাসরঘরের কথা নেই। গোকুল মেধ সম্পর্কে প্রভাসচন্দ্র সেন লিখেছেন, ‘গোকুল গ্রামে অবস্থিত মেড় (মন্দির) নামক একটি প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চ ইষ্টকময় স্তূপ অদ্যাপী দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে’। কাজী মোহাম্মদ মিছের ‘বগুড়ার ইতিকাহিনী’তে (১৯৫৭) লিখেছেন, ‘প্রচলিত প্রবাদ এই রূপ ইহা লক্ষীন্দরের মেড়’ (পৃ. ১০২)। ১৯৩৪-৩৬ খ্রিস্টাব্দের আগে এটি যদি বেহুলার বাসরঘর রূপে পরিচিতি পেত তাহলে পূর্ববর্তী লেখকদের লেখায় অবশ্যই তার উল্লেখ থাকত। বেহুলার বাসরঘরের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান-নাম তাদের লেখায় বাদ পড়ত না। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে ১৯৩৪-৩৬ খ্রিষ্টাব্দের পরই বেহুলার বাসরঘরের নামটি মিথ আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার উৎস নিঃসন্দেহে মহাস্থানের স্থানীয় কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র এবং তার ‘পদ্মাপূরাণ’। ঐতিহাসিকভাবে এ স্থাপত্য একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত শাসনামলে স্তূপীকরণ পদ্ধতিতে এটি নির্মিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ১৭২টি বদ্ধ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ১৩ মিটার উচ্চতার এবং ৭৭X৫৩ মিটার আয়তনের এ বৌদ্ধ স্থাপত্যে পরবর্তীকালে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন শাসনামলে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী শাসকদের সময় এটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত ছিল। ১৯৩৪-৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এটি জনসম্মুখে উন্মুক্ত হয়। মহাস্থানের আশপাশে সতেরো-আঠারো শতকে সৃষ্ট মনসাসংক্রান্ত অন্য স্থান-নামগুলোর (চাঁদনিয়া বা চাঁদমুহা, উজানীনগর, কালীদহ সাগর, নেতাই ধোপানির ধাপ বা পাট ইত্যাদি) প্রভাবে এটি ‘বেহুলার বাসরঘর’ নাম ধারণ করে এবং মিথ আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। (বিস্তারিত দেখুন: ড. বেলাল হোসেন, বাংলা একাডেমি পত্রিকা ৫৩: ২, জানু-জুন ২০০৯ পৃ. ১২৫-১৪১ এবং রবীন্দ্র জার্নাল ৪: ১ অক্টোবর ২০১২, পৃ. ৬৬-৮২) ড. বেলাল হোসেন: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ উপাধ্যক্ষ, সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া
গোকুল মেধ ছবি: শাফিউল ইসলাম সৈকত/ উইকিমিডিয়া কমনস