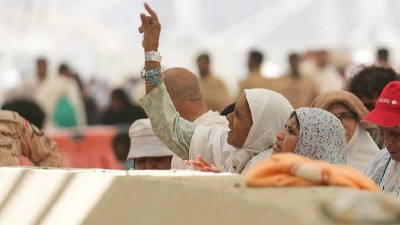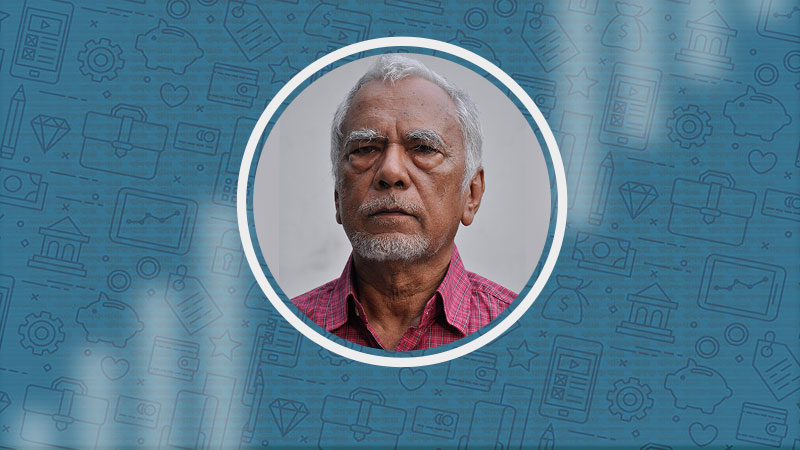 ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা ব্যাংক নিজে নিজে ব্যর্থ হয় না, ব্যাংককে ব্যর্থ করানো হয় অথবা ব্যর্থ হতে দেয়া হয়। ব্যাংক চালায় মূলত উদ্যোক্তাদের দ্বারা গঠিত পরিচালনা বোর্ড। ব্যাংকের প্রধান কার্যনির্বাহী যিনি সিইও বা এমডি নামে পরিচিত তিনিও বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যাংকার। আগে সিইও সাহেব বোর্ডের হাতের পুতুল ছিলেন, বোর্ড চাইলেই সিইওকে বাদ দিতে পারত। পরে অবশ্য বাংলাদেশ ব্যাংক সিইওকে অনেক ক্ষমতায়ন করেছে। এখন বোর্ড চাইলেই কোনো সিইওকে বাদ দিতে পারে না। রেগুলেশনের মাধ্যমে সিইওর হাতকে শক্তিশালী করা হয়েছে। একই সময় তাকে জবাবদিহির আওতায়ও আনা হয়েছে। অবশ্য এ কাজটি করতে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক সময় নিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বুঝতে সময় নিয়েছে যে ব্যাংকগুলোর বোর্ডে অনেক দুষ্ট লোকও আছে যারা সিইও সাহেবের মাধ্যমে অনেক সুবিধা নেয়ার জন্য সদা তৎপর থাকে। তবে এখনো যে সব সিইও একই রকম স্বাধীনতা ভোগ করেন তা কিন্তু নয়। নির্ভর করছে যাকে সিইও পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তিনি স্বাধীন থাকতে চান কিনা। কিছু কার্যনির্বাহী আছেন যারা পরাধীন থাকতে পছন্দ করেন এবং এখনো আগের মতো বোর্ড সদস্যদের স্যার স্যার বলে জান পেরেশান করেন। এদের যত স্বাধীনতাই দেয়া হোক না কেন কোনো কাজ হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংককে সিইওদের কার্যাবলি এবং সফলতা-ব্যর্থতার ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। এখন তো আবার বাংলাদেশ ব্যাংক সিইওদের পরীক্ষা (ইন্টারভিউ) নেয়া শুরু করেছে। তবে কাজটি অপছন্দনীয়। কে সিইও হিসেবে ভালো করবে, কে অনিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তা বাংলাদেশ ব্যাংক আগে থেকেই জানার কথা। তাদের পরীক্ষার নামে খাটো করার প্রয়োজন নেই। ব্যাংক ভালো হতে সময় লাগে, তবে খারাপ হতে বেশি সময় লাগে না। আর একটা সত্য হলো, আর্থিকভাবে অসফল ব্যাংকগুলো আরো খারাপের দিকে যাওয়া যত সহজ, ভালোর দিকে যাওয়া অনেক কঠিন। কারণ ব্যাংক চলে বিশ্বাসের দ্বারা, বিশেষ করে আমানতকারীদের বিশ্বাসের দ্বারা। এক যুগ আগেও আমানতকারীরা আমানত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর মধ্যে পার্থক্য করত না। আর এখন তা খোঁজে কোন ব্যাংক তাদের আমানতের জন্য নিরাপদ। সুদ যে ব্যাংক বেশি দেয় সেই ব্যাংক তাত্ত্বিকভাবে বেশি আমানত পাওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে এখন বিষয়টা সে রকম নয়। এখন লোকে দেখে প্রথমে তাদের অর্থের নিরাপত্তা, পরে দেখে সুদের হার। শুধু নিরাপদ ভেবেই বহু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে বিদেশী ব্যাংকের ঢাকা ব্রাঞ্চে অর্থ জমা রাখছে। অথচ এসব জমায় তারা খুবই সামান্য সুদ পাচ্ছে। ব্যর্থ ব্যাংকগুলোকে অনেক বেশি সুদ দিয়ে আমানত নিতে হচ্ছে, ফলে তাদের ব্যবসা ব্যয় অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা অর্থ নিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে লাভও করছে কম। কম লাভের এ চক্র থেকে ওপরে ওঠা সত্যি বড় কঠিন।
এর অন্য অর্থ, ব্যাংকের সুনাম হলো বড় সম্পদ। দুর্নাম হলো বড় ভারী এক বোঝা। কোনো কোনো ব্যাংক আগে অনেক ভালো ছিল, কিন্তু বর্তমানে পানির ওপর নাকটা তুলে শ্বাস নিচ্ছে। এরা তাদের ক্ষুদ্র শেয়ারহোল্ডারদের তথা ব্যাংকের ক্ষুদ্র হাজার হাজার মালিককে এক রকম ডিভিডেন্ড বা মুনাফা দেয়া বন্ধ করেই দিয়েছে। অথচ এসব ক্ষুদ্র শেয়ারধারীরাই ব্যাংকের ৭০ শতাংশ পুঁজির জোগানদাতা। শুধু ৩০ শতাংশ শেয়ারের ধারণকারীরা উদ্যোক্তা সেজে ব্যাংক বোর্ডের সদস্য হয়ে বসে অন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে। ব্যাংকে বসে এদের অনেকে ঋণ পাইয়ে দিতে তদবিরও করে বলে শোনা যায়। জানি না এ তদবিরও অর্থের বিনিময়ে ঘটে কিনা। ব্যাংকের অনেক মিটিংয়ে তারা অংশগ্রহণ করেন এবং আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে নাস্তা পানি বা বিস্কুট সবকিছুরই সুবিধা পান। কিন্তু কোনো রকম সুবিধা পান না ওইসব ব্যাংকের ক্ষুদ্র পুঁজি জোগানদাতারা। তারা বসে থাকেন কখন এপ্রিল মাস আসবে, কখন তাদের ব্যাংক একটা ভালো মুনাফা প্রদানের ঘোষণা দেবে। অবশেষে তারা হতাশ হয়ে পড়েন যখন দেখা গেল তাদের ব্যাংক শুধু ২ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ মুনাফা ঘোষণা করেছে। কোনো কোনো ব্যাংক ৩ শতাংশও মুনাফা ঘোষণা করেছে। হায়রে ব্যাংক ব্যবসা! তুমি আমানত নিচ্ছো ১২ শতাংশ সুদ দিয়ে অথচ যারা তোমার ব্যবসায় পুঁজি দিল, তাদের দিচ্ছো শূন্য শতাংশ মুনাফা! আমার এক ছাত্র সে এখন একটি বড় চাকরি করে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, যে ব্যবসায় মুনাফা থাকে না সেটা তো অর্থনীতির সূত্র ধরে বন্ধ হয়েই যাওয়ার কথা, তাহলে বাংলাদেশে অনেক ব্যাংক কোনো রকম ব্যবসা না করে চলছে কীভাবে? তার এ প্রশ্নের উত্তর আমিও দিতে পারলাম না। ব্যবসায় লোকসান অথচ ব্যবসা চলছে, এটা কীভাবে সম্ভব? সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ, তাই ব্যাংক ব্যবসাও লোকসান দিয়েই বছরের পর বছর চলছে। আজকে এ ব্যবসার চালকের আসনে যারা বসে আছেন তারা লোকসানকে স্বীকার করতে চান না। লোকসান স্বীকার করলে তো তাদের ব্যাংকে কেউ অর্থ জমা রাখবে না। আর অন্য কথা হলো, ব্যাংক নাই-বা লাভ করল, তাদের তো কিছু লাভ হচ্ছে। সমাজে তারা বলতে পারে, অমুক ব্যাংকের পরিচালক। ব্যাংকের কাজ হলো এক শ্রেণী থেকে অর্থ নিয়ে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অন্য শ্রেণীকে সেই অর্থ দেয়া। কম সুদে অর্থ নিয়ে একটু বেশি সুদে অন্যকে ধার দেয়া। দুই সুদের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাকে বলে সুদের ব্যাপ্তি। এ ব্যাপ্তি থেকেই ব্যাংক সুদ আয় করে। অনেক ব্যাংকের জন্য সুদ আয়ই হলো মুখ্য আয়। ব্যাংক ব্যর্থ হয়েছে মূলত শ্রেণী বিন্যাসকৃত ঋণের ভারে (ক্ল্যাসিফায়েড লোন)। বেশি ব্যবসা করতে গিয়ে অথবা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এমন এমন ঋণ এসব ব্যাংক প্রদান করেছে যে, তাদের শ্রেণীকৃত ঋণ এখন তাদের শুধু নিচেই নামিয়েছে।
একদিকে বদনাম, অন্যদিকে শ্রেণীকৃত ঋণের পাহাড় তাদের ব্যবসাকে কঠিন করে তুলেছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংককে তার অবস্থান আরো শক্ত করে জানান দেয়া উচিত। কিছু পদক্ষেপ বাংলাদেশ ব্যাংক নিতে পারে যদি তাতে ব্যর্থ ব্যাংকগুলোর আর্থিক অর্জনে কিছুটা উন্নতি হয়। ব্যর্থ ব্যাংকগুলোর আমানত বীমার আওতায় আনা যায় কিনা চিন্তা করা যেতে পারে। ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স প্রদান করতে বলা হোক। এ বাবদ ব্যয় ব্যাংকগুলোকেই বলে ব্যর্থ ব্যাংকের উদ্যোক্তাদেরকে পকেট থেকে অতিরিক্ত পুঁজির জোগান দিতে বলা হোক। না দিলে বোর্ডে বসার অধিকার হারানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে। যারা বড় পাবলিক শেয়ারহোল্ডার তাদের প্রতিনিধিত্ব বোর্ডে বাড়ানো যেতে পারে। ব্যর্থ ব্যাংকগুলোর বোর্ড সদস্যরা অন্য সবার মতো সুযোগ-সুবিধা নেবে সেই বিধি এক্ষেত্রে রহিত হোক। অর্জনের সঙ্গে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার বিধানকে বেঁধে দেয়া উচিত। যাদের কারণে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থায় দুর্যোগ নেমে এসেছে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হোক। ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত সুবিধা শিকারিদের বোর্ড সদস্য হতে বিরত রাখা হোক। কোনো ব্যাংকই পারিবারিক নিয়ন্ত্রণে যাতে না থাকে সেটার নিশ্চয়তাও বাংলাদেশ ব্যাংককে করতে হবে। বাংলাদেশে ব্যাংক খাতে লুট হয়েছে সত্য, তবে সব ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিষয়টা এমন নয়। একটা ভালো বোর্ড এবং একজন ভালো সিইও হলো আমানতকারীদের জন্য বড় আর্শীবাদ। আবারো বলতে চাই, শীর্ষ ১০টি ব্যাংকের পক্ষে ব্যবসা করা যতটা সহজ হবে, ব্যর্থ ব্যাংকগুলোর জন্য ব্যবসা করা ততটাই কঠিন। যে ব্যাংক চলবে না তাকে জোর করে চালাতে নেই। আমাদের সামনে তো পদ্মা ব্যাংকের উদাহরণ আছেই। যথাসময়ে ওইসব ব্যাংক বেচা-বিক্রির মাধ্যমে অবসায়নে যাওয়া উচিত। দেরি করে ফেললে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে। যে ব্যাংকের এনএভি ঋণাত্মক (সম্পদ থেকে দেনা বেশি) সে ব্যাংকের দেনা দিনদিন বাড়বে। কোনো রকমের সুযোগ-সুবিধা দিয়েই ওইসব ব্যাংককে লালন করতে গেলে দায়-দেনা আরো বাড়বে, শেষ পর্যন্ত সেই দায়-দেনা বহন করতে হয় পুরো সমাজকেই।
আবু আহমেদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান