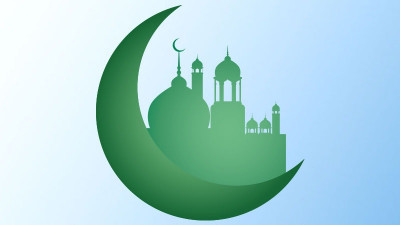ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা ২০১২ সালের ১৪ মার্চ হামবুর্গভিত্তিক সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের (আইটিএলওএস) রায়ে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালের ৮ জুলাই হেগভিত্তিক স্থায়ী আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ে ভারতের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৪০ বছর ধরে চলা বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধের অবসান ঘটেছে। ফলে বাংলাদেশের এখতিয়ারভুক্ত সমুদ্র অঞ্চলের আয়তন দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারে, যা প্রায় পুরো বাংলাদেশের আয়তনের সমান। এছাড়া ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে বাংলাদেশ।
বঙ্গোপসাগরে অমিত সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে এবং তা কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে বাংলাদেশের মেরিটাইম অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ এবং সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৪ সালে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সমুদ্র বিষয়ে আইন, ‘দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স অ্যান্ড মেরিটাইম অ্যাক্ট ১৯৭৪’ প্রণয়ন করেছিল। এরপর আমাদের সামুদ্রিক প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার যথাক্রমে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে অনুরূপ আইন প্রণয়ন করেছে।
১৯৮২ সালের ৬ ডিসেম্বর জ্যামাইকার মন্টিগো বে-তে সমুদ্র আইনসংক্রান্ত তৃতীয় জাতিসংঘ সম্মেলনের শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ অধিবেশন চলাকালে ১০ ডিসেম্বর সমুদ্র আইন বিষয়ে এক ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩২০ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট এই কনভেনশনে সমগ্র সমুদ্র এলাকা নিয়ন্ত্রণ উপযোগী একটি বিস্তারিত আইন কাঠামো প্রদান করা হয়। সম্মেলনে ১৫০-এর অধিক দেশ অংশগ্রহণ করে, কনভেনশনটি স্বাক্ষরের জন্য ১০ ডিসেম্বর উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রথম দিনেই বাংলাদেশসহ ১১৯টি দেশ এতে স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষরিত চুক্তির বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে ওপরে উল্লিখিত রায় দুটির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে পৃথিবীর অন্যতম জটিল সমুদ্রসীমা বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়।
এরই মধ্যে কিছুটা দেরিতে হলেও ১৯৮২ সালের চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি রাষ্ট্রীয় আইনে সন্নিবেশনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আইন কমিশন বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের রাষ্ট্রীয় সমুদ্র ও সামুদ্রিক অঞ্চল আইনটির (Territorial Waters and Maritime Zones Act 1974) সংশোধনপূর্বক ‘টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোন (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল-২০২১’ (Territorial Waters and Maritime Zones (Amendment) Act, 2021) নামে ২০২১ সালের ৭ ডিসেম্বর মাননীয় রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করেছে। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ায় অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও রাষ্ট্রীয় জলসীমা, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানে সমুদ্র সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মেরিন অ্যাফেয়ার্স ইউনিট আছে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ব্লু ইকোনমি সেল করা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিউটের কার্যক্রম চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র, সামুদ্রিক সম্পদ ও সামুদ্রিক মৎস্যবিষয়ক বিভাগ খুলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা হচ্ছে। মৎস্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটা মেরিন ফিশারিজ উইংও আছে। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে সংশ্লিষ্ট এসব দপ্তর বা বিভাগ এমনকি কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান সভা, সেমিনার, সিম্পজিয়াম ও ওয়ার্কশপ করেই যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এতে দেশের পর্যটন, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, বাণিজ্য এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কিছুই এখনো অর্জন হয়নি। এমনকি সঠিক কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি কোনো কর্মপরিকল্পনাও নেয়া সম্ভব হয়নি এ পর্যন্ত। অথচ অর্থনীতিবিদরা বলছেন, সমুদ্রতলের গ্যাস, মৎস্যসহ অন্যান্য সম্পদ আহরণ, বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও পর্যটনের ক্ষেত্রে যথোচিত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ২০৩০ সাল নাগাদ সমুদ্র থেকে প্রতি বছর প্রায় আড়াই লাখ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব।
অথচ ২০১২ সালে সমুদ্র বিরোধ সমাধানের পরপরই মিয়ানমার দ্রুততম সময়ে তাদের সামুদ্রিক অংশে মাত্র দুই বছরে নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পাশাপাশি বাংলাদেশের সীমানা লাগোয়া তাদের ব্লক থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে দেয়। আর সেই গ্যাস দিয়ে এখন দেশটি নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে গ্যাস করছে চীনে। ভারত এ যাবৎ ৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আবিষ্কার করেছে বঙ্গোপসাগরে। নিয়মিত গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে দেশটি। সমুদ্রসীমা নির্ধারণ হওয়ার পর আমাদের অংশে ২৬টি গ্যাস ব্লক নির্ধারণ করা হয় যার ১১টিকে অগভীর ও ১৫টিকে গভীর সমুদ্রে হিসেবে স্থির করা হয়। ২০১৯ সালে মাত্র চারটি ব্লকে অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। তা-ও আবার কাজ চলছে ধীরগতিতে। একটি কূপও তখনো খনন করা হয়নি। বাকি ২২টি ব্লক খালি পড়ে থাকে। ২০২২ সালে এসে শুধু বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে জরিপ করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এখানে ন্যূনতম ১৭ থেকে ১০৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট (টিসিএফ) গ্যাস হাইড্রেটস মজুদ রয়েছে।
সারা পৃথিবীতে সব উপকূলীয়, সামুদ্রিক কিংবা দ্বীপ দেশগুলো সমুদ্র শক্তি ও সম্পদের অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশ মনে হচ্ছে সমুদ্র বিজয় নিয়ে যতটা উল্লসিত হয়েছিল, সে সম্পদ কাজে লাগাতে ততটা উৎসাহিত নয়। শুধু তেল-গ্যাস তথা জ্বালানি নয়, অন্যান্য মূল্যবান সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্র ঘিরে। অস্ট্রেলিয়া এ খাত থেকে বছরে তাদের ঘরে ফসল তুলছে প্রায় ৪৭ দশমিক ২ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ২০২৫ সালের মধ্যে সমুদ্র অর্থনীতির আয়কে ১০০ বিলিয়ন ডলারে নিতে চায় দেশটি। সিঙ্গাপুরের জিডিপির ৪০ ভাগ সমুদ্রনির্ভর। চীনের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ আসছে সমুদ্র অর্থনীতি থেকে।
পৃথিবীতে এমন সামুদ্রিক, উপকূলীয় কিংবা দ্বীপরাষ্ট্র বিরল যাদের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিপরিষদে সমুদ্রসংক্রান্ত মন্ত্রণালয় কিংবা কাউন্সিল নেই। চীনে মিনিস্ট্রি অব নেচারাল সায়েন্স যার অধীনে ওশান অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল, ভারতে মিনিস্ট্রি অব আর্থ সায়েন্স, পাকিস্তানে মিনিস্ট্রি অব মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স, দক্ষিণ কোরিয়ায় মিনিস্ট্রি অব ওশানস অ্যান্ড ফিশারিজ, ইন্দোনেশিয়ায় মিনিস্ট্রি অব মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স, মালদ্বীপে মিনিস্ট্রি অব ফিশারিজ অ্যান্ড ওশান রিসোর্সেস ইত্যাদিসহ যেকোনো দেশের সমুদ্রবিষয়ক মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর সেসব দেশের সমুদ্র ও সামুদ্রিক উন্নয়নের সব আয়োজন সমন্বয় করে, নেতৃত্ব দেয়। ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিমির ভূমিভিত্তিক বাংলাদেশের জন্য অর্ধশতাধিক মন্ত্রণালয় থাকলেও দুর্ভাগ্য আমাদের সমুদ্রের, উত্তর বঙ্গোপসাগরের তথা উপকূলীয় বাংলাদেশের! সমুদ্রের সুযোগ নিতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় তৎপর হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে, সমুদ্রের বিপদে এগিয়ে আসতে এমনকি সমুদ্র নিয়ে যারা কাজ করে তাদের পাশে দাঁড়াতে নেই কোনো মন্ত্রণালয়, এমনকি কেন্দ্রীয় কোনো কাউন্সিল কিংবা অধিদপ্তর। সমুদ্রকে অভিভাবকহীন রেখে সুনীল অর্থনীতির উন্নত বাংলাদেশ গড়া অসম্ভব বলে মনে করছি। ২০১১ সাল থেকে বাংলাদেশে একটি সমুদ্রও স্বাক্ষর সমাজ প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্লু এ গ্রীন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও সাক্ষাৎকারে এ দাবি করে আসছি।
সমুদ্রের পরিবেশ, খনিজ ও প্রাণিজ সম্পদ রক্ষা ও আহরণের জন্য যেসব মন্ত্রণালয় ও এজেন্সি জড়িত, তাদের কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত ও পর্যালোচনা করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিশন বা অনুরূপ একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন এম শাহ আলম, সদস্য, আইন কমিশন তার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি বিষয় এক লেখায়।
বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের তথ্যমতে, দেশে সমুদ্রবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন সম্পর্কিত এক বক্তব্যে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘আমাদের বর্তমান সিস্টেমগুলো সমুদ্রের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবেলা অপর্যাপ্ত, যেমন অতিরিক্ত মাছ ধরা, উপকূলীয় সুরক্ষা এবং প্রবাল প্রাচীরের বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়া। একই সময়ে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ছে, যেমন অফশোর তেল ও গ্যাস, শিপিং ফ্লিট সম্প্রসারণ, ক্রমবর্ধমান পর্যটন এবং সমুদ্রের তলদেশে খনি আবিষ্কার ইত্যাদি। তাই জাতীয় এজেন্ডায় সমুদ্রসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর প্রোফাইল উত্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি এবং এজন্য একটি নতুন সমুদ্রবিষয়ক মন্ত্রণালয় তৈরি করা এ বিশাল এবং অপরিহার্য সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শাসন কাঠামো তৈরি করতে হবে।’ সমুদ্রসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সর্বপ্রথম কাজ হবে সমন্বয় করা। মৎস্য সুরক্ষা ইউনিট, উপকূল রক্ষার উদ্যোগ, পর্যটন কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং গবেষণা সংস্থাগুলোর মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভাগ এবং সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে একটি ব্যাপক কৌশল বাস্তবায়নের জন্য অর্থ, শিক্ষা, গবেষণা, আইনসহ সবার সঙ্গে সমন্বয় করবে এ মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় বেসরকারি খাতের সঙ্গে সমুদ্রবিষয়ক চুক্তির নিযুক্তি, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োগ ও কার্যক্রম পরিচালনার মূল কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে।
ড. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন: অধ্যাপক, ওশানোগ্রাফি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়