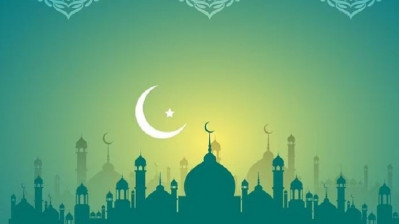ছবি : বণিক বার্তা
ছবি : বণিক বার্তা সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মানুষ পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, সমুদ্র মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে স্পর্শ করে। বায়ুমণ্ডল থেকে জীবনধারণের জন্য শ্বাস নেয়া, নির্দিষ্ট জলবায়ুতে বসবাস করা, খাদ্য গ্রহণ ও পণ্য ব্যবহার থেকে শুরু করে সবকিছুতেই কোনো না কোনোভাবে সমুদ্রের অবদান রয়েছে। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশজুড়ে রয়েছে এ বিশাল সাগর-মহাসাগর। পৃথিবীর প্রায় সব মিঠা পানির উৎসও সাগর-মহাসাগর। সমুদ্র পৃথিবীতে কার্বন, শক্তি এবং পানির সংরক্ষণ, পরিবহন ও সরবরাহের মাধ্যমেও পৃথিবীর জলবায়ুকে উল্লেখযোগ্য হারে প্রভাবিত করে। খাদ্য, জীবিকা ও ওষুধের সবচেয়ে বড় উৎস সমুদ্র। অন্যদিকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বেশির ভাগ কার্যাবলি সমুদ্রকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্র থেকে সংগৃহীত মাছ ও জ্বালানি কিংবা মানুষের দ্বারা উৎপাদিত বর্জ্য, যেমন পয়োনিষ্কাশন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ব্যবহৃত প্লাস্টিক সমুদ্রে মিশে সামুদ্রিক পরিবেশকে দূষিত করছে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং সুনামির মতো প্রকাণ্ড সামুদ্রিক বিপর্যয় মানুষের জীবন, জীবিকা ও পরিবেশ লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে, যা মানুষকে প্রতিনিয়ত ভাবিয়ে তুলছে।
তাই সমুদ্র, সমুদ্রের জটিল প্রক্রিয়া, সামুদ্রিক সম্পদ ও শক্তি, সমুদ্রের সঙ্গে বায়ুমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গভীর জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সঠিকভাবে বোঝা ছাড়া এ গ্রহে মানুষের অবস্থান ও অবস্থাকে পুরোপুরি বোঝার এবং উপলব্ধির দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।
সমুদ্র ও মানুষের উপর্যুক্ত সম্পর্কের অল্প কিছু দিক সহস্রাব্দ ধরে উপকূলীয় জনগণের চেতনাবোধ তৈরি করেছে। যেমন মাছ ধরা এবং সংগ্রহ করার বিষয়টি তাদের কাছে লাভজনক আহরণের সুযোগ হিসেবে; অন্যদিকে হ্যারিকেন এবং সুনামি হুমকি হিসেবে উপলব্ধ। এমনকি তুলনামূলক কম বাস্তব আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের কিছু বিষয়ও সমুদ্রের সঙ্গে উপকূলীয় জনগণের সম্পর্কের বিশ্বাস তৈরি করেছে। তবে ভূ-বিজ্ঞান কিংবা প্রকৃতি বিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রধান শাখা হিসেবে সমুদ্রবিজ্ঞানের আবির্ভাব অতি সাম্প্রতিক, যা প্রায় ১৯ শতকে শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিকে মানুষের নজর কেড়েছে। বহু বছর ধরে আনুষ্ঠানিক সামুদ্রিক বিজ্ঞান কিছু বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যারা ইউরোপীয় বা উত্তর আমেরিকার বংশোদ্ভূত, তাদের সংরক্ষণে রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে আরো দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সমুদ্রবিজ্ঞান ইউরোপীয় বা উত্তর আমেরিকার বংশোদ্ভূত বিশেষ কিছু ব্যক্তির কাছে সীমাবদ্ধ ছিল, যা ২০ শতকের মাঝামাঝি থেকে আরো দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে।
এ সাম্প্রতিক যাত্রা এবং ক্ষেত্রের কিছুটা সীমাবদ্ধ প্রকৃতি নিঃসন্দেহে সমুদ্র সম্পর্কে জনসাধারণের দ্বারা প্রাসঙ্গিক ধারণা গ্রহণকে ধীর করে দিয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত ও যত্রতত্র ব্যবহারের কারণে অনেক সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ, উৎপাদন ও ধারণক্ষমতার দ্রুত অবনতি ঘটেছে বলে সমুদ্রও শিক্ষাবিদরা মনে করছেন।
এ ধরনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র সাক্ষরতার প্রত্যাশিত সর্বজনীনতা ও বর্তমান দুর্বল অবস্থার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করেছে। ফলে ১৯৭৬ সালে গঠিত মার্কিন সামুদ্রিক বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের জোট ‘জাতীয় সমুদ্র শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন (এনএমইএ)’ ২০০০ সালের দিকে একমত হয়েছিল। ঠিক তখন থেকে, বিশেষ করে ২০০২ থেকে ২০০৪ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের এ জোট ব্যাপক মিটিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সের মতামতের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাসাগর বা সমুদ্র সাক্ষরতার একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত সংজ্ঞা তৈরি করে, যা হচ্ছে ‘সমুদ্রের ওপর মানুষের প্রভাব এবং মানুষের ওপর সমুদ্রের প্রভাব বুঝতে পারা’। সংজ্ঞা অনুসারে, ‘একজন সমুদ্র-শিক্ষিত (সমুদ্র সাক্ষর বা ওশান লিটারেট) ব্যক্তি সমুদ্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে মৌলিক ধারণাগুলো বুঝবেন, একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে মহাসাগর সম্পর্কে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং মহাসমুদ্র এবং তার সংস্থান সম্পর্কে অবহিত এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন’।
তখন থেকে, সমুদ্র সাক্ষরতার ধারণাটি সমুদ্রবিজ্ঞান এবং এ-সংক্রান্ত শিক্ষা এবং নীতি প্রণয়নের আলোচনায় ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে এ আলোচনা অত্যন্ত বিস্তৃত আঙ্গিকে স্থান পেয়েছে। এমনকি ধারণাটি সমসাময়িক সময়ে ঘোষিত জাতিসংঘের বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০-এর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ (এসডিজি ১৪)-তে ‘পানির নিচে জীবন’ উল্লেখ করে সুনির্দিষ্টভাবে সাগর, মহাসাগর ও সমুদ্রসম্পদের টেকসই ব্যবহার ও সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪-এর লক্ষ্য সামুদ্রিক জলরাশির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার বাস্তুসংস্থানের দূষণ রোধ করা, যার মূল ভিত্তিই হলো সমুদ্র শিক্ষার মাধ্যমে জনসচেতনতা ও সমুদ্র বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এছাড়া সমুদ্রকে কাজে লাগিয়ে সামুদ্রিক টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের জন্য সমুদ্রবিজ্ঞানের দশক ২০২১-৩০ ঘোষণা করা হয়েছে। এরই মধ্যে যার বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের প্রায় সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষ করে সামুদ্রিক অঞ্চল ও দেশগুলোয় এ সম্পর্কিত নানা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উৎসব চলছে, যে আয়োজনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিই হচ্ছে সমুদ্রশিক্ষা ও গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমুদ্র বিশেষজ্ঞ এবং সব বয়স ও মানুষের মাঝে সমুদ্র সচেতনতা তৈরি করা। বিশেষত সমুদ্রবিজ্ঞান দশকের জন্য বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে যে সাতটি মূল প্রত্যাশিত সামাজিক উন্নয়ন ফলাফল সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তার অন্যতম হলো—
‘ফলাফল ৭: একটি অনুপ্রেরণামূলক এবং আকর্ষণীয় সমুদ্র, যেখানে সমাজ, মানবকল্যাণ এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমুদ্রকে বোঝাবে এবং মূল্যায়ন করবে। আচরণের পরিবর্তনকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং দশকের অধীনে বিকশিত সমাধানগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য সমুদ্রের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের একটি ইতিবাচক পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এ পরিবর্তন সমুদ্র সাক্ষরতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষামূলক এবং সচেতনতা বৃদ্ধির পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং সমুদ্রে ভৌত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব হবে।
সে কারণে অধিকতর টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সমুদ্রের পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সমাজ রূপান্তর করার প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সমুদ্র সাক্ষরতাকে বিবেচনা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বেশির ভাগ উন্নত ও উন্নয়শীল সামুদ্রিক দেশের শিক্ষা কারিকুলামের প্রতিটি স্তরের উপযোগী করে সমুদ্র ও সামুদ্রিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথবা অনানুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিটি শিক্ষা কিংবা এক্সট্রা-কারিকুলার শিক্ষা হিসেবেও সমুদ্রশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশে দেশে গত কয়েক দশকে একাধিক জাতীয় কমিশনের তত্ত্বাবধানে সমুদ্র বিষয়ক ধারণা ও বিষয়গুলোকে ধারাবাহিক বিন্যাসে প্রয়োজনীয় বাজেটের আওতায় এনে জাতীয় পর্যায়ে সামুদ্রিক শিক্ষা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে সমুদ্র ও পরিবেশ সচেতন আধুনিক ও স্মার্ট নাগরিক গড়ে উঠছে। জাপান, চায়না ও তাইওয়ানসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে সমুদ্রকেন্দ্রিক টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট সমুদ্র কারিকুলাম ও পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপে অনেক আগেই সমুদ্রবিজ্ঞান সিকোয়েন্স ফর গ্রেডস ১-১২ কার্যকর রয়েছে। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় সমুদ্রবিজ্ঞানকে স্কুলের কারিকুলামে যুক্ত করা হয়েছে।
কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদের সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কারিকুলামে সমুদ্র সম্পর্কিত বিষয় এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে জীবন, জীবিকা ও পরিবেশের জন্য সমুদ্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। এছাড়া সমুদ্র কীভাবে মানুষের স্বাস্থ্য ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা অনুধাবনেও ব্যর্থ হচ্ছে তারা। ফলে দেশের শতকরা ৭৫ শতাংশ অজ্ঞরজ্ঞানসম্পন্ন জনগোষ্ঠীসহ গোটা সমাজ সমুদ্রের বিষয়ে নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে। তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টেকসই উন্নয়নসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।
প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে যথাক্রমে ২০১২ ও ২০১৪ সালে সমুদ্র সীমা নিষ্পত্তি হয়। এর পরপরই বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে সমুদ্র গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষায় সমুদ্র ও সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবনে দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওশানোগ্রাফি বিভাগ ও বিশেষায়িত মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। এছাড়া সমুদ্র ও সম্পদের গবেষণা করতে জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় অনেক আগেই। বাজেট, দক্ষ জনশক্তি ও অবকাঠামো সীমাবদ্ধতায় এসব প্রতিষ্ঠানের বিস্তার, কার্যক্রম ও গবেষণায় রয়েছে প্রত্যাশার চেয়ে ধীরগতি। দেশের সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন।
বাংলাদেশে সুনীল অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগাতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনে ব্লু ইকোনমি সেল গঠন করা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘সমুদ্র বিষয় ইউনিট’-এর তত্ত্বাবধানে আন্তঃসরকারীয় পর্যায়ে সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও রক্ষা এবং তার যথাযথ ব্যবহারে কাজ করছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য বাস্তবতার কারণে ১৯৭১ সালে প্রস্তাবিত বাংলাদেশে প্রথম মেরিন বায়োলজি ও ওশানোগ্রাফি বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। পরে ১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেরিন বায়োলজি বিভাগ হিসেবে চালু হয়। পরবর্তী সময়ে এটি ১৯৮৩ সালে অবকাঠামো ও সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনায় ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সে উন্নীত হয়। গত ৫০ বছরে সহস্রাধিক স্নাতক ডিগ্রিধারী তৈরি করেছে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ তৈরি হয়নি এখনো।
এদিকে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সের অধীনে ওশানোগ্রাফিতে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়। পরে ২০১৯ সালে মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদের অধীনে ওশানোগ্রাফি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওশানোগ্রাফির স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বের হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে তাদের অধিকাংশই সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনাবিষ্কৃত সমুদ্রসম্পদ ও শক্তিকে কাজে লাগাতে ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত সমুদ্রবিশেষজ্ঞ তৈরির পাশাপাশি সমুদ্র সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হবে।
দক্ষতার সঙ্গে দেশের সামুদ্রিক সম্পদের আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে সমুদ্র বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, গবেষক ও অভিজ্ঞ প্রশাসককে অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত একটি সমুদ্র শিক্ষা কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এ কমিশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমুদ্র কারিকুলাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কারিকুলামের উপযুক্ততা যাচাই করে একটি যুগোপযোগী সমুদ্র কারিকুলাম তৈরি করবে। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিকভাবেও সব বয়স ও পেশার মানুষকে সমুদ্র সচেতন করে গড়ে তোলার বিষয়েও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বঙ্গোপসাগরের সম্পদ ও শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সমুদ্র তথা বঙ্গোপসাগর সচেতন নাগরিক সমাজ তৈরি করতে হবে। তাই দেশের সব বয়স ও পেশার মানুষের কাছে সহজবোধ্য সমুদ্র ও সামুদ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তথ্য-উপাত্ত পৌঁছে দিতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গৃহীত সমুদ্র সাক্ষরতার সাতটি মূলনীতি ও ৪৫টি মৌলিক ধারণাকে কাজে লাগিয়ে দেশে সমুদ্র শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।
ড. মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন: অধ্যাপক, ওশানোগ্রাফি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ব্লু গ্রিন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ