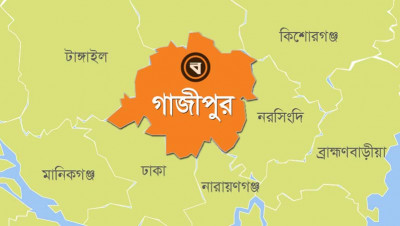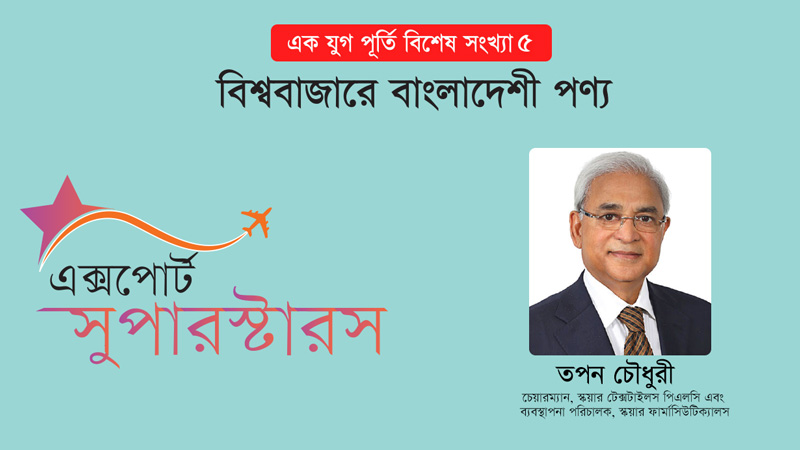
বাংলাদেশের ওষুধ রফতানি ক্রমেই বাড়ছে। এ দেশের ওষুধের ওপর বৈশ্বিক আস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।
রফতানি বাড়ছে মানেই বিদেশের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি ওষুধের ওপর আস্থাও বাড়ছে। এ আস্থাকে সামনে রেখে সঠিক মানে, সঠিক সময়ে, সঠিক প্যাকেজিংয়ে ও সঠিক মূল্যে রফতানি চালিয়ে যেতে পারলেই সে ভলিউমে অনেক পরিবর্তন আসবে। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বাজারে ওষুধ সরবরাহকে আমরা রফতানির ওপরে গুরুত্ব দিই।
প্রায় তিন দশক ধরে বিশ্ববাজারে স্কয়ার ওষুধ রফতানি করছে। বর্তমানে ৩৫টির বেশি দেশ আপনার প্রতিষ্ঠানের ওষুধের ক্রেতা। এখন পর্যন্ত রফতানিতে স্কয়ারের অভিজ্ঞতা কেমন?
ওষুধ রফতানিতে আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। অনেক ধৈর্য নিয়ে, অনেক বিনিয়োগ করে, অনেক কাজ আমাদের করতে হচ্ছে। রফতানি বাজারকেন্দ্রিক ব্যবসা পরিচালনা নীতি আমাদের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যে যেতে সাহায্য করছে। কেনিয়ায় আমাদের নতুন কারখানা, ফিলিপাইনে মার্কেটিং কোম্পানি গঠন, ব্রাজিলের জিএমপি সার্টিফিকেশন—এসবই আমাদের রফতানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের একেকটি পর্যায়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বাজার যুক্তরাষ্ট্রে আরো বেশি ওষুধের অনুমোদন লাভ ও রফতানি মূল্য বৃদ্ধির পরিকল্পনায় আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
ওষুধের কাঁচামাল আমদানির কোনো উল্লেখযোগ্য সমস্যা রয়েছে, যা রফতানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে?
বাংলাদেশ সরকার ওষুধ রফতানি প্রবৃদ্ধিতে অনেক যত্নশীল। এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি ও সার্বক্ষণিক উৎসাহের জন্য কৃতজ্ঞ। তবে রফতানির উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত কিছু কাঁচামালের ওপর থেকে শুল্কহার ‘শূন্য’ করা গেলে রফতানি আয় বাড়ত। সেই সঙ্গে বর্তমান সময়ে ব্যাংক থেকে এলসি (ঋণপত্র) খোলার সময় প্রাধিকার বিবেচনা আমাদের সবার জন্যই খুব সহায়ক হতো।
বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ওষুধের দাম আর স্থানীয় বাজারে দামের তারতম্য সম্পর্কে জানতে চাই। দুই বাজারে ওষুধের মানে ভিন্নতা রয়েছে কি?
বাংলাদেশের বাজারে ওষুধের দাম সরকার নির্ধারণ করে দেয়। আর বাংলাদেশ যেসব দেশে ওষুধ রফতানি করে সেখানে বাজারমূল্য নির্ভর করে সরবরাহের ওপর। সেসব দেশে সাধারণত খুচরা বিক্রেতারাই সরবরাহ ও প্রস্তুতকারক কোম্পানি বিচারে বিক্রয়মূল্য ঠিক করে। তাই বাংলাদেশে কোনো ট্যাবলেট ১০ টাকায় বিক্রি হলেও রফতানি বাজারে তার খুচরা মূল্য হতে পারে ৫০ টাকা। তাছাড়া রফতানির ক্ষেত্রে সবসময়ই বাজারভেদে ও আমদানিকারক দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির বিবেচনায় মূল্যের তারতম্য ঘটে।
এছাড়া রফতানীকৃত আর বাংলাদেশে সরবরাহকৃত ওষুধের পার্থক্য হচ্ছে কেবল মোড়কে। স্কয়ার তার প্রতিটি উৎপাদন ইউনিটে একই মানদণ্ড অনুসরণ করে। উৎপাদনের পর ওষুধগুলো দেশ বা আমদানিকারকভিত্তিক রিলিজ স্পেসিফিকেশন অনুসারে পরীক্ষা করে প্যাকেটজাত করা হয়।
উন্নত বিশ্বের ওষুধ শিল্পের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের অবস্থান ও মান সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?
বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রতিটি কোম্পানির উৎপাদন ও মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এখন উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর সমতুল্য। পার্থক্য হচ্ছে একটাই, আমরা বাংলাদেশের সীমারেখায় তৈরি করছি আর ইউরোপ-আমেরিকার কোম্পানিগুলো তাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক অবস্থানে থেকে একই কাজ করে যাচ্ছে।
১৫২টি দেশে ওষুধ রফতানি করছে বাংলাদেশ। তবে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বাজারে এখনো শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়নি। এফডিএ, এমএইচআরএর মতো সংস্থার অ্যাক্রেডিটেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে দেশীয় ওষুধ শিল্পের সীমাবদ্ধতাগুলো কী?
যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোয় ওষুধ রফতানিতে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এ অপেক্ষার সময়টা ১০ বছরের কাছাকাছি। আমার জানামতে বাংলাদেশের শীর্ষ দশের অনেক কোম্পানিই সেই সময়টা পার করছে বা করে ফেলেছে। বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোর প্রতিনিয়ত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ওষুধ অনুমোদনের খবর তারই ইঙ্গিত দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) বা যুক্তরাজ্যের মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রডাক্ট রেগুলেটরি এজেন্সির (এমএইচআরএ) কাছ থেকে জিএমপি সার্টিফিকেশন প্রাপ্তিতে যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে বা সামনে আসবে, তা কোম্পানিগুলোর নিজের কারিগরি ও মানদণ্ড নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতাতেই দূর করতে হবে।
ওষুধ শিল্পে স্কয়ারের অবদান প্রায় ৬৫ বছরের। অ্যালোপেথিক, হারবাল ও পুষ্টি, পশু ও কৃষির কয়েক হাজার ওষুধ প্রস্তুত করছে; মেডিকেল ডিভাইসও রয়েছে। স্কয়ারের কোন কোন ওষুধ বিশ্ববাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে?
স্কয়ারের অনেকগুলো ব্র্যান্ডই বিশ্ববাজারের বিভিন্ন দেশে শীর্ষস্থানে রয়েছে। আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ‘জিম্যাক্স’ সাসপেনশন মালয়েশিয়া, জ্যামাইকা, উগান্ডা ও তানজানিয়ায় মার্কেট লিডার। ফিলিপাইনে রাইনাইটিসের ওষুধ ‘ফ্লোনা স্প্রে’ ও স্নায়ুরোগের ওষুধ ‘ভেলোয়েট সিরাপ’ নিজ নিজ ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত ব্র্যান্ড। ‘ক্লোফেনাক’ ইনজেকশন মিয়ানমারের ক্লিনিক ও হাসপাতালে এক অতিপরিচিত ব্যথানাশক। শ্রীলংকার বাজারে আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে জীবন রক্ষাকারী ‘স্পেকব্যাক’ ইনজেকশন, শিশুদের জন্য তৈরি ‘সেডনো সিরাপ’ ও ‘এইস সাপোজিটরি’। নেপালে আমাদের চোখের ড্রপ লুবটিয়ার ‘অ্যালাকট’ ও ‘নেক্রোমিন’ সর্বোচ্চ মার্কেট শেয়ার অর্জন করেছে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ওষুধ ‘লেরজল’ মার্কেট কম্পিটিশনে সবার আগে। কেনিয়ায় স্নায়ুরোগের ওষুধ ‘ডিপ্রেক্স’, ‘মেলক্যাম’, ‘পাইলোট্রিপ’ ও ‘টরি’ এক দশক বাজার ধরে রেখেছে। এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের দেশ ফিজিতেও ডায়াবেটিসের ওষুধ ‘সিগ্লিম্যাট’ ডাক্তারদের আস্থার শীর্ষে। আশা করছি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারেও আমরা উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধগুলো নিয়ে একটি ভালো অবস্থানে যেতে পারব।
বিশ্ববাজারে ন্যায্যমূল্যে ওষুধ রফতানিতে ওই দেশগুলোর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেমন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হচ্ছে বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোকে?
রফতানি বাজারে সেখানকার স্থানীয় কোম্পানিগুলোর আধিপত্য থাকবেই। বাজারমূল্যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সত্যিই মুশকিল। তার ওপর সরকারি ক্রয়ে তারা সবসময়ই একটা প্রাধান্য পায়। তাদের মোকাবেলায় আমাদের বাংলাদেশের তৈরি ওষুধের মান ও সেখানকার ডাক্তারদের আস্থার ওপর ভীষণভাবে নির্ভর করতে হয়।
ওষুধ শিল্পে আমাদের গবেষণা নেই বললেই চলে। এ অবস্থা আগামীর রফতানিকে সংকুচিত করবে কিনা। আর নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদৌ কোনো সম্ভাবনা দেখতে পান?
বাংলাদেশের একটি দায়িত্বশীল জেনেরিক ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে আমাদের নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের মৌলিক গবেষণা এখনই শুরু করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন ওষুধ উদ্ভাবন এবং সেটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের খরচ জোগানো বাস্তবে আমাদের প্রস্তুতকৃত অন্যান্য ওষুধের দামকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে। অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক মূল্যে দেশের বাজারে ওষুধ বিক্রিকে আমরা কখনই সমর্থন করি না। তবে ওষুধ শিল্পে আমাদের গবেষণা নেই—এ কথা ঠিক নয়। কালিয়াকৈর ও পাবনায় স্কয়ারের দুটি বড় রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শতাধিক বিজ্ঞানী সেখানে কাজ করছেন। উন্নত দেশে প্রাপ্য অন-পেটেন্ট, উচ্চমূল্যের জীবন রক্ষাকারী ওষুধকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসে সহজলভ্য করতে দেশের ওষুধ বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও অবদানকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। মূল্যসাশ্রয়ী, অফ পেটেন্ট জেনেরিক ফর্মুলেশনের গবেষণাই আমাদের ওষুধ রফতানি খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসবে।
এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন-পরবর্তী পরিস্থিতি ও মেধাস্বত্বের সুবিধা বাতিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে ওষুধ শিল্পের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাই। এমন কোনো পদক্ষেপ রয়েছে, যা এখনই নেয়া প্রয়োজন?
বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এক আনন্দের ব্যাপার। দেশের সব সাধারণ মানুষের মতো আমরাও সে সময়ের অপেক্ষায় আছি। দেশের মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ শিল্পের বর্তমান বিলম্বিত মেধাস্বত্বের সুবিধাটি আর থাকবে না। মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগের কারণে তখন বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো অন পেটেন্ট ওষুধগুলোর জেনেরিক ভার্সন উৎপাদনের অধিকার হারাবে। এটির মানে হচ্ছে, বাংলাদেশের মানুষ তখন বিশ্ববাজারে অন পেটেন্ট এমন ওষুধ আর বর্তমান মূল্যে কিনতে পারবে না। বর্তমান সময়ের ওষুধ ব্যবহারের ধরনে, সে সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, লিভারের রোগ ও ক্যান্সার রয়েছে। এ পরিস্থিতির সঠিক ও কার্যকর মোকাবেলা একমাত্র বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সব সদস্য এক হয়ে করতে পারেন। মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের ঠিক আগে জাতীয় সংসদ যদি এমন একটি সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয় যে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ মুহূর্তের আগে যত ওষুধ বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি হতো সেসবের জন্য মেধাস্বত্ব আইন কার্যকর হবে না, যেমনটি করেছিল ভারত ২০০৪ সালে তাদের উত্তরণের সময়। আমি বিশ্বাস করি, তাহলেই বাংলাদেশে আসন্ন দুর্ভোগ থেকে সবাইকে রক্ষা করা যাবে।
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা স্যামসন এইচ চৌধুরী প্রতিষ্ঠানকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থান থেকে আপনার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান আরো অনেক এগিয়েছে। এ সাফল্য কীভাবে অর্জন করলেন?
বাবার সঙ্গে আমি দীর্ঘ সময় কাজ করেছি। পড়ালেখা শেষ করে যখন ব্যবসায় আসি, তখন বয়স কম ছিল। অনেক ব্যাপারেই মনে হতো উনি পুরনো দিনের মানুষ—‘ফ্রম দ্য ওল্ড স্কুল অব থটস’, এজন্য ভ্যালুজ নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা বলেন, আইনকানুন নিয়েও বলেন। অথচ আমি দেখতাম, ওই সময় যারা আমাদের প্রতিযোগী, তারা অনেক ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করছে। ব্যবসার প্রফিট, লয়্যালটি এ বিষয়গুলোয় তিনি ছিলেন কঠোর। আমার মনে আছে, যখন প্রথম এ দেশে ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর চালু হয়, তখন আমাদের প্রতিযোগীরা প্রকৃত টার্নওভার ঘোষণা করত না। এজন্য হয়তো অনেক পয়সা তাদের সেভ হতো। আমি একদিন সাহস করে তার কাছে বিষয়টি বলাতে তিনি আমাকে বললেন, ভ্যাট কী জিনিস বোঝো? আমি বিব্রত ও অপমান বোধ থেকেই বললাম, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, ভ্যাট কে দেয়? বললাম কনজিউমার (ভোক্তা) দেয়। এরপর তিনি জানতে চাইলেন তোমার ভূমিকা কী? বললাম, কালেক্ট করে সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া। তখন তিনি বললেন, তাহলে এ টাকার দিকে তোমার নজর কেন? এ টাকা কি তোমার?
এরপর তিনি কড়া কথা শোনালেন। বললেন, তোমার প্রফিট্যাবিলিটি তোমার কস্টিংয়ের মধ্যে যদি বিল্ডআপ না থাকে, যখন দেখছো মুনাফা হচ্ছে না, তখন সে ব্যবসা থেকে বেরিয়ে পড়ো। তুমি সে পণ্য উৎপাদন কোরো না, যদি দেখো ওই ইন্ডাস্ট্রিতে লাভ নেই। যে টাকা সরকারের, আর দিচ্ছে ভোক্তা, সে টাকার দিকে তোমার নজর কেন? তখন আমি বিপণন পরিচালক, ভেবেছিলাম পুরনো ধ্যান-ধারণার মানুষ এমনই। পরে তিনি ডাকলেন, কথা বললেন পিতা হিসেবে পুত্রকে। বললেন, দেখো তুমি যাদের কথা বলছো, আমি হয়তো বেঁচে না-ও থাকতে পারি, কিন্তু তুমি দেখবে এরা কেউ ব্যবসায় থাকবে না। বাবা যে সঠিক ছিলেন, তিনি জীবিত থাকতেই তা দেখলাম। সাত-আট বছরের মধ্যে কোম্পানিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।
স্যামসন এইচ চৌধুরীর নাম এলেই বিজনেস ভ্যালুজের কথা এসে যায়। বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?
‘সৎভাবে কাজ করলে সফল হবেই’—এটা তিনি সবসময় বলতেন। আরো বলতেন, তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে, সৎভাবে পরিশ্রম করে যেতে হবে। বাবার ওই বিষয়গুলো ভেইনের মধ্যে রয়ে গেছে। সবসময় চিন্তা করতেন কোন উপায়ে ব্যবসায় নিরাপদ থাকা যাবে। দিনে অনেকবার দেখতেন ইল্ড কী হচ্ছে, ওওএস (আউট অব স্পেসিফিকেশন) কোন জায়গাগুলোয় হচ্ছে, কিন্তু মান কম্প্রোমাইজ ছাড়া। যে পণ্যটি তুমি কিনছো, সেটা সর্বোচ্চ কম্পিটিটিভ প্রাইসে কিনছো কিনা, ওল্ড মার্কেটে কী ধরনের প্রাইস আছে, এ বিষয়গুলোয় সচেতন থাকতে বলতেন। ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য খুবই সেনসিটিভ পণ্য। সস্তায় তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়, তাই সোর্সগুলো আবার অডিট করতে হয়। এ বিষয়গুলো সবসময় মাথার মধ্যে ছিল। ইচ্ছা করলেই নীতি বিসর্জন বা কম্প্রোমাইজ করা যায় না। এ বিষয়গুলো রক্তে রয়ে গেছে, কখনো বদলাতে পারব না।
১৯৫৮ সালে ৫ হাজার করে চার বন্ধু মিলে ২০ হাজার টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন বাবা। আমার দাদা ছিলেন ডাক্তার, পাবনা শহর থেকে ১২ মাইল দূরে আতাইকুলা এলাকায়। বাবা শহরে এসে যে বাড়িটায় থাকতেন তার ভাড়া ছিল ৩০ টাকা। সেটা নিয়ে তার কোনো যন্ত্রণাবোধ ছিল না। তিনি কখনই ঢাকায় আসতে চাননি। তার কথা ছিল—পাবনাতেই আমার শুরু, যা করব এখানেই করব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় আসার একমাত্র যে কারণটি ছিল তা হলো ব্যবসা বহুমুখী করা। ওই সময় ইপিজেড হচ্ছিল, গার্মেন্টস খাতটা শুরু হলো। আমরাও ওই খাতে যাওয়া যৌক্তিক মনে করলাম। বাবা বললেন, আমাদের ভালো হবে স্পিনিংয়ে যাওয়া। তখন আমরা স্পিনিং শুরু করলাম। এরপর বেশকিছু সময় পার হলো। পাবলিক লিস্টিংয়ে (পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি) গেলাম। এভাবেই ধীরে ধীরে সফলতা এসেছে। রাতারাতি অনেক কিছু করতে হবে, এমন ধারণায় আমরা কখনই বিশ্বাস করতাম না।
আমাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন দক্ষ পেশাজীবীরা। পরিবারের সদস্যরা থাকলেও পেশাজীবীরাই মূলত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছেন। এটাই আমাদের সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভালো প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। দেশে প্রচলিত আইনের প্রতি আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। নিজের দেশের প্রতি আস্থা আমাদের আছে। এ দেশের সম্ভাবনা প্রচুর। মাঝে মাঝে নীতিগত বিষয় নিয়ে কিছু প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, যেগুলো সরকারের সহযোগিতা নিয়েই আমরা কাটিয়ে উঠি। প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সঙ্গে আমরা সবসময় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রয়েছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের যে ভিন্ন ভিন্ন খাতের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষের হাতে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য পৌঁছে দিতে পারছি। সর্বোপরি আমরা দেশের জনগণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণ মানুষের আস্থার কারণেই আমরা বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছি।
বিদেশে বাংলাদেশের বিনিয়োগকে নিরাপদ করতে কী ধরনের নীতিমালা প্রয়োজন?
পলিসিটা হতে হবে সিকিউরড। এখন আন্ডারটেকিং নেয়া হচ্ছে। আমাদের ক্ষেত্রে যেমন চার বছরের মধ্যে টাকা ফেরত আসতে হবে। এছাড়া অনেক পেনাল্টির ধারা আছে। তারপর আছে প্রফিটের বিষয়, সে টাকা অনুমোদন ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া আরো কিছু বিষয় আছে, যেমন প্রতি বছর নিয়মিত অডিট করা এবং যেকোনো সময় অডিট করা। অনেক নিয়মনীতি আছে, সেগুলো সরকার যদি কঠোরভাবে অনুসরণ করে, তাহলে বিদেশে বিনিয়োগ নিরাপদ। গার্মেন্টস খাতেও এ সুযোগ দেয়া উচিত। আমরা মনে করি, বিদেশে বিনিয়োগের দ্বার খুলে দিলেই সমস্যা দেখা দেবে, এটা সঠিক নয়। এখন দু-একটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশে গিয়ে টাকা রাখাটা সহজ নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় তো প্রশ্নই ওঠে না। কেউই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না, অনেক কঠিন। সুতরাং টাকা নিয়ে চলে যাবে ওই সময় পার হয়ে গেছে।
২০৩২ সাল সামনে রেখে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বর্তমান প্রস্তুতি কতটা কার্যকর বলে মনে করেন?
এপিআই (অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট) প্রক্রিয়াটি খুবই ধীরগতিতে চলছে। যে প্রকল্পটি চলছে, সেটি শেষ হতে অনেক বেশি সময় লাগছে। বাংলাদেশ থেকে এপিআই রফতানির ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল নয়। ভারত-চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে রফতানি করাটা এত সহজ হবে না। এপিআইয়ের জন্য পেট্রোকেমিক্যালসহ যেসব কাঁচামাল প্রয়োজন, সেগুলোর জন্য ভারত ও চীনের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওদের কাছ থেকে কাঁচামাল এনে এখান থেকে রফতানি করে টিকে থাকা কঠিন। আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে কিছু চাহিদা আছে, সেগুলোর বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বড় পরিসরে কিছু করার সুযোগ এপিআইয়ে নেই। স্কয়ার, বেক্সিমকো, গ্লোব এপিআই নিয়ে কাজ করছে। এখন বায়োটেকনোলজির সম্ভাবনা উন্মোচন হচ্ছে। আমাদেরও এখন অনেক বিজ্ঞানী প্রয়োজন। বাংলাদেশীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে আমরাও কাজ করছি। আর ফার্মা খাতে বর্তমান যুগে মান নিয়ে কথা বলার সুযোগ নেই, এটা বাধ্যবাধকতা। মান বজায় রাখব, এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই, রাখতেই হবে। মানের কথা বলতে গেলে মানুষ হাসবে আর সন্দেহ পোষণ করবে। ফার্মা পণ্যে এটাই বাস্তবতা। হয় ভালো, নয়তো বাতিল—এর বাইরে অন্য কোনো মাপকাঠির বিষয় নেই।
ব্যাংক ঋণ নিয়ে খেলাপি হওয়া এখন চর্চায় পরিণত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সফলভাবে ডেট ফ্রি ব্যবসা পরিচালনা করছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। এর রহস্য কী?
যখনই কোনো নতুন প্রকল্প হয়, দেখা যায় লোকজন বিপুল পরিমাণ দায় সৃষ্টি করে। এ দায় শোধ করতে গিয়ে কোম্পানিকে গলদ্ঘর্ম হতে হয়। এর কোনো মানে হয় না। আমার কস্ট অব ক্যাপিটাল কী? আমার তো শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আমি যদি ২০০ কোটি টাকা ঋণ নিই, তাহলে মাসে মাসে আমাকে ওই টাকার ওপর ইন্টারেস্ট দিতে হবে না? নির্দিষ্ট সময় পর আবার প্রিন্সিপ্যাল অ্যামাউন্টও তো সমন্বয় করতে হবে। প্রথম যখন আমরা ব্যাংক থেকে প্রকল্পের টাকা নিয়েছি, প্রথম দুই বছরে পাই পাই শোধ করেছি। ওই সময় পর্যন্ত একটি পয়সাও নেয়া হয়নি ওই প্রকল্প থেকে। আমরা যখন স্কয়ার হাসপাতাল করি, হাসপাতাল প্রকল্প কিন্তু প্রথম সাত-আট বছর ব্রেকইভেনে আসেনি। প্রথম দিন থেকেই আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টা করেছি। আর এ প্রকল্প থেকে কোনো টাকা আমরা লভ্যাংশ হিসেবে নিইনি। আমাদের স্পন্সরদের কারো এটা দরকার নেই। এক পয়সাও আমরা এ প্রকল্প থেকে নেব না। এখানে আরেকটি চর্চা আমরা ধরে রেখেছি—আমরা (স্পন্সর) এখান থেকে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ডিসকাউন্ট নিই না। আমাদের ফার্মার যারা কর্মী আছেন, তারা হাসপাতালে ডিসকাউন্ট পান। কিন্তু তা হাসপাতাল নয়, পরিশোধ করে ফার্মাসিউটিক্যালস। আমাদের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীর জন্যই এটা প্রয়োজ্য। এ ধরনের নিয়মাচারের জন্যই সাত-আট বছরের মধ্যে প্রকল্পটি ব্রেকইভেনে চলে এসেছে।
পুঁজিবাজার নিয়ে স্কয়ার ফার্মার দর্শন কী?
ক্যাপিটাল মার্কেট আইন অনুযায়ী আজকেই যদি আমি ডিক্লেয়ার করি, আট লাখ শেয়ার আমি মার্কেট থেকে নেব, স্পন্সর হিসেবে আমি তা পারি। আপনারা দেখবেন তাৎক্ষণিকভাবেই মূল্য বেড়ে যাবে। একইভাবে আমি যদি বলি আট লাখ শেয়ার আমি কাল বিক্রি করব, মূল্য নিচে নেমে আসবে। তারপর আবার এক-দেড় মাস পর আমি মার্কেটে ছেড়ে দেব, এগুলো সবই স্বাভাবিক ও বৈধভাবে সম্ভব। বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরনের ব্যাপারগুলো হচ্ছে। কিন্তু আমার বাবা কখনো এ বিষয়গুলো অ্যালাউ করতেন না। বলতেন, আমাদের দেশে যারা ক্যাপিটাল মার্কেটে আসে, তারা অনেকেই ব্যালান্সশিট বোঝেন না, সারা জীবনের পুঁজি ঢেলে লাভ কোত্থেকে আসবে তাও বোঝেন না। এ ধরনের বিষয়গুলোকে তিনি কখনই উৎসাহ দিতেন না। আমরাও এখনো সেগুলো ধরে রেখেছি, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও। তার দেয়া সব শিক্ষা আমরা ধরে রেখেছি, যার প্রতিফলনও পরে আমরা দেখেছি। কিছু জায়গায় আমরা খুবই কনজারভেটিভ। আমরা কখনই মূল্য সুবিধা নিতে হঠাৎ করে বাজারে স্পর্শকাতর কোনো তথ্য ছড়িয়ে দিইনি। কখনো কখনো আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, ভাই এখন কী কিনব? আমি বলেছি, সরি এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না। তবে আমি বলতে পারি স্কয়ারের ভিত্তি অনেক শক্তিশালী। আপনি আজকে যে দামেই কেনেন, রশিদ রাখেন, বিক্রির প্রয়োজন পড়লে ঠিক সে দামেই কিনে নেব সেটাই গ্যারান্টি। আমাদের দেশে ব্যবসায় এ ধরনের চর্চা অনুপস্থিত। তবে এ ধরনের চর্চা হওয়া প্রয়োজন, তাহলে সবার জন্যই ভালো হতো। এসব মিলিয়েই আমাদের সফলতার চাবিকাঠি। এ সাফল্যকে শুধু টাকা দিয়ে বিচার করলে হবে না।
বর্তমানে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের অবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?
আস্থাটা কমে যাচ্ছে—শুধু বিনিয়োগকারী নয়, সাধারণ মানুষেরও। এটা কিন্তু আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না। কারণ একটা ধারণা তৈরি হলে মানুষ প্রভাবিত হয়। মানুষ যখন দেখছে অমুক ব্যাংকের এত হাজার কোটি টাকা নেই, তখন তাদের মধ্যে আস্থার সংকট দেখা দিচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে তাহলে হচ্ছেটা কী? বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য এগুলো ভালো উদাহরণ নয়।
নতুন প্রজন্মকে দেশের উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
আজকে স্কুলের শিশু থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যে কাউকে প্রশ্ন করলে সে বলবে, এ দেশ ছেড়ে আমি বিদেশে চলে যাব। বিস্ময়ের বিষয় হলো এটা তাদের স্বপ্ন। এখন মা-বাবাও তাই চান। কেউ বিদেশে পড়ালেখা করতে গিয়ে আর ফিরে আসে না। যারা ভালো করছে, তাদের মাধ্যমে ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারলে নতুন প্রজন্মকে ধরে রাখতে না পারার কোনো কারণ নেই। নতুন প্রজন্মকে ধরে রাখতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। এভাবে ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। প্রবাসীরা বাংলাদেশকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তারা দেশের জন্য ভাবে। আমাদের আগে তারা দেশের খবরটা পায়। বিজ্ঞানী, ব্যবস্থাপনাসহ সব ধরনের বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশীদের মধ্যে আছে, তাদের শুধু স্বীকৃতি দিতে হবে। দেশে এখন অনেক ভালো প্রকল্প হচ্ছে। মান নিয়ে ভীষণ রকম খুঁতখুঁতে জাপানিরা পর্যন্ত স্কয়ারের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছ। ভারতীয়রা প্রকল্প দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে সে দেশের মানুষের কাছে বলছে, শোনো আমরা তো বাংলাদেশের কাছে হেরে গেলাম। ইন্ডাস্ট্রি এখন ভালো হচ্ছে, নতুন প্রজন্ম এগুলো দেখে দেশেই সুযোগ সম্ভাবনার বিষয়ে আশাবাদী হতে পারছে। তবে দেশের শিক্ষা কেন্দ্র বলতে এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। আর আছে অল্প কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বাকিগুলোয় শুধু টাকা ও ড্রাগস। পড়ালেখাটাও এখন পশ্চিমা দেশগুলোর মতো ব্যবসা হয়ে গেছে। এ ডিগ্রি দিয়ে কী হবে?
দেশের অর্থনীতির জন্য পরবর্তী বড় শিল্প কী হতে পারে?
একদম নতুন করে কোনো শিল্প এখনই দেখছি না। বড় বিনিয়োগ আসে, এমন নতুন খাতের মধ্যে বিদ্যুৎ ও এলএনজি নিয়ে অনেকে দৌড়াচ্ছে। আমরা মনে করছি, অনেক কিছু আমরা ছোঁব না। ঠিক এ মুহূর্তে আমরা কোর বিজনেসে মনোনিবেশ করব। আমাদের একটা নিশ্চিত শক্তি তৈরি হয়েছে। এটাকেই আরো অনেক বেশি অর্গানাইজড করতে চাই, এক্সপ্যানশনে যেতে চাই, একটু অন্যভাবে দেখতে চাই। সেটা ফার্মা হোক, টেক্সটাইল হোক, টয়লেট্রিজ বা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ। দেশে-বিদেশে সব জায়গায়ই এগুলোর বিপুল সম্ভাবনা আছে। প্রথম যখন জুঁই বিক্রি শুরু হয়, তখন খোলাবাজার থেকে বেরিয়ে আট আনা বেশি দিয়ে মানুষ মানসম্পন্ন পণ্যটি বেছে নিল। লোকে ভালো পণ্য চায়, তারা যদি তা না-ই চাইত, তাহলে আমরা এখনকার অবস্থানে থাকতাম না।
স্কয়ার গ্রুপের কোনো ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আছে, যা জানলে অন্যরা শিখতে পারবে?
আমরা কিছু নতুন ফিল্ডে ট্রাই করেছিলাম, যেমন পিএসটিএন নিয়ে ব্র্যাকের সঙ্গে। একটা পর্যায়ে আমরা সরে আসি। সেটা খুবই ভালো সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ ওখানে খুব খারাপ অবস্থায় পড়তে হয়েছে। ওই একটাই ছিল।
দেশের নীতিনির্ধারকদের জন্য কোনো বার্তা দিতে চান?
‘লেটস হ্যাভ সামথিং ইন্টারঅ্যাকটিভ’—সবাই কথাটা সবসময় বলে, ব্যবসায়ীরা সবসময় এটা চান, ওটা চান। ব্যবসায়ীরা আসলেও চান। তবে সরকারের দিকটিও ভাবতে হবে। সরকারের প্রচুর সীমাবদ্ধতা আছে। আমি দুদিকেই ভাবতে চাই। আমরা যদি সবসময় শুধু কমাতে বলি, তাহলে সমস্যা। আর ব্যবসার পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে বলব, সবকিছু নিয়ে যদি আমাদের দৌড়াতে হয়, সেটাও সমস্যা। আমরা কথায় বলি দুর্নীতি হচ্ছে, কিন্তু আমরা কীভাবে নিশ্চিত, ওখানে আমার লোকটি নেই। আসলে নতুন প্রজন্মের জন্যই সবকিছুতে এখন স্বচ্ছতা প্রয়োজন। বহু মানুষ আছে, যারা সৎ কিন্তু তাদের ভুগতে হচ্ছে।