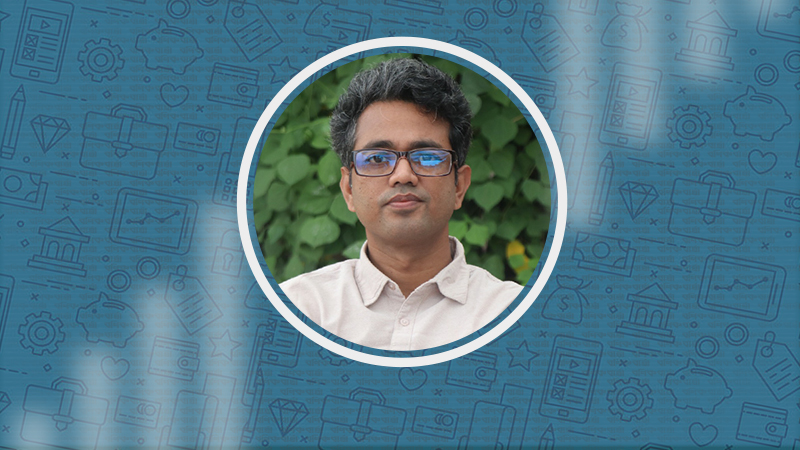
দিন কয়েক পরই বিজয়ের ৫৩তম বার্ষিকী উদযাপন করব আমরা। এরই মধ্যে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নানা আয়োজন। কিন্তু এসবের কোথাও নেই মুক্তিযুদ্ধে নদীর অবদান নিয়ে কোনো আলোচনা বা আয়োজন। অথচ একাত্তরের নয় মাসে অন্য অনেক কিছুর মতো নদীই হয়ে উঠেছিল অন্যতম সহায়ক শক্তি। আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ নদীর দেশ। নদী মানেই বাংলাদেশ। জালের মতো ছড়িয়ে থাকা হাজারো নদ-নদীতে ঘেরা এর ভূখণ্ড। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষ নদীতীরে বসতি গড়েছে। সখ্য করেছে নদীর সঙ্গে। নদী হয়েছে তার আপনজন। তবে এ নদীর সঙ্গে তাদের বৈরিতাও কিন্তু কম নয়। বন্যা, হঠাৎ পাহাড়ি ঢল ও ভাঙন নদী পাড়ের মানুষের নিত্যসঙ্গী।
এই নদ-নদীই ১৮৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় ত্বরান্বিত করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ভাষণের একপর্যায়ে পাকিস্তানিদের হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন, ‘আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব’। বাংলার নদী-নালা, খাল-বিলকে মনে রেখেই তিনি তাদের পানিতে মারার কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, পাকিস্তানিদের জন্য নদ-নদীতে ঘেরা এ ভূখণ্ড অবাধ বিচরণে সহায়ক হবে না। বঙ্গবন্ধু বাংলার নদীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বহু আগেই। তিনি নিজেকে ‘পানির দেশের মানুষ’ বলে পরিচয় দিতেন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় এ নদীকে কেন্দ্র করেই সমর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এর প্রধান কারণ বাংলার এ অঞ্চলটিই নদ-নদীপ্রধান। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার লেখায়। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ঢাকা। যেভাবেই হোক ঢাকা পৌঁছতে হবে, ঢাকাকে দখল করে নিতে হবে। কাজটি যত দ্রুত সম্ভব হবে, পাকিস্তানিদের পরাজয় তত সহজতর হবে। আর তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সবদিক থেকে শত্রুদের বহুমুখী আক্রমণ চালাতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের ভাবনার অগ্রভাগে ছিল নদী। পূর্ব বাংলাকে নদী দিয়ে বিভক্ত করে এলাকা অনুযায়ী চারটি সেক্টরে ভাগ করে অভিযান পরিচালনা করলে লক্ষ্য পূরণ সহজ হবে, এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা। একইভাবে পাকিস্তানি লে. জেনারেল এএকে নিয়াজি ১৯৭১-এর যুদ্ধে বাংলাদেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে সেনা মোতায়েন করেছিলেন। তাতে নদীই ছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অংশ।
মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অসংখ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খোদ নদীতেই। নদীতে সংঘটিত ছোট-বড় এসব যুদ্ধে বীর বাঙালির কাছে পরাস্ত হয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এসব নদী দিয়েই ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল লাখ লাখ বাঙালি। আগরতলায় স্থাপিত ইয়ুথ রিলিফ ক্যাম্পের নামকরণও হয়েছিল নদীর নামে। ভারত সরকারের সহযোগিতায় ও অর্থায়নে স্থাপিত শিবিরগুলোর নাম ছিল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, গঙ্গা প্রমুখ। সে সময় সীমান্তের এক-একটা নদী হয়ে উঠেছিল আশ্রয়প্রার্থী অসহায় মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির অন্যতম প্রিয় স্লোগান ছিল ‘তোমার আমার ঠিকানা—পদ্মা, মেঘনা, যমুনা’। শুধু পদ্মা, মেঘনা, যমুনা নয় বাংলার প্রায় সব নদ-নদীই হয়ে উঠেছিল মুক্তিকামী বাঙালির ঠিকানা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হাজারো গণহত্যা সংঘটিত করে বাংলার নদ-নদীর তীরেই। তারা বাঙালিদের হত্যা করে লাশ ফেলে দিত নদীতে। অসহায়, নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর অব্যাহত নির্মম নির্যাতনে রক্তস্নাত বাংলার হাজারো নদী ফুঁসে ওঠে হানাদারদের বিরুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নদী হয়ে ওঠে সহায়ক শক্তি। নদ-নদীবিধৌত বাংলায় বেড়ে ওঠা দামাল ছেলেদের কাছে সবকিছুই ছিল পরিচিত। হাতে অস্ত্র নিয়ে নদীতে সাঁতার কাটতে কাটতে কখনোবা পানিতে ডুবে ডুবে যুদ্ধ করেছে তারা। পক্ষান্তরে পাকিস্তানিদের কাছে তা একেবারেই অপরিচিত পরিবেশ। এ সুযোগই কাজে লাগান রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধারা। নদীপথের লড়াইকে আরো জোরালো করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় নৌ-কমান্ডো দল। সারা দেশের নদীপথে গেরিলা অপারেশন চালানোর জন্য এ দল তৈরি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালে নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ১০ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল। এই সেক্টরে পদস্থ কর্মকর্তা না থাকায় ছিল না কোনো অধিনায়ক।
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নৌ-কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় ভাগীরথী নদীর তীরে। নদীটি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবাহিত। পলাশীর মাঠের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভাগীরথী। নদীটিকে ভাগীরথী-হুগলি নদীও বলা হয়।
পলাশীর এই নৌ-ক্যাম্পটি নিয়ন্ত্রণ করত ভারতীয় নৌবাহিনী। ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন লে. কমান্ডার জিএম মার্টিস। এই ক্যাম্পের প্রশিক্ষণ অফিসার ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর অফিসার লে. একে দাস ও লে. কপিল। এই ক্যাম্পেই যোগ দেন সে সময় ফ্রান্স থেকে মাতৃভূমির টানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে আসা আটজন বাংলাদেশী সাবমেরিনার। তারা হলেন আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, আবদুর রাকিব মিয়া, সৈয়দ মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, আহসানউল্লাহ, আমিনউল্লাহ শেখ, আবদুর রহমান ও বদিউল আলম।
নৌ-কমান্ডোদের এ প্রশিক্ষণে পরে যারা যোগ দেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের ছাত্র এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনার তরুণ-যুবক। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এ যুবকরা পূর্ব বাংলার খরস্রোতা নদীগুলো থেকে যথাসম্ভব সুবিধা নেয়ার মতো সাঁতারের কৌশল জানতেন। সম্পূর্ণ অন্ধকারে তাদের মাইলের পর মাইল সাঁতরাতে হতো, বাঁশ বা পেঁপে পাতার চোঙা দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে পানিতে মাইন বহন করে শত্রুপক্ষের কাছাকাছি রেখে সেটি বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই সাঁতরে নিরাপদ দূরত্বে ফিরে আসতে হতো। এ ধরনের কঠিন কাজের জন্য যে দৈহিক ও মানসিক শক্তিমত্তার প্রয়োজন, পূর্ব বাংলার তরুণদের তা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই সাঁতারু বা ফ্রগমেন বাহিনীর নেতৃত্ব শুরুর দিকে নৌবাহিনীর সদস্যদের হাতে থাকলেও অচিরেই তা চলে যায় বিপুলভাবে উদ্দীপিত শিক্ষিত যুবকদের হাতে।
নৌ-কমান্ডো বাহিনী চট্টগ্রাম, চালনা-খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও দাউদকান্দি-চাঁদপুর নিয়ে চারটি টাস্কফোর্সে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি টাস্ক ইউনিটে ১০টি করে টাস্ক এলিমেন্ট ছিল। প্রতিটি টাস্ক এলিমেন্টে ছিল তিনজন করে নৌযোদ্ধা। প্রত্যেক নৌযোদ্ধার জন্য বরাদ্দ ছিল দুটো করে লিমপেট মাইন, একটি গ্রেনেড, একটি ছোড়া, একটি কম্পাস ও এক জোড়া ফিন্স (সাঁতারের সময় পায়ে বাঁধা ডানা)। এর বাইরে প্রতিটি টাস্ক এলিমেন্টের জন্য ছিল একটি রাইফেল।
পলাশীর নৌ-ক্যাম্পেরই একটি ৩১ সদস্যের নৌ-কমান্ডো টিম ১৪ আগস্ট রাতে অপারেশন চালায় কর্ণফুলী নদীর চট্টগ্রাম বন্দরে। সেদিন শুধু চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতেই নয়, একযোগে চট্টগ্রাম, মোংলা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে পাকিস্তান বাহিনীর ২৬টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেয়। এতে দুর্বল হয়ে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনীর নৌশক্তি। অপারেশন ‘জ্যাকপট’খ্যাত দুঃসাহসিক সেই অভিযানে হানাদারদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। পরে সেই অপারেশনের কথা ফলাওভাবে প্রচার হয় আন্তর্জতিক সংবাদমাধ্যমে। বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা।
মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল ভারতের আগরতলার পত্রিকা ‘দৈনিক সংবাদ’ তাদের সম্পাদকীয়তে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পরাজয়ের সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণ করেছিল। তার মধ্যে বর্ষায় বৃষ্টির পানি ও নদ-নদী, খাল-বিল যে তাদের জন্য ভয়ংকর হয়ে উঠবে তাও আলোচনায় আসে। পত্রিকাটির বিশ্লেষণ ছিল এমন—‘মুক্তিফৌজের সংগ্রাম নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সুতরাং তার আন্তরিকতা ও তীব্রতা ভাড়াটে সৈন্যের চেয়ে বেশি হতে বাধ্য। তবে বাংলায় যেসব পাঞ্জাবি সৈন্য আবদ্ধ হয়ে আছে কিংবা যেসব পশ্চিমা পাক অধিবাসী রয়েছে তাদের অবস্থা পিঁজরা বাঁধা পশুর মতো। বাংলাদেশের মুক্তিফৌজের বেড়াজাল ভেঙে ওদের আর পালাবার পথ নেই। তাই ওরা হন্যে হয়ে ধ্বংস ও হত্যার কাজে লিপ্ত হয়েছে। আসন্ন বর্ষায় ওদের অবস্থা হবে আরো শোচনীয়। বাংলাদেশের নদী-নালা, খালে-বিলে তখন পাঞ্জাবি সৈন্যের ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে গেলেই তাদের মৃত্যু অনিবার্য।’
হয়েছেও তাই। বর্ষায় বৃষ্টির পানি ও বাংলার নদ-নদী পাকিস্তানিদের পরাজয় মানতে বাধ্য করে। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর তীরের স্থাপিত নৌ-কমান্ডো ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসা যোদ্ধারাই নয়, লাখ লাখ সাধারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনী তাদের নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে নদীতে সংঘটিত যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে বিশেষত বর্ষাকালে নদী ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করেন মুক্তিযোদ্ধারা। এ সময় নদীগুলোও তাদের সহযোদ্ধা হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করে। আগস্টে দেশের নদী বন্দরগুলোয় নৌ-কমান্ডোদের পরিচালিত অপারেশন ‘জ্যাকপট’, সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানিদের রসদবাহী জাহাজে হামলা এবং ডিসেম্বরে অপারেশন ‘হটপ্যান্টস’ তাদের নৌশক্তি বিধ্বস্ত করে দেয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিজয় আসে নদীপথেও। ইতিহাসের বিচারে নদীই হয়ে ওঠে অন্যতম মুক্তিযোদ্ধা। তা আমাদের মনে রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে নদীর অবদান ভুলে যাওয়া চলবে না।
ফয়সাল আহমেদ: নদী গবেষক ও সম্পাদক—রিভার বাংলা







