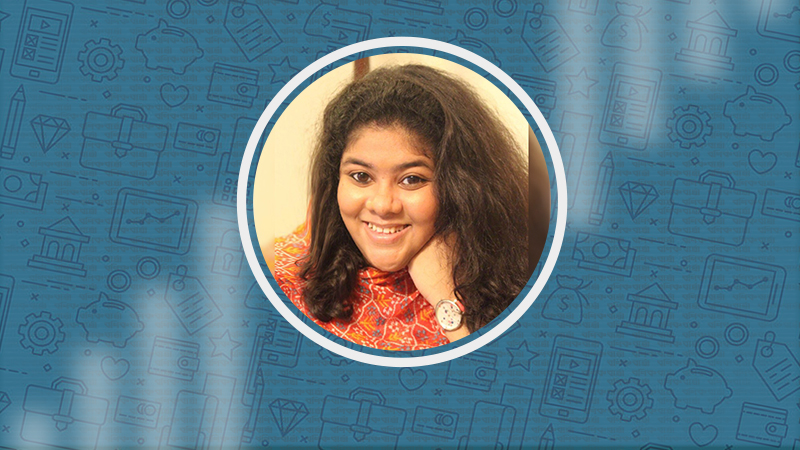একজন মানুষ পরের বেলায় কী খাবে, কী রান্না হবে—এ নিয়ে চিন্তা করাটাই আসলে ছোটখাটো একটা সংসার। পরের দিন টেবিলে ভাতের সঙ্গে কী তরকারি রান্না হবে, বাজার থেকে কী মাছ কেনা হবে, কলমিশাক নাকি পালংশাক। এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে যেমন স্বাধীনতা আছে তেমনি দায়িত্বও আছে। সেই দায়িত্বের একটা অংশ হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ করা, আরেকটা অংশ হচ্ছে সমবণ্টন নিশ্চিত করা। ধরুন, কোনো মায়ের লক্ষ্য হচ্ছে তার সন্তানদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানো। তাই তিনি খাবারের মধ্যে শাকসবজির উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। আবার হয়তোবা এক শিশু মাছ বেশি পছন্দ করে কিন্তু পরিবারের বয়স্করা মুরগির মাংস খেতে চান। যদি দুই পদই করা সম্ভব না হয়, যা বেশির ভাগ পরিবারেরই বাস্তবতা, তাহলে সিদ্ধান্তকারীকে সাধারণত মাকে ভাবতে হয় যে কোন বেলায় কার পছন্দকে প্রাধান্য দেবে। কখন কার প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। একটা দেশ চালানোর ক্ষেত্রেও ঠিক এ রকমই বিভিন্ন প্রয়োজনকে আনুপাতিক প্রাধান্য দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয় অনবরত। এমনকি প্রতি বছর যে বাজেট নির্ধারণ করা হয়, সেটাও দিনশেষে খাওয়ার টেবিলের সিদ্ধান্তের মতোই চিন্তাভাবনায় জড়িত, খালি আরেকটু বেশি জটিল, এই আর কি!
প্রতি বছর জুনে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলোয় বাজেট নিয়ে যত লেখালেখি হয়, তাতে ছোটবেলা থেকে প্রতি বছরই আশা করে থাকতাম— এই তো, আগামী বছর বদল আসবেই। বড় হতে হতে আশাটা কমতে থাকল এবং এ বছর আবার একই রকম লেখালেখি দেখে ভাবলাম নিজেই একটু কলম ধরি। আমি লিখব শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ বাজেট নিয়ে। কারণ শিক্ষাক্ষেত্র শুধু যে আমার পড়াশোনার মূল ক্ষেত্র তা নয়, এটা আমার আগ্রহেরও জায়গা। অনেকেই বরাবরের মতো এ বছরও এটা নিয়ে লেখালেখি করেছেন, বলেছেন। সব বক্তব্যের আসল সারমর্ম হলো যে শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের বরাদ্দ বাড়াতে হবে বাংলাদেশে। কেন? কারণ ইউনেস্কো বলেছে যে শিক্ষায় সরকারের ব্যয় জিডিপির অনুপাতে অন্তত ৪ থেকে ৬ শতাংশ এবং মোট বাজেটের অন্তত ১৫ শতাংশ হওয়া উচিত। তাই বেশির ভাগ মানুষই ক্ষিপ্ত যে কেন তিন বছর ধরে শিক্ষায় জিডিপির অনুপাতে বরাদ্দ ২ দশমিক শূন্য ৮ থেকে ১ দশমিক ৭৬ শতাংশে নেমে এল। মোট বাজেটের অনুপাতে শিক্ষায় সরকারের ব্যয় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১ দশমিক ৫৭ শতাংশ—এটিও ইউনেস্কোর হিসাবে কম। আমিও একমত, শিক্ষায় বাজেটের বরাদ্দ বাড়ানো উচিত, কিন্তু আমার দুটো আপত্তি আছে এ ব্যাপারটা আমরা কীভাবে চিন্তা ও আলোচনা করছি তা নিয়ে। এ দুটো আপত্তি কী তা বলার আগে নিজেদের মনে করিয়ে দিতে চাই ছোটবেলায় বড়দের বলা সেই কথা—টাকা গাছে ধরে না। শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো মানে অন্য কোনো খাত থেকে টাকা কমিয়ে ফেলা। কোথা থেকে কমানোর পরিস্থিতি আছে আমাদের? স্বাস্থ্য খাতের যা-তা অবস্থা, রাস্তাঘাট তলিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টিতে। আবারো, খাবার টেবিলের মতোই পরিস্থিতি। যদি একটি পরিবারের সবদিক থেকেই পুষ্টির অভাব থাকে, তাহলে তো সহজে সবজিতে বরাদ্দ টাকা কমিয়ে মাছে দেয়া যায় না। পরিবারটির সবজি খাওয়াও খুব দরকার, মাছের আমিষ ও গুণাগুণেরও খুব অভাব।
আমার প্রথম আপত্তি হচ্ছে যে আমরা শিক্ষায় বরাদ্দ বাজেট বাড়ানোর কথা বলি কিন্তু যতটুকু বরাদ্দ হয়েছে তা কীভাবে ও কোন খাতে ব্যবহার হচ্ছে তা নিয়ে খুব একটা আলাপ করি না। এখানে লক্ষ্য বা নিয়তের বড় একটা প্রভাব আছে। শিক্ষার পেছনের লক্ষ্য কী? শিক্ষা থেকে আমরা কী চাই? একজন শিক্ষিত মানুষ, একটি শিক্ষিত জাতি বলতে আমরা কী বুঝি? নিয়তই সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করবে—এটি নির্ধারণ করবে যে আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে কোন লক্ষ্যগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছি। যেমন ধরুন, খাবারের পেছনে সীমিত বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে মা কীভাবে বণ্টন করবেন তা ঠিক হবে মায়ের লক্ষ্যের ওপর এবং পরিবারের প্রয়োজনের ওপর। মায়ের প্রধান লক্ষ্য যদি থাকে সন্তানদের পুষ্টিময় খাবার খাওয়ানো, তাহলে মা সেভাবে বরাদ্দ বাজেট ভাগ করবেন ফলমূল, শাকসবজি, দুধ ডিমের ওপর।
এক্ষেত্রে কয়েকটা প্রশ্ন জাগে স্বভাবতই। মা কীভাবে জানেন পরিবারের প্রয়োজনগুলো কীভাবে মেটাতে হবে? কীভাবে জানবেন যে সন্তানদের কোন খাবারগুলো দিলে তারা সুস্থভাবে বড় হবে? এক কথায় উত্তর যদি দিতে হয় তাহলে এসব প্রশ্নের উত্তর হবে তথ্য। যাদের হাতে দায়িত্ব থাকে বাজেটের, তাদের কাছে তথ্য থাকতে হবে যে কীভাবে, কোন কোন খাতে, কম-বেশি বাজেট কোথায় বণ্টন করতে হবে। শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে মনে রাখা জরুরি যে আমাদের সবদিকেই সংকট আছে—আমাদের ক্লাসরুমের সংকট আছে দেশব্যাপী আবার আমাদের ক্লাসরুমের ভেতরের অনেক বিষয়েরও সংস্কার দরকার। আমরা অনেকদিন ধরে পরিমাণের ওপর মনোযোগ দিয়েছি যার কারণে শিক্ষার গুণমানের অবহেলা হয়েছে। লক্ষণীয় যে অনেক অসমতা রয়েছে আমাদের দেশে, যার কারণে সবাই সমান সুযোগ পায় না শিক্ষাক্ষেত্রে। গ্রাম-শহরের শিক্ষা সরবরাহে অসমতা আছে, অনেক ক্ষেত্রে টাকা-ধন-সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত বৈষম্য তো আছেই। এসব বিষয়ে মনোযোগ দিতে হলে শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে আমাদের অনেক বিষয়ে নতুন করে ভাবতে হবে, প্রশ্ন তুলতে হবে। প্রথমে নিয়তের ব্যাপারে একমত হতে হবে এবং এ নিয়ত দেশের বেশির ভাগ জনগণের নিয়তের প্রতিফলন হতে হবে, শুধু মুষ্টিমেয় শক্তিধর ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নিয়তের প্রতিফলন নয়। একদিকে নিয়ত যেমন নিয়তি নির্ধারণ করবে, অন্যদিকে মনে রাখতে হবে যে তথ্যের খাঁটি উৎস লাগবে এবং এক্ষেত্রে একটাই উপায় আছে—নির্ভরযোগ্য গবেষণা যা নিয়ে এল আমাকে আমার দ্বিতীয় আপত্তিতে।
শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ ও বণ্টন উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিৎ গবেষণা দ্বারা সমর্থিত—আমাদের দেশের বাস্তবতায় করা গবেষণা। অন্য দেশের ওপর করা গবেষণার ভিত্তিতে নয়। কারণ দেশভেদে, কনটেক্সট-ভেদে তারতম্য থাকতেই পারে। আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বলেছে বলে বাজেট বরাদ্দের জন্য জোরদার না করে আমাদের গবেষণা থেকে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের দেশের জন্য এ সময়ে শিক্ষার বাজেট কত হওয়া উচিত, কেন তা হওয়া উচিত। নিজেরা গবেষণা না করে অন্ধভাবে বাইরের শক্তিদের কথা শুনতে থাকা ঠিক হবে না। এর ফলে আমরা বিপদে পড়ব সামনে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এজন্য চিন্তা, চেতনা, পদ্ধতি ও গবেষণার ‘ডিকলোনাইজেশন’ নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, কাজ হচ্ছে। এটি নিয়ে আমাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। পরিবারকে, পরিবারের কর্তাকে জানতে হবে পরিবারের প্রয়োজন সম্পর্কে যেন সে নির্ধারণ করতে পারে খাবারের টেবিলে কী খাওয়া দেয়া হবে এবং জানতে হবে যে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হলে সেটা কীভাবে কোথায় বণ্টন করা হবে, কীভাবে প্রয়োজন অনুসারে সমবণ্টন করা হবে। সমান সমান ভাত প্লেটে বণ্টন করে দিলেই সমবণ্টন হয় না। কারণ টেবিলে পরিবারের সব সদস্যের প্রয়োজন এক নয়। নিজেদেরকে পড়াশোনা করে প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে হবে, নিজেরা জানতে হবে যে বাজেট কত বাড়াতে হবে এবং পরিষ্কার থাকতে হবে যে বাজেট কেন বাড়াতে হবে। পাশের বাড়ির কর্তা বলেছে বলে খাবারের বাজেট বাড়াতে হবে বা বনানীর বাড়িগুলো বাজেট বাড়িয়েছে বলে ধানমন্ডিতেও বাড়াতে হবে—এটি সঠিক গন্তব্যে ভুল পথে পা বাড়ানোর শামিল।
সময় এসেছে খাতা-কলম নিয়ে বসে ঠিক করার যে আমরা শিক্ষা থেকে কী চাই। এটিও ঠিক যে সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনও বদলায়। একসময় দেশের লক্ষ্য থাকবে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক বানানো, কিন্তু সময়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে লক্ষ্য হবে দক্ষ ন্যায়বান নৈতিক মানুষ বানানো। আমাদের আগামী ৫০ বছরের লক্ষ্যই ঠিক করে দেবে আমাদের পথ। জুনে গত বাজেট নিয়ে না লিখে আমি জুলাইয়ে আগামী বাজেট নিয়ে মনের কথাগুলো লিখলাম যেন আমরা সময় নিয়ে বিষয়গুলো আলোচনা করতে পারি। যেন আমাদের লেখা, আমাদের কথা, আমাদের বকবক থেকে কিছু বদল আসে। আশা রাখলাম।
রুবাইয়া মোরশেদ: প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বর্তমানে যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষক