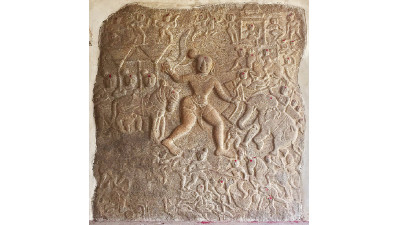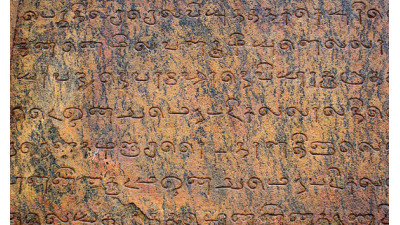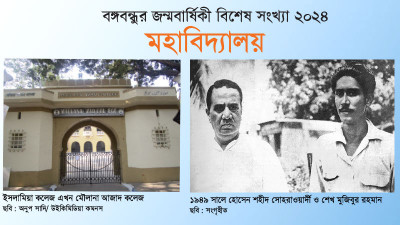দার্শনিক কনফুসিয়াস প্রাচীন হার্প এবং লুটের সুরের ঐক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, এ হচ্ছে স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে সুখময় মিলনের মতো। হাফেজ ইব্রাহিম বলেছেন, আমরা ছিলাম সৃষ্টিকর্তার হাতের লুটের মতো। তার উষ্ণ শরীর থেকে সরে আসার পর তার কাছে ফিরে যাওয়ার সার্বক্ষণিক আকুলতা এ যন্ত্রের সুরে। লুট তারনির্ভর একটি বাদ্যযন্ত্র। তারের সংখ্যা দুটির বেশি। গিটারের চেয়ে ছোট। প্রাথমিক দৃষ্টিতে অদ্ভুত গিটার ভাবলেও ভুল হবে না। পারস্যের কবি জালালউদ্দিন রুমির ভাষ্য: আমরা তো লুট। এর চেয়ে কম কিছু নই, এর চেয়ে বেশি কিছু নই। এর ধ্বনি ধারণ করার বাক্স যদি সুর ছাড়া অন্য কিছুতে পূর্ণ করা হয়, যখন তোমার আহার ও পানীয় অঢেল, যেখানে তোমার আত্মা থাকার কথা সেখানে শয়তান বাস করে। কাহলিল জিবরান আকৃষ্ট হয়েছেন এ যন্ত্রের তারের প্রতি। লুটের তার যেমন একাই নৃত্য করে সুর এসে তাকে তূণে ভরে নেয়। কাহলিল জিবরান আরো বলেছেন, বাটালিতে কেটে যে কাঠকে ফাঁপা করা হয় সেই লুটই কি তোমার আত্মাকে প্রশান্তি দেয় না? কবি জন মিলটন অ্যাপোলার লুটে শনাক্ত করেছেন ঐশ্বরিক দর্শন—মধুমাখা মিষ্টান্নের অনন্ত ভোজ। জালালউদ্দিন রুমি বলেছেন, আমি তোমাকে লুটের মতো শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে চাই, যাতে আমরা ভালোবেসে একসঙ্গে কেঁদে উঠতে পারি। রুমি আরো বলেছেন, আমরা তো লুটের মতো। ধ্বনি ধারণের বাক্স যখন পরিপূর্ণ তখন কোনো সুর আসে না। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক ও পাকস্থলী যখন ক্ষুধায় জ্বলতে থাকে, প্রতি মুহূর্তে অগ্নিদহন থেকে সুর উঠে আসে। অস্কার ওয়াইল্ড লিখেছেন, জীবন ও ভালোবাসা যখন পরস্পরের প্রতি সুবিচার করে তখন বেহালার সুরে নাচা বড় আনন্দের কিন্তু বাঁশি ও লুটের সঙ্গে নাচা বড় কঠিন, সংবেদনশীল এবং কদাচিৎ তা ঘটে থাকে। জিওভান্নি বোক্কাচিওর (১৩১৪-৭৫) প্রধান গ্রন্থ ডেকামেরন-এর একটি অন্যতম চরিত্র ডিওনিও একজন লুটবাদক, গান ও নৃত্যে সংগত করে থাকে। ডেকামেরনের একটি বর্ণনা—নৈশভোজ শেষ হলে রানী সংগীতের বাদ্যযন্ত্র আনতে বললেন। লরেটো নৃত্যে নেতৃত্ব দিল আর এমিলিয়া গাইল গান, সবটার সঙ্গে থাকল ডিওনিওর লুটবাদন। ফ্রান্সেসকো পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) বোক্কাচিওর দীক্ষাগুরু, পাশ্চাত্যের মানবতাবাদের জনকখ্যাত এ প্রেমিক কবি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বড় বাদক ছিলেন। সনেটের উদ্ভাবন তারই হাতে। তার প্রেমিকা লরার মৃত্যুর (গবেষকরা মনে করেন প্রেমটা একপক্ষীয় ছিল, পেত্রার্কই মজেছিলেন) পর তার মনে হয়েছে আর্ফিয়ুস যেমন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মৃত্যুপুরীতে ইউরিডাইসকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, আমিও লরাকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারব। অর্ফিয়ুসের সেই যন্ত্রকে শেকসপিয়ার বলছেন লুট— Orpheus
with his lute made trees And the
mountain tops that freeze Bow
themselves when he did sing: To his
music plants and flowers Ever
sprung; as sun and showers There
had made a lasting spring. আরো প্রাচীন লায়ার রেনেসাঁ যুগে লুট হয়ে লায়ারের সব পৌরাণিক জাদু ও শক্তি নিয়ে বিকশতি হয়েছে। পেত্রার্ক যে যন্ত্রটি বাজাতেন গবেষকরা মনে করেন তা হচ্ছে লুট। পেত্রার্কের প্রায় ৩০০ বছর পর একজন ফরাসি প্যাট্রন লুটের ৪৬টি কম্পোজিশন উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজ লুটবাদক ও ফরাসি লুটবাদক পরস্পরের প্রতিযোগী ছিলেন। ইংরেজের গান ছিল হোমোফোনিক—একই সুরে পুরো গান। কিন্তু ফরাসিটা পলিফোনিক, একাধিক সুরসংবলিত, চারটি পর্যন্ত সুর। রেনেসাঁ লুট ছিল আট তারের, পরে তা ১৩ তারধারী হতেও দেখা যায়। খোল তৈরি হতো স্প্রুস-জাতীয় বৃক্ষের কাঠ থেকে। মনে করা হয়, হাজার বছরের পুরনো আরবীয় বাদ্যযন্ত্র উদ থেকে লুট যন্ত্রটি উদ্ভূত। স্প্যানিশ অঞ্চলে মুরদের মাধ্যমে প্রবেশ করে একসময় ইউরোপ জেঁকে বসে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় যুদ্ধের বর্ণনায় সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করা বাদ্যযন্ত্র লুটের নাম এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ভারতীয় সেতার সম্পূর্ণ মৌলিক একটি বাদ্যযন্ত্র হলেও তা লুটের অনেকটাই কাছাকাছি। ইউরোপীয় বিশ্লেষকরা সেতারকে লুট গোত্রভুক্ত করতে পছন্দ করেন। রেনেসাঁর সময় লুটের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছে। ইতালির লুটবাদকরা প্রথম নবজাগরণের সুর ছড়াতে থাকেন। বাদ্যযন্ত্রটি গণমানুষের সুর তোলার যন্ত্রে পরিণত হয়। রাস্তাঘাটে, উৎসবে-পার্বণে লুটবাদন অনির্বাণ অনুষঙ্গ করে ওঠে। অতঃপর ফরাসি ও স্পেনীয় লুটবাদকরা এতে নিজ নিজ সংস্কৃতির মাত্রা যোগ করেন। ইউরোপে শ্রেণী নির্বিশেষে স্বল্পমূল্যের এ বাদ্যযন্ত্র এক ধরনের সাংস্কৃতিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই নিজে দক্ষ লুটবাদক ছিলেন। রাজা ও রানী নতুন সুর সৃষ্টি করতে শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন। পলিফোনি বা বহু সুর সমন্বয় মূলত জার্মান অবদান। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী সুর ও ছন্দের স্বাধীনতার কাল। এ সময় ইতালি ও ফ্রান্সের স্বরগ্রাম বিতর্ক পরবর্তী সময়ে সংগীতের ইউরোপীয় সর্বজনীন ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে শুরু করে গোটা ষোড়শ শতাব্দী ইউরোপীয় সংগীতের স্বর্ণযুগ। সপ্তদশ শতাব্দীতে আসে ব্যারোকশৈলী, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোকো। লুট এ বিবর্তনে অপাঙেক্তয় হয়ে ওঠেনি বা পরিত্যক্ত হয়নি, বরং বিবর্তিত হয়ে ধ্বনি স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখেছে। রেনেসাঁ যুগের শেষে ব্যারোক যুগে লুট আকারে বড় হয়েছে। শুরুতে পৃথক অঙ্গুলি দিয়ে লুট বাজানো হতো। পরবর্তী সময়ে লুট কারিগররা একে আঙুলে সুর বাজানোর উপযোগী করে তোলেন। শেষের দিকে লুটের তার নাইলন কিংবা ধাতব ইস্পাত থেকে তৈরি হলেও শতকের পর শতক মৃত প্রাণীর অন্ত্র থেকে তা তৈরি করা হতো। লুট যন্ত্রের কাঠের খোলের নামটি কৌতুহলোদ্দীপক—রোজ কিংবা গোলাপ। খোলের ভেতরের কাঠ চেঁছে তুলে আনার বিষয়টি কেবল দক্ষ কারিগরের কাজ। সে কারিগরের থাকতে হয় অসাধারণ সুর ও ধ্বনিজ্ঞান। খোলের কোথায় কতটুকু গভীরতা থেকে কেমন ধ্বনি উদ্গত হবে সেই জ্ঞান ছিল জরুরি। রেনেসাঁকালের লুটকে কেউ বলেছেন ‘বাদ্যযন্ত্রের রানী, কেউ বলেছেন ‘ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাঞ্জেল’। বিশ্বখ্যাত সুরস্রষ্টা বাখ একটি লুটযন্ত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি এর জন্য কিছু সুরযোজনাও করেছিলেন। একই সময় লুট এ তার সংযোগ করে এবং হংসকণ্ঠ ডিজাইন দিয়েছিলেন জার্মান সুরকার সিলভিয়াস লিওপোল্ড ওয়েইস। সেবাস্টিয়ান বাখ ও ওয়েইসের মৃত্যুর পর ১৭৫০ থেকে লুট প্রায় পরিত্যক্ত বাদ্যযন্ত্রে পরিণত হয়। ইতালির লুটবাদক ভিনসেনজো ক্যাপ্রিয়োলাই লুট সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। তার দ্য ক্যাপ্রিয়োলা লুটবুক হচ্ছে একমাত্র আকরগ্রন্থ। ১৫১৫-২০ সালের মধ্যে গ্রন্থটি লিখিত। শেকসপিয়ারের একাধিক কাব্যতে লুট অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে ধ্বনিত হয়েছে। বিশেষ করে লুট হাতে নারী পুরো রেনেসাঁজুড়ে চিত্রশিল্পীদের একটি প্রিয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। ডাচ স্বর্ণযুগের চিত্রশিল্পী ইউহানেস ভারমিয়ার এঁকেছেন ‘ওমেন উইথ আ লুট’ নামের একাধিক ছবি। অর্থনৈতিক মন্দা, মহামারী প্লেগ, ছবি আঁকার পেছনে বিপুল ব্যয় তাকে নিঃস্ব করে তুলেছিল। তিনি সবচেয়ে দামি রঙ ব্যবহার করে ছবি আঁকতেন। জোনাথান রিচম্যান ভারমিয়ারকে নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, ‘ভারমিয়ারের মতো আর কেউ নেই।’ ১৬৬২-৬৫ সময়জুড়ে তিনি এঁকেছেন। মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট নিউইয়র্কে রক্ষিত ৫১.৪*৪৫.৭ সেন্টিমিটার মাপের তেলরঙ ‘ওমেন উইথ আ লুট’ ছবিটি। জিওভান্নি বাতিস্তা ডি জ্যাকোপে (১৪৯৫-১৫৪০) এঁকেছেন ‘অ্যাঞ্জেল প্লেইং দ্য লুট’; কারাভাজ্জিও (১৫৭১-১৬১০) যখন ক্যানভাসের ওপর ব্রাশ চালাতে শুরু করলেন আধুনিক পেইন্টিংয়ের যুগ শুরু হলো। সেই শিল্পী এঁকেছেন ‘দ্য লুট প্লেয়ার’। পল পিটার রুবেনস (১৫৭৭-১৬৪০) এঁকেছেন ‘লুট প্লেয়ার’। স্যার থমাস উইয়াট যে নারীকে ভালোবেসেছিলেন তার নির্মম প্রত্যাখ্যানের শিকার হয়ে লিখেছিলেন, ‘প্রেমিক লুট কখনো দোষী হতে পারে না।’ তারপর তিনি লিখেছেন, ‘জেগে ওঠো আমার লুট।’ পল লরেন্স ডানবার লিখেছেন, ‘তুমিই আমার জীবন লুট, আমি তোমারই গান গাই।’ থমাস দ্য কেয়সারের সপ্তদশ শতাব্দীর কবিতা: লুট তুমি আমার অশ্রুর সাক্ষী লুট তুমি আমার আনন্দের সাক্ষী। পৃথিবীর একদার অনুরণন লুট ঊনবিংশ শতাব্দীতেই লুপ্তপ্রায় তারযন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এখন বাদকের হাতে নেই; আছে বাদ্যযন্ত্রের জাদুঘরে।
এম এ মোমেন: সাবেক সরকারি কর্মকর্তা
তরুণী লুটবাদক। শিল্পী: ওরাজিও জেনটিলেশি, ১৬২৬