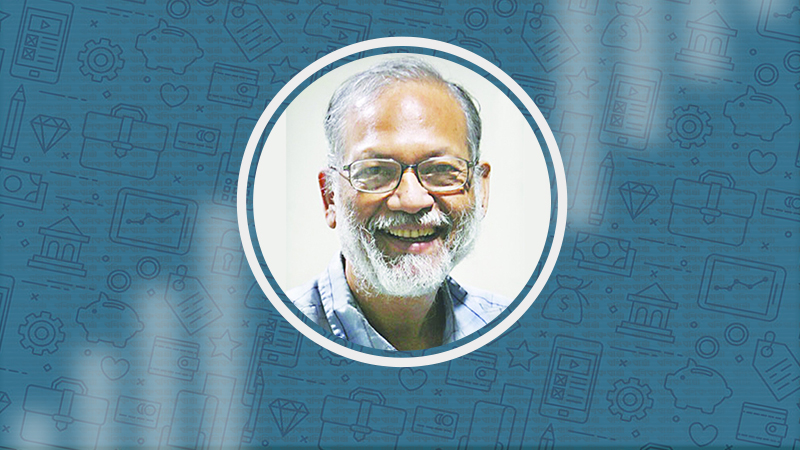
প্রায় এক মাস অসহযোগ আন্দোলন চললেও সশস্ত্র আক্রমণ হলে কীভাবে তা প্রতিহত করতে হবে সে সম্পর্কে দেশবাসীর কোনো ধারণা ছিল না। যুদ্ধের ব্যাপকতা সম্পর্কে কোনো পক্ষেরই ধারণা ছিল না। অর্থাৎ পাকিস্তানিরাও প্রতিরোধের ব্যাপকতা অনুমান করতে পারেনি। ২৫ মার্চের পর যখন চারদিকে প্রতিরোধ গড়ে উঠল তখন বাংলাদেশী যোদ্ধাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাঁচটি বেঙ্গল রেজিমেন্টের (প্রথম বেঙ্গল—যশোর, দ্বিতীয় বেঙ্গল—জয়দেবপুর, তৃতীয় বেঙ্গল—সৈয়দপুর, চতুর্থ বেঙ্গল—কুমিল্লা এবং অষ্টম বেঙ্গল—চট্টগ্রাম) বাঙালি সৈন্য, সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর বাঙালি ইপিআর সৈনিক এবং পুলিশ, আনসার ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধের মূল যোদ্ধা। এ কারণে যুদ্ধ শুরু হলে প্রথমেই চিন্তা করা হয় সহযোগী গ্রুপ তৈরির। বাংলাদেশী সৈনিক-অফিসার যেখানে যেভাবে সুযোগ পেয়েছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এক থেকে সাতদিনের স্বল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের মূল বাহিনীর সহায়ক শক্তিরূপে প্রস্তুত করা হয়। এদের মধ্যে ছিল আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র, যুবকসহ উৎসাহী জনতা। এর মাধ্যমে প্রতিরোধটা কেবল সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনপ্রতিরোধে রূপ নেয়।
দ্বিতীয় সমস্যা ছিল খাদ্য সমস্যা। মাত্র কয়েক দিনে প্রদেশের অধিকাংশ স্থান যোদ্ধাদের করায়ত্ত হলেও পাকিস্তানিরা সেগুলো দখল করতে থাকে। ফলে যোদ্ধাদের বারবার অবস্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছিল। এ সময়কালে নিয়মিত খাদ্যের জোগান ঠিক রাখতে সমরবিদদের নতুন পথ অবলম্বন করতে হয়। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষ এ খাদ্য সরবরাহে এগিয়ে আসে এবং প্রতিরোধের অংশ হয়ে যায়।
তৃতীয় সমস্যা ছিল যুদ্ধোপকরণ বা অস্ত্রশস্ত্রের সমস্যা। প্রতিরোধ শুরু হতেই অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাব অনুভূত হয়। এটা সমাধানের জন্য পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন প্রতিবেশী (সেই হিসেবে বাংলাদেশের বন্ধু) ভারতের সাহায্যের আশা করা হয় এবং যোগাযোগ শুরু হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায়নি, বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ের সক্রিয় প্রতিরোধের সময়। এছাড়া যাতায়াত, অবস্থানগত এবং আহতদের চিকিৎসা সমস্যাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু প্রতিরোধ স্বতঃস্ফুর্তভাবে গড়ে ওঠে, তাই এ দিকগুলো নজরে আসে। এ কারণে প্রতিরোধের আর্থসামাজিক চিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ।
প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র
প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুতেই বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে সংগ্রাম কমিটি। ২৬ মার্চ টাঙ্গাইলে মির্জা তোফাজ্জেল হোসেন এমপিএর আহ্বানে গঠিত হয় ‘স্বাধীন বাংলা গণমুক্তি পরিষদ’। এ পরিষদ সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বদিউজ্জামান খানকে সভাপতি এবং আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করে। এটি ‘হাইকমান্ড’ নামে পরিচিত ছিল। পুরনো কোর্ট ভবনে হাইকমান্ডের অস্থায়ী কার্যালয় করা হয়। ৩০ মার্চ হাইকমান্ড নির্দেশ জারি করে—
ক. অস্ত্র থানায় জমা না দিয়ে হাইকমান্ডে জমা দিতে হবে। খ. থানার অস্ত্রও হাইকমান্ডের নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে। গ. স্থানীয় ব্যাংক হাইকমান্ডের নির্দেশে লেনদেন করবে। ঘ. অবস্থাপন্নদের কাছ থেকে নির্ধারিত অংকের টাকা নিয়ে হাইকমান্ডের তহবিল গঠন করা হবে। ঙ. ‘গণমুক্তি বাহিনী’ গঠন করা হয়। ‘আর্মস সেল’ অস্ত্র সংগ্রহ করে তাদের সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।
উল্লেখ্য, বদিউজ্জামান, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, আবদুল মতিন, আল মুজাহিদী এবং ডিসি ও এসপিকে নিয়ে এই আর্মস সেল গঠন হয়।
২ এপ্রিল নাটোরের মহকুমা প্রশাসক কামালউদ্দিনের সভাপতিত্বে তারই কক্ষে গঠিত হয় ‘জয় বাংলা বাহিনী’। আনসার কমান্ডার ইউসুফসহ কয়েকজন ২ এপ্রিল থেকে সাতদিনের এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শিবির করেন। এ সংক্ষিপ্ততম প্রশিক্ষণের পর জয় বাংলা বাহিনীকে ট্রেজারির অস্ত্র সরবরাহ করা হয় নাটোরে পাক আগমন প্রতিহত করতে।
বগুড়ার মহকুমাগুলোতেও ২৫ মার্চের পর ছাত্র-জনতা ও তরুণদের নিয়ে ‘মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠন হয়। কিন্তু এর সদস্যরা প্রতিরোধে অগ্রসর হলে পাক আক্রমণে হতাহত হয়ে ফিরে আসে। কুড়িগ্রাম মহকুমায় সংগ্রাম পরিষদ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ‘গণপ্রতিরোধ বাহিনী’ গঠন করে। এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বাঙালি ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র, যুবক ও জনতা। সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা থানা থেকে তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেন। এ যোদ্ধারা কিছু দিন তিস্তা ব্রিজ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।
নোয়াখালীতে ২৬ মার্চ টাউন হলের পাবলিক লাইব্রেরিতে স্বাধীনতাযুদ্ধের কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। এখানে অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সৈনিক, ইপিআর ও আনসারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। জেলার প্রতিটি থানায় অনুরূপ শিবির গড়ে ওঠে।
স্থানীয়ভাবে এসব প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। তবে যুদ্ধরত বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা সৈন্যস্বল্পতা বিবেচনা করে সহযোগী গ্রুপ তৈরি করতে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গড়ে তোলেন। মেজর সফিউল্লাহ ৪ এপ্রিল থেকে তেলিয়াপাড়ায় একটি ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করেন। মেজর নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে মাত্র কয়েকজন অফিসার ও ইনস্ট্রাক্টরকে নিয়ে এই ক্যাম্প চালু হয়। এখান থেকে প্রায় ৫০০ যুবককে প্রাথমিক ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সহযোগী বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছিল। মেজর খালেদ মোশাররফ তার হেডকোয়ার্টারে ক্যাপ্টেন হায়দার ও হাবিলদার মুনিরের মাধ্যমে একটি ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করেন। মেজর জিয়াও রামগড়ে এরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন।
যোদ্ধাদের প্রধান সমস্যা ছিল খাদ্যের। এ সমস্যা মোকাবেলা করতে যুদ্ধরত অফিসাররা প্রধানত নির্ভর করেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জেলার বা মহকুমার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার ওপর। মেজর সফিউল্লাহ ২৯ মার্চ ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের অফিসাররা, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনাসংক্রান্ত এক বৈঠক করেন। বৈঠকে জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামরিক বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ভার বেসামরিক প্রশাসন এবং পরিষদ সদস্যদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। জনগণের সহযোগিতায় তাদের খাদ্যের জন্য বড় ধরনের কোনো সমস্যা প্রতিরোধকালীন হয়নি। মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যুদ্ধের বেসামরিক কার্যক্রমের জন্য মহকুমা প্রশাসকের কাছে সাহায্য কামনা করেন। মহকুমা প্রশাসক স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় রসদ সরবরাহ, যানবাহন জোগাড়, সৈনিকদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা, চিকিৎসা এমনকি আর্থিক সহায়তা করেন। তবে যখন তিনি ট্রেনিং সেন্টার খোলেন এবং এক হাজার বা তারও বেশি যুবক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে তখন খাদ্য সমস্যা তৈরি হয়। এ সময় রসদ, অর্থ এবং থাকার জায়গার অভাব দেখা দেয়।
চুয়াডাঙ্গায় মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর আহ্বানে তার বাসায় ক্যাপ্টেন এআর আযম চৌধুরী, এমপিএ ডা. আসহাবুল হক, পুলিশ কর্মকর্তা এবং বেসামরিক প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এক বৈঠকে মিলিত হন। এখানে মেজর ওসমানকে সামরিক ও বেসামরিক প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখান থেকে কুষ্টিয়া আক্রমণের যে পরিকল্পনা করা হয় তার বেসামরিক দিকগুলো ছিল।
ক. টেলিফোন বিভাগের সহায়তায় পোড়াদহে ফিল্ড এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা করা। খ. ডা. আসহাবুল হকের নেতৃত্বে ফিল্ড চিকিৎসা কেন্দ্র, ডাক্তার ও ওষুধের ব্যবস্থা করা। গ. খাদ্য সরবরাহের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কিছু অংশকে কুষ্টিয়ার আওয়ামী নেতারা ও নেতৃস্থানীয়দের কাছে পাঠানো হয় যেন তারা সম্পূর্ণ বাহিনীর খাদ্যের ব্যবস্থা করে। ঘ. স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে যথাস্থানে কাজে লাগানো।
উল্লেখ্য, কুষ্টিয়ার প্রতিরোধযুদ্ধে এমপিএদের আহ্বানে প্রতিটি ইউনিয়ন, গ্রাম থেকে খাদ্য পাঠানো হয়।
যশোরের প্রতিরোধের প্রাথমিক অবস্থায় পুলিশরা নিউটাউনের আমবাগানে একটি রাইফেল চালনা শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এখানে শতাধিক উৎসাহী যুবক অংশ নেয়। এ প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন বাড়ি থেকে আহরিত চাল, ডাল প্রভৃতি নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তা হিমাংশু ব্যানার্জির স্ত্রীর নেতৃত্বে স্থানীয় মেয়েরা নিয়মিত রান্নার ব্যবস্থা করে। এছাড়া নড়াইল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের যে দলটি যশোরের উদ্দেশে আসে তাদের সঙ্গে রান্না করা, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা ও উৎসাহ দিতে ১১ জন মেয়ের সমন্বয়ে একটি গ্রুপ আসে।
ভারতগামী শরণার্থীদের খাদ্যের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে মং রাজা মং প্রু সেন এবং গর্ভবতী মহিলাদের তার স্ত্রী সহায়তা করেন।
খাদ্যের সমস্যা মূলত এজন্য হয় যে জনগণ একবারে খাদ্য জোগাড় করতে পারে। কিন্তু যদি সেটা অনেক ব্যক্তির জন্য এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় তবে সেটা চালিয়ে নেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—
১. ক্যাপ্টেন এমএসএ ভূঁইয়া কুমিরা সংঘর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ‘আমাদের সৈন্য বোঝাই ট্রাকগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। এমন সময় একজন বুড়ো লোক তার পথের পাশের দোকান থেকে সিগারেট নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিল। বলল: স্যার আমি গরিব মানুষ, কিছু দেওয়ার মতো আমার ক্ষমতা নেই, এই নিন আমার দোকানের সিগারেট (সিগারেট তিন কার্টন ছিল); আপনার জওয়ানদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। আর একজন একটি ট্রাকে করে প্রায় এক ড্রাম কোকা-কোলা নিয়ে এল। কেউ কেউ খাদ্যসামগ্রীও নিয়ে এল।’
২. মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া ও তার দলের আখাউড়ার দক্ষিণে উজানিশর বিল অতিক্রম করতে গিয়ে পাকসৈন্যদের অবস্থানের কারণে একদিন পাশের গ্রামে থাকতে হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, ‘সানকিতে করে দুপুরের খাবার এল। চেয়ে দেখে মনে হলো বড় মাছের ডিম ঝোল দিয়ে পাতলা করে রান্না করা। মনে করলাম, নিশ্চয় আমার জন্য বিশেষ কোনো আয়োজন। প্রচণ্ড ক্ষুধায় হাত বাড়িয়ে সানকি নিলাম, মুখে দিয়ে দেখি বিস্বাদ, পানসা পানসা লাগে। জিজ্ঞাসা করতেই লোকটি বলল, ‘কাউনের জাও স্যার। গরিব মানুষ আমরা। চাইলে বছরের খোরাক অয় না।’ এ জিনিস কী করে খেতে হয়—চুমুক দিয়ে না লোকমা দিয়ে, দ্বিতীয় চিন্তা না করে চুমুক দিতে শুরু করলাম।
৩. তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে কুমারখালী থানার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক এবং কুষ্টিয়ায় প্রতিরোধযুদ্ধের সহযোগী রেজাউল করিম হান্নানের ক্ষেত্রে। ১১ এপ্রিল যখন পাকবিমান কুমারখালীতে বোমাবর্ষণ করে তখন তার নেতৃত্বে একটি দল পাংশার বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নেয়। তিনি যে বাড়িতে আশ্রয় নেন সে বাড়িটি ছিল এক অতি দরিদ্র একজনের বাড়ি। সেখানে থেকে মাতবরের বাড়িতে খেতে যাওয়ার কথা সবার। কিন্তু বুড়ি তাকে খাবারের দাওয়াত করেন। অন্যরা মাতবরের বাড়িতে গেলেও বুড়ি জোর করে ‘মুক্তিরে খাওয়াইবো’ বললে তিনি থেকে যান। বুড়ি যবের ময়দার রুটি আর কচুরিপানার ফুলের ডাঁটা ঘণ্ট করে দেন। তিনি বলেন, ‘আমি জীবনে রুটিই খাইনি। কিন্তু বুড়ি যখন গালে তুলে দিচ্ছিল তখন না করি কীভাবে?’
প্রতিরোধের প্রথমে যোদ্ধারা সফল হলেও সাফল্য ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের। এ কারণে কমান্ডাররা অস্ত্র ও রসদ পাওয়ার চেষ্টা করে। মেজর কেএম সফিউল্লাহ প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সাহায্যের জন্য এমএনএ সৈয়দ আবদুস সুলতানকে দিল্লি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন (২৯ মার্চ)। এছাড়া ক্যাপ্টেন আজিজকে পাঠানো হয় বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। হালুয়াঘাটে ক্যাপ্টেন বালজিতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং লে. কর্নেল সিনহার সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করতে সক্ষম হন।’ তারা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মেজর খালেদ মোশাররফ তার প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের জন্য তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও সাচ্চু মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্রশস্ত্র আনার বন্দোবস্ত করতে বলেন। তাদের প্রচেষ্টায় ভারতের সাড়া পাওয়া যায়। তারা মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আগরতলার জেলা প্রশাসক মি. সাইগলের সাক্ষাৎ করাতে সমর্থ হন। এছাড়া কয়েক দিন পর ৫৭ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল গানজালভেসের সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ হয়। তবে সরকারি নির্দেশ ছাড়া তারা অস্ত্র সাহায্য দিতে অসমর্থ হন। পরে কর্নেল ওসমানীর প্রচেষ্টায় বিএসএফের ব্রিগেডিয়ার পান্ডে মেজর খালেদ মোশাররফের হেডকোয়ার্টারে আসেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তার সহায়তায় কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। তবে এ সাহায্য ছিল খুবই সামান্য—কিছু ৩০৩ রাইফেল ও গুলি।
ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে অস্ত্রের জন্য আগরতলায় সিনিয়র বিএসএফ অফিসার কালিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তবে সরকারি বিধি-নিষেধের কারণে তিনি সাহায্য দিতে সক্ষম হননি। এছাড়া ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিংয়ের সঙ্গেও আলোচনা হয়। তার কাছেও অস্ত্র আর রসদ চাওয়া হয়। তবে আশ্বাসের বেশি কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু ৯২ বিএসএফের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ঘোষ কয়েকটি এলএমজি, রাইফেল, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং কিছু গোলাবারুদ সরবরাহ করেন। ক্যাপ্টেন মেহেক সিংয়ের মাধ্যমে ৪ এপ্রিল এগুলো ক্যাপ্টেন রফিকের কাছে পৌঁছে। সৈন্যদের হতাহত এবং অস্ত্রের অপ্রতুলতায় একের পর এক তাকে অবস্থান ত্যাগ করতে হয়। ক্যাপ্টেন রফিকের ভাষায়, ‘সবচেয়ে নাজুক অবস্থা ছিল আমাদের—অর্থাৎ সমর ক্ষেত্রের কমান্ডারদের, যাদের সৈন্য ও অফিসারদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারটা বোঝাতে হতো।’ মিরসরাই এলাকায় যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘শত্রুর গোলায় আহত এক সৈনিক আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাদের কামানের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের কামানগুলি ব্যবহার করছেন না কেন? এ প্রশ্নের আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি।’ আসলে এ আশ্বাস ভারতীয় আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই দেয়া হয়েছিল।
মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ৫ এপ্রিল বিএসএফের ৭৬ নম্বর ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল এইচআর চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এখানে যশোর আক্রমণের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের তালিকা দেয়া হয়। তিনি অস্ত্র পাওয়ার আশ্বাস দেন বেশ জোরের সঙ্গেই। এমনকি নিজের চেকোস্লোভাকিয়ান এলএমজি সঙ্গে সঙ্গেই দিতে চাইলেন। এছাড়া আইজির অফিসে মেজর বিএন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলেন। এর পর থেকে মেজর ওসমান নিয়মিত আইজি অফিসে সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট করতেন। আর প্রতিবারই শিগগিরই অস্ত্র পৌঁছে দেয়ার আশ্বাস পেতেন। কিন্তু এ সাহায্য আর আসেনি। যশোরও আক্রমণ করা হয়নি। তবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উৎসাহে লে. কর্নেল মেঘ সিং বেনাপোল সীমান্তে লে. হাফিজ ও ইপিআরদের সাহায্যে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু তার কয়েকজন সৈন্য বন্দি হলে আন্তর্জাতিক চাপের কারণে তিনি সরকারি নির্দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন।
মেজর জলিল বরিশালে প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করতে নূরুল ইসলাম মঞ্জুরকে ভারতে পাঠান। তিনি ভারত থেকে ৫০টি এসএমজি, ১৫টি এসএলআর, ২০০টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল, ৩০০টি হ্যান্ড গ্রেনেড, কিছু এনারগা গ্রেনেড ও রকেট লঞ্চার নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এছাড়া বিএম কলেজের কেমিস্ট্রির একজন অধ্যাপক ও তার কয়েকজন সহযোগী হ্যান্ড গ্রেনেড মলোটভ ও ককটেল তৈরি করে। বগুড়ায়ও স্থানীয়ভাবে হাতবোমা তৈরি করা হয় পাক প্রতিরোধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। সিরাজগঞ্জে আবুল মিস্ত্রি ছোট ছোট কামান তৈরি করেন।
এছাড়া অস্ত্র সংগ্রহের জন্য মেহেরপুরের এসডিও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এবং সিরাজগঞ্জের এসডিও শামসুদ্দিন আহমদ ভারতের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেন। শামসুদ্দিন আহমদ ভারতীয়দের কাছে সরাসরি অস্ত্র কিনতে চান। তিনি পশ্চিম দিনাজপুরের এক ভারতীয় কর্নেলের কাছে প্রস্তাব দেন। কিন্তু এভাবে অস্ত্র বিক্রি হয় না বলে এসডিও চরম উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি করেও অস্ত্র জোগাড় করতে পারেননি। এ অবস্থায় এ ধরনের উত্তরে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লে ভারতীয় কর্নেল এসডিও ও সহযোগী মোজাফ্ফর হোসেন উভয়কে পাক গোয়েন্দা মনে করে বন্দি করেন। পরে ছাত্রনেতা ও কংগ্রেস এমপিদের প্রচেষ্টায় তারা ছাড়া পান ।
দেশের ভেতর অস্ত্র সংগ্রহ করা হয় মূলত ট্রেজারি ও পুলিশ লাইনসের অস্ত্রাগার থেকে। এছাড়া কুষ্টিয়া, বগুড়াসহ আরো কিছু এলাকার যুদ্ধে পাক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ হস্তগত হয়।
যাতায়াতের ক্ষেত্রে দেখা যায়—জয়দেবপুর থেকে দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈন্যদের অস্ত্র ও রসদ স্থানীয়দের মাধ্যমে জোগাড় করা ১৬টি ট্রাকের সাহায্যে ময়মনসিংহ পৌঁছানো হয়। মং রাজা তার নিজস্ব গাড়ি সৈনিকদের দেন। তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী ভারতীয় অস্ত্র নিয়ে আসতে দর্শনা চিনিকলের ট্রাক ব্যবহার করেন।
শেষাংশে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো—
১. চুয়াডাঙ্গা উইং কমান্ডার মেজর ওসমানের ছয় বছরের মেয়ে কলি কাগজের ওপর বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে কঞ্চির মাথায় লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছোট শিশুর এ উদ্দীপনা ফরাসি টেলিভিশনের ভ্রাম্যমাণ দলটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা তৎক্ষণাৎ এটি ক্যামেরাবন্দি করেন (৩ এপ্রিল)।
৩০ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ধ্বংস হওয়ার পর ৩ এপ্রিল রাত সাড়ে ৯টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের গোপন স্থান থেকে আরেকটি বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়। ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি দিয়ে এটি চালু করা হয়। গানটিতে কণ্ঠ দিতে আসে চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার আবদুর রহমানের তিন কন্যা। প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রতিরোধের আর্থসামাজিক দিকের পূর্ণাঙ্গ নয়, প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র।
(কথাপ্রকাশ প্রকাশিত ‘১৯৭১ অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ’ বই থেকে নেয়া)
আফসান চৌধুরী: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব






