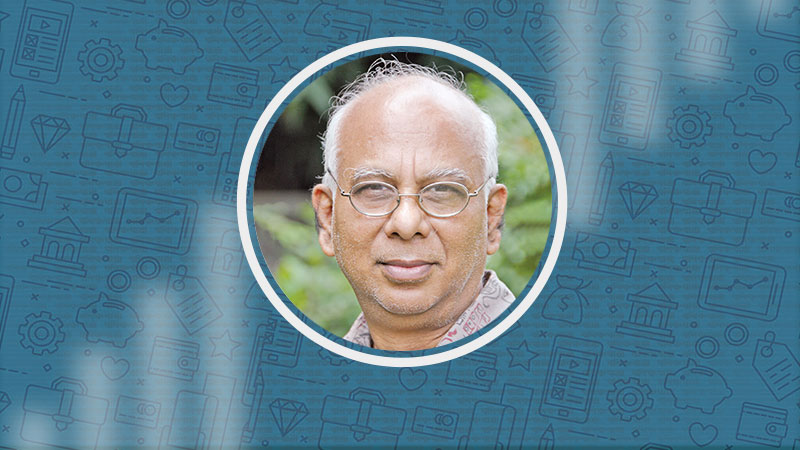
পানি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। সীমিত ও দুর্লভ এ সম্পদের ওপর নির্ভর করে আমাদের খাবার পানি সরবরাহ, দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজ, ফসল সেচ, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, নৌ-চলাচল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, লোনা পানি অনুপ্রবেশ রোধ, জলাশয় পরিবীক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক অবস্থান্তর ও জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় পানিসম্পদ সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান বিশেষ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চারদিকে স্থলজ জলাভূমি ও জলাশয়গুলো দেখলে অনুধাবন করা যায় আগামীতে পানিসম্পদের ঘাটতিতে কী ধরনের ঝুঁকিতে আমরা পড়তে পারি। এগুলোর আয়তন, পরিধি ও ধারণক্ষমতা সংকোচন পানি সংকটের ইঙ্গিত দেয়। দেশের নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, প্লাবনভূমি, বাঁওড়, দিঘি ও পুকুরগুলোয় আগের মতো পানিও থাকে না। অন্যদিকে এগুলো থেকে পানি উত্তোলন করে ফসল সেচ, মাছ চাষ ও গৃহস্থালিকাজে ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আবাদি জমির মাটির পানি ধারণ কমে যাওয়ায় সেচ চাহিদাও ঊর্ধ্বগামী। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলাভূমির পানি ফুরিয়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমে সেচের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ দুষ্কর হয়ে পড়ে। ব্যাপক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে সেচাধীন বহু এলাকায় পানির স্তর হস্তচালিত নলকূপের কার্যকর নাগালের নিচে নেমে গেছে বলে জাতীয় পানি নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শহর ও নগর এলাকায় পানির চাহিদা মেটাতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা পানি সংকটকে আরো প্রকট করে তুলছে।
সামগ্রিকভাবে সর্বোচ্চ পানির চাহিদা কৃষি উৎপাদনে। অর্ধ শতাব্দী আগেও ফসল আবাদে সেচপানির ব্যবহার ছিল নিতান্তই কম। মাটির আর্দ্রতা ধারণক্ষমতা সহায়ক হওয়ায় অধিকাংশ আবাদি জমিতে বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর বিনা সেচে ফসল আবাদে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হতো না। ফসলবিন্যাস ও উৎপাদন ব্যবস্থাও ছিল অনন্য। শুষ্ক মৌসুমে উঁচু এলাকার জমিতে আবাদের জন্য মাটির প্রাকৃতিক আর্দ্রতার ভিত্তিতে ফসল নির্বাচন করা হতো। নিচু জমিতে বন্যার পানি নিষ্কাশনের পর বোরো ধানের চারা রোপণ করে পরবর্তী সময়ে সেচ দেয়া হতো। দেশের মোট আবাদি এলাকার মোটামুটি ১০ শতাংশ ছিল সেচের অধীন। নদ-নদী, খাল, বিল, ছড়া ও ডোবায় অফুরন্ত ভূ-উপরিস্থ পানির ভাণ্ডার ছিল। আড় বাঁধ, সেউতি বা দোন ও নালা ব্যবহারসহ বিভিন্ন স্থানীয় পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হতো। সেচযন্ত্র ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার ছিল সীমিত। মোট আবাদি এলাকার প্রায় ৯০ শতাংশে ফসল আবাদে সেচপানি সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গ্রীষ্মকালের শেষদিকে বৃষ্টিপাতের পর আউশ ধান, পাট ও অন্যান্য ফসলের বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হতো। বর্ষাকালে রোপণ করা হতো আমন ধানের চারা। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতে প্রাকৃতিক আর্দ্রতায় বপন করা হতো হরেক ফসলের বীজ। প্রতিটি ফসলের স্থানীয় উপযোগী অসংখ্য জাত ছিল। এসব জাতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম ছিল খরাসহিষ্ণুতা। বৃষ্টিপাত কম হলেও বা অনাবৃষ্টিতে টিকে থাকার ক্ষমতা ছিল। উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবাদ প্রসারে স্থানীয় জাতগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে।
আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বংশপরম্পরায় চলে আসা আবাদ পদ্ধতি বদলে গেছে। সম্প্রসারিত হয়েছে সেচাধীন ফসল আবাদি এলাকা। আধুনিক জাতের ফসল আবাদে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে সেচপানির চাহিদা। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমানে মোট ফসলি জমির প্রায় অর্ধেকাংশে কমবেশি সেচের প্রয়োজন হয়। ফসল আবাদে বর্ষা মৌসুমের আগে ও পরে সম্পূরক সেচের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে মোট ফসলি জমির এক-তৃতীয়াংশের ওপর পুরোপুরি সেচ নির্ভরশীল। এ মৌসুমে সেচ পানির প্রধান উৎস ভূ-গর্ভস্থ আধার। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ডিভিশন ধান উৎপাদনে সেচপানির চাহিদা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে থাকে। স্থানীয় এক পত্রিকায় এই ডিভিশনের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী বৃষ্টিপাত অপর্যাপ্ত হলে আমাদের দেশে এক কেজি ধান উৎপাদনে গড়পড়তা ১ হাজার ৪০০ লিটার পানি সেচের প্রয়োজন হয়। তবে এলাকাভেদে সেচপানির এ চাহিদা এক হাজার লিটারের কাছাকাছি থেকে আড়াই হাজার লিটার ছাড়িয়ে যায়। দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে গড়পড়তা ১ হাজার ৬০০ লিটারের ওপর পানি সেচের প্রয়োজন হয়। পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে শুষ্ক মৌসুমে প্রতি কেজি বোরো ধান উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সেচপানির পরিমাণ উঁচু জমিতে মোটামুটি পাঁচ থেকে সাড়ে ছয়শ মিলিমিটার এবং নিচু জমিতে চার-পাঁচশ মিলিমিটার। অন্যান্য ফসল উৎপাদনে এ সেচের পরিমাণ দু-তিনশ মিলিমিটার। এ হিসাবে এক কেজি ধান উৎপাদনে গড়ে এক হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হতে পারে। অন্যান্য ফসলে এর প্রায় অর্ধেক। জমির অবস্থান, মাটির বৈশিষ্ট্য, বৃষ্টিপাতের হার, আবাদকাল, জলবায়ু, আবহাওয়া, ফসলের জাত ইত্যাদির ভিত্তিতে পানির চাহিদায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যাবে।
পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপে দেশে মাথাপিছু প্রতিদিন খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ গড়পড়তা ৯৭৫ গ্রাম। এর মধ্যে চাল, অন্যান্য উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত খাদ্যের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮, ৪৪ ও ১৮ শতাংশ। এ হিসাবে আমাদের শুধু ভাত খেতে ধান উৎপাদনে পানির চাহিদা মাথাপিছু গড়ে দৈনিক ৫০০ লিটারের ওপরে। অন্যান্য ফসল আবাদ, মৎস্য চাষ ও গবাদি পশু পালনে পানির চাহিদা বাড়ছে। পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিবেদনে ২০২৫ সালে গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, শিল্প ও কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য পানির প্রাক্কলিত চাহিদা দৈনিক মাথাপিছু গড়পড়তা ১ হাজার ৪৬১ লিটার উল্লেখ করা হয়েছে। এ পানির উৎস বৃষ্টিপাত, ভূ-উপরিস্থ জলাশয়ও ভূ-গর্ভস্থ আধার। অধিকতর খাদ্য চাহিদা, শিল্প ও কলকারখানার প্রসার এবং জনসংখ্যা বর্ধনে পানির চাহিদা আরো বাড়বে। পাশাপাশি শিল্প-কারখানা, হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খামার থেকে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্য, ফসলের জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক নিঃসরণ এবং গার্হস্থ্য বর্জ্যে ভূ-উপরিস্থ জলাশয় দূষণ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মানের অবনতির আশঙ্কা রয়েছে।
ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সমন্বয়ে বাংলাদেশের পানিসম্পদ। এ সম্পদের মূল উৎস বৃষ্টিপাত ও বহির্দেশ থেকে উৎসারিত নদ-নদীর প্রবহমান পানি। এর অধিকাংশই বিভিন্ন খাল ও নদ-নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় বঙ্গোপসাগর অভিমুখে। অবশিষ্ট অংশ ভূ-উপরিস্থ প্লাবনভূমি, জলাশয় ও নদ-নদীর মোহনা এবং ভূ-গর্ভস্থ আধারে জমা হয়। কিছু আবার বাষ্প আকারে বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। দেশব্যাপী বার্ষিক বৃষ্টিপাতে বেশ তারতম্য রয়েছে। সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। সবচেয়ে কম হয় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। বিগত দশকে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের রাজশাহী স্টেশনে ২০১৮ সালে এক হাজার মিলিমিটারের কাছাকাছি এবং সিলেট স্টেশনে ২০১৭ সালে প্রায় ছয় হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল। বেশির ভাগ বৃষ্টিপাত হয় জ্যৈষ্ঠ বা মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র বা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে। অন্যান্য মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম বা একেবারেই হয় না। বর্ষা মৌসুমের আগে ও শেষে ফসলের জমিতে খরার সম্ভাবনা থাকে। শুষ্ক মৌসুমে খরা প্রকট হয়ে ওঠে। এ সময় নদ-নদীতে পানি কমে আসে। অধিকাংশ খাল, বিল, প্লাবনভূমি ও পুকুর শুকিয়ে যায়।
দেশের প্রায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলা দিয়ে বড়, মাঝারি বা ছোট নদ-নদী প্রবাহিত। এসব নদ-নদীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে অসংখ্য খাল। নদ-নদীর পানি খালে প্রবাহিত হয়ে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে আবাদি জমি নিমজ্জিত করে প্লাবনভূমি ও বিলে জমা হয়। এসব জলাশয় বিস্তৃত এলাকার পরিমাণ প্রায় দেশের মোট এলাকার এক-তৃতীয়াংশের নিচে। এর অধিকাংশ হলো নদ-নদী ও এগুলোর মোহনা, খাল, বিল, হাওর, লেক বা হ্রদ এবং প্লাবিত ভূমিসহ উন্মুক্ত জলাশয়। এছাড়া পুকুর, ডোবা, বাঁওড় ও উপকূলীয় নিচু এলাকাসহ বদ্ধ জলাশয়েও পানি জমা হয়। উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্রতীর থেকে দূরবর্তী এলাকার জলাশয়ে বৃষ্টিপাত থেকে সংরক্ষিত পানি মিষ্টি থাকে। এ পানি গৃহস্থালি কাজ, ফসল সেচ ও মৎস্য খামারে ব্যবহার করা যায়। উপকূলীয় অঞ্চল নদ-নদী ও খালে প্রবাহিত পানি এমনকি ভূ-গর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়। কোথাও কোথাও গভীর ভূ-গর্ভস্থ আধার থেকে টিউবওয়েলের সাহায্যে মিষ্টি পানি উত্তোলন করা যায়। এসব আধারের সঙ্গে স্থলভাগের মিষ্টি পানিসমৃদ্ধ নদ-নদীর সংযোগ থাকে। তবে অতিরিক্ত উত্তোলনে উপরিস্তর থেকে লবণাক্ত পানি শোষিত হয়ে সম্পূর্ণ আধার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বিভিন্ন স্তরে ও গভীরতায় বিস্তৃত ভূ-গর্ভস্থ আধার থেকে পানি উত্তোলনের জন্য অগভীর ও গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। বৃষ্টিপাত, নদ-নদী ও খালে প্রবহমান এবং দূরবর্তী মিষ্টি পানির উৎস থেকে ভূ-গর্ভস্থ আধার পুনর্ভরণ হয়। বর্ষা মৌসুমে যখন নদ-নদীতে পানির প্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি থাকে তখন বেশির ভাগ ভূ-গর্ভস্থ আধারে পুনর্ভরণ সম্পন্ন হয়। কয়েকটি কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক সময় ওঠানামা করে। যেমন গভীর আধার থেকে পানি উত্তোলন, বৃষ্টিপাত থেকে গভীর আধার পুনর্ভরণের মাত্রা এবং পার্শ্ববর্তী নদ-নদী ও খালের পানির গভীরতা, পরিমাণ বা সমতল, অন্তঃপ্রবাহ ও পার্শ্বিক নিষ্কাশন। মাটির উপরিস্তরে সবসময় পার্শ্ববর্তী নদ-নদী থেকে বা নদ-নদীর দিকে পানি প্রবাহ থাকে। নদ-নদী থেকে এ পানি প্রবাহ কমে গেলে এবং তুলনামূলকভাবে পার্শ্বিক নিষ্কাশন বৃদ্ধি পেলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। আবার নদ-নদীতে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি পায়। নদ-নদী ও খালের প্রবাহ থেকে সম্ভাব্য পানি প্রাপ্যতা ও খরার ঝুঁকি বোঝা যায়।
আগামীতে তিন ধরনের খরার ঝুঁকি আসতে পারে। বৃষ্টিপাতের অভাবে বা স্বল্পতায় মেট্রোলজিক্যাল খরা, নদ-নদী ও ভূ-গর্ভস্থ আধারে পানির অভাবে হাইড্রোলজিক্যাল খরা এবং মাটিতে পানির অভাবে এগ্রিকালচারাল খরা। নদ-নদী ও খালে নিম্ন প্রবাহ, প্লাবনভূমি ও জলাশয় সংকোচন এবং পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ ঘাটতির ফলে সব ধরনের খরার ঝুঁকি মাঝারি থেকে তীব্র হতে পারে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনে খরার প্রকোপ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেচ ও অন্যান্য চাহিদা পূরণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ঊর্ধ্বমুখী চাহিদার সঙ্গে সরবরাহ কমে গেলে সংকট অধিকতর প্রকট হয়ে উঠতে পারে। এসব থেকে পরিত্রাণে পুকুর, নদ-নদী ও খালসহ সব প্রবহমান জলাধার ও জলাশয়ে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং শুষ্ক মৌসুমে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির জন্য খনন বা পুনর্খনন, পুনরুদ্ধার ও তীর ভাঙন রোধে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যারেজ ও রাবার ড্যাম নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থার সংস্কার, গৃহস্থালি পানি সরবরাহ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং পানি অপচয় ও দূষণ রোধ পানিসম্পদ সংরক্ষণে সহায়ক হবে। এসব কার্যক্রমে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা অংশীজনদের সম্পৃক্ততা পানি সংকট মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। জলাভূমি ও জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণে ও পানিসম্পদ সংরক্ষণে সমবেত উদ্যোগ ফলপ্রসূ হবে। মাঠপর্যায়ে সেচপানি ব্যবস্থাপনা, ফসলবিন্যাসে খরাসহিষ্ণু ও স্বল্প সেচে আবাদযোগ্য জাত অন্তর্ভুক্তি, সেচাধীন এলাকায় আবাদে মাটির পানির ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন, বৃষ্টিরপানি সংরক্ষণ, সেচে যথাসম্ভব ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার, সঠিক পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ এবং পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও অপচয় রোধ সহজ হবে। এসব কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাল্টি-সেক্টরাল উদ্যোগ আবশ্যক।
ড. কিউ আর ইসলাম: গবেষক







