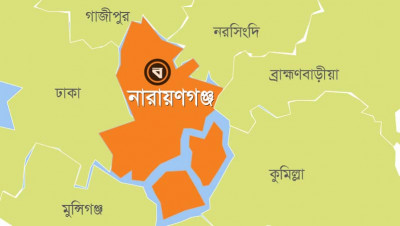রাজধানীর মাতুয়াইল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে সাইফ হাসান। প্রতিদিন সকালে চাকরিজীবী মায়ের হাঁকডাকে ঘুম ভাঙে তার। বিছানা থেকে জোর করে টেনে তুলে স্কুলের জন্য প্রস্তুত করাটা মা-ছেলের নিত্যদিনের রুটিন ওয়ার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো মতে সামান্য নাশতা মুখে দিয়ে স্কুলে ছুটতে হয় সাইফকে। এরপর কংক্রিটের শহরে গাঁ-ঘেষে গড়ে ওঠা সুউচ্চ ভবনের আঁটসাঁট ক্লাসরুমে নিয়মতান্ত্রিক কঠোর পড়াশোনা। দিনের পর দিন স্কুল ভ্যানের জন্য দৌড়, ক্লাস, সাপ্তাহিক টেস্ট, আর্ট, টার্ম আর ফাইনাল পরীক্ষা নামের গণ্ডিতে বড় হচ্ছে সে। ক্লাসের মাঝখানে কিছু সময়ের বিরতি থাকলেও ওই ইনডোর গেমস সাইফকে টানে না। সে চুপচাপ ক্লাসে বসে থাকে। পরীক্ষায় কম মার্কস বা খারাপ করলে অভিভাবককে তলব করে স্কুল, এ আতঙ্ক নিয়েই বাসায় ফেরে সাইফ। ফেরার পর গোসল-খাওয়াটা কোনোমতে শেষ করেই হাতে নেয় মায়ের সেলফোন। সন্ধ্যার টিউটর আসার আগ পর্যন্ত এভাবেই চলে। মোবাইল গেমস, কার্টুন, ফেসবুকেই মগ্ন হয়ে পড়ে সে। ঘণ্টাখানেক টিউটরের কাছে বসে পড়া শেষ করেই আবার টিভি রিমোট নেয় হাতে। টিউটরের রাগারাগি, মায়ের চিৎকার-বকাবকি শুনতে শুনতে এখন আর এসব খারাপ লাগে না সাইফের। জোর করে বসতে হয় পড়ার টেবিলে। রাত ১০টা-১১টা বাজতেই পরের দিনের প্রস্তুতি শুরু করতে হয় মা-ছেলের। সাইফের মতো লক্ষাধিক নগর শিশুর বেড়ে ওঠার প্রতিদিনকার চিত্রটা এমনই। বছরের পর বছর ধরে গৎবাঁধা, সাধহীন, যান্ত্রিক জীবন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে।
ফ্লাশব্যাকে এবার একটু পেছনে ফেরা যাক। নব্বইয়ের দশক। গ্রামীণ পরিবেশ। ঘরে নেই টিভি, নেই কোনো সেলফোন বা ডিজিটাল ডিভাইস। বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব তিন-চার কিলোমিটার। যেতে হবে হেঁটে। অবশ্য কারো কারো রয়েছে সর্বোচ্চ যোগাযোগ বাহন বাইসাইকেল। সকালে লাল আটায় বানানো মোটা রুটি বা ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে স্কুলের উদ্দেশে দে-দৌড় অবস্থা। দেরি হলে কান ধরে শিক্ষক বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দেবে—এ ভয়। শীত, বর্ষা, তীব্র দাবদাহে কিংবা দুর্যোগেও এ স্কুলযাত্রা বন্ধ নেই। দুইটা ক্লাস শেষ হতেই ক্রিকেটের ব্যাটবল, ফুটবল হাতে ছেলেরা নেমে পড়েছে মাঠে, অন্যদিকে মেয়েরা ব্যস্ত বৌচি, গোল্লাছুট বা ক্লাসরুমে টেবিলের ওপর কলম খেলায়। ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেটির মনও তখন পড়াশোনায় বসত না। নব্বইয়ের দশকে ছেলে-মেয়েদের জনপ্রিয় খেলার মধ্যে আরো ছিল দাঁড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি, গোশত চুরি, কুতকুত, হাঁড়িভাঙা, ইচিংবিচিং, ওপেন টু বায়োস্কোপ, কড়ি খেলা, কানামাছি, লাঠি খেলা, বউ-ছি, রুমাল চুরি, পুতুল বৌ, ফুল টোক্কা, মার্বেল, মোরগ লড়াই, লাটিম, লুডু, ষোল গুটি, এক্কাদোক্কা, চেয়ার সিটিংসহ বিভিন্ন ধরনের খেলা।
ক্লাস শুরু হতেই আবার সবাই সিরিয়াস। পড়া না হলে শিক্ষকের বেতের বাড়ি; ফেল করলে শিক্ষক-অভিভাবকের বকুনি, পরীক্ষায় ভালো করলে পুরস্কার—এসব ছিল রোজকার দিনলিপি। স্কুল ফাঁকি দেয়াটা ছিল নব্বইয়ের দশকের সবচেয়ে মজার কালো অধ্যায়, কারণ স্কুল পালিয়ে বাড়ি ফেরার পর শাস্তি, আবার পরদিন স্কুলে গেলেও শাস্তি। তবে স্কুল শেষে ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি ফিরতে হবে—এমন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। স্কুলে আসা-যাওয়ার বেলায় ঘটত আরো মজার ঘটনা। দেখা গেছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে স্কুল থেকে ফেরার পথে অন্যের বাগানের পাকা আম-কাঁঠাল দেখে অনুমতি না নিয়ে পেড়ে খাওয়ার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ মিশে থাকত। কোনো সহপাঠী অসুস্থ হলে দলবেঁধে সবাই চলে যেত তার বাড়ি। তখনকার দিনে আড্ডায় ক্লাসের বিষয়ভিত্তিক সমস্যা নিয়ে আলাপ, নবীনবরণ বিদায় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, এলাকার দুর্যোগ বা দুর্ভোগে মানুষের বিপদে কীভাবে পাশে দাঁড়ানো যায় সেসব বিষয় নিয়ে বন্ধুরা মিলিত হতো।
সন্ধ্যায় টিউটর নামের বাড়তি কোনো চাপ দেয়া হতো না শিক্ষার্থীর ঘাড়ে। নব্বইয়ের দশকে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। জীবনদর্শনের মূল হাতে খড়িই দিতেন শিক্ষকরা। আর শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাভরে তা মাথায় তুলে রাখত। বর্তমান সময়ের তুলনায় সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর নিতেন। স্কুলের ডানপিটে যে ছেলেটা সবচেয়ে রাগী শিক্ষকের ভয়ে কাঁপতেন, আবার প্রয়োজনের সময় ওই শিক্ষকই তার খোঁজ আগে নিতেন। শ্রদ্ধা আর সম্পর্ক কতটা নিবিড় হতে পারে, তার সবশেষ উদাহরণ হয়তো নব্বইয়ের দশক একান্তই যত্নে তুলে রেখেছে।
গত ২০-২৫ বছরের মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এবং পরিবেশ ও অবকাঠামোয় যে আমূল পরিবর্তন এসেছে, তার প্রভাবে প্রধান যে জায়গায় বেশি ক্ষতি হয়েছে সেটি হলো শিক্ষায় আনন্দের বিলুপ্তি। সমকালীন নগরায়ণ ও তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন জীবন সহজ করে দিয়েছে সত্য, কিন্তু আনন্দ হয়েছে উধাও। বেড়ে ওঠার হিসাব করেছে জটিল। দুই দশক আগের শিক্ষাজীবন ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। তখন মোবাইল, টেলিভিশন সহজলভ্য না থাকায় বইয়ের প্রতি বিপুল আবেদন ছিল শিক্ষার্থীদের। চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিংকী, টিনটিন আর আর্চির কথার মতো কমিকস সিরিজ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তৎকালীন ঢাকায়। পাঠ্যবইয়ের ভেতর লুকিয়ে তিন গোয়েন্দা পড়ে মায়ের হাতে মার খাওয়ার মতো সেসব মজার স্মৃতি এখন অনেকটা গল্পের মতোই। দলবেঁধে প্রতিবেশীর বাগান থেকে ফুল চুরি করে একুশের প্রভাত ফেরিতে সমবেত হওয়া, স্বাধীনতা দিবসের প্রতিযোগিতায় বন্ধুরা মিলে অংশ নিয়ে পুরস্কার জেতার আনন্দ, স্কুলমাঠে বসা পহেলা বৈশাখের মেলায় যে নির্মল আনন্দ মিশে থাকত, তা আজকের নগরজীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনকি অধিকাংশ গ্রামেও সে পরিবেশ এখন আর দেখা যায় না।
বর্তমান ও নব্বইয়ের দশকের মধ্যে যে বিবর্তন ও বিচিত্রতা উঠে এসেছে, তা আমাদের একদিনের খেসারতের ফল নয়। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দেশে সেলফোনের নেটওয়ার্ক শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কিছুদিন পর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হলে তা চট্টগ্রামে পৌঁছায়। ১৯৯৬ সালে সেলফোন সেবা বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে তিন প্রতিষ্ঠান—গ্রামীণফোন, একটেল এবং সেবাকে লাইসেন্স দেয়া হয়। দ্রুত এটি রাজধানী ছাড়িয়ে সারা দেশে পৌঁছতে থাকে। এরপর এ নেটওয়ার্ক থামেনি। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সবশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দেশে সেলফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮ কোটি ছাড়িয়েছে। একই সময়ে ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৫০ লাখের বেশি। ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা যেমন ব্যাপক আকারে বেড়েছে, তেমনি বিভিন্ন কোম্পানির স্মার্টফোন, ট্যাব, নোটবুক, ল্যাপটপসহ আনুষঙ্গিক ডিভাইসে দেশ আজ পরিপূর্ণ। এর প্রভাব যেমন নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত পৌঁছেছে, তেমনি এ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না বর্তমান শিশু ও কিশোর প্রজন্ম। শিক্ষার্থীদের মাঝে এ আসক্তি দিনকে দিন বেড়ে চলেছেই। নগর উন্নয়নের কবলে পড়ে বাচ্চাদের খেলার মাঠগুলো ভবনে রূপ নিয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আকৃতি যেমন ছোট থেকে ছোটতর হচ্ছে, পাশাপাশি ডিজিটাল ডিভাইসের আগ্রাসনে আজকের শিশু ঘরকুনো প্রজন্ম হিসেবে বেড়ে উঠছে। শিক্ষার আনন্দ তো হারিয়েছেই, এর সঙ্গে চার দেয়ালের গণ্ডিতে থাকা এসব শিশু-কিশোর স্থূলকায়, উচ্চরক্তচাপ, চোখ ও মস্তিষ্কে সমস্যা, নিদ্রাহীনতা, একাকিত্বে ভোগার মতো সমস্যায় ভুগছে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের মানসিক বিকাশও।
শিশুদের হাতে ডিজিটাল ডিভাইস তুলে দেয়ার ফলটা ভবিষ্যতের জন্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে, এ বিষয়ে সম্প্রতি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘মিশিগান মেডিসিন স্টাডি’-এর একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটি ‘জেএএমএ পেডিয়াট্রিকস’ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রকাশিত ‘জেএএমএ পেডিয়াট্রিকস’ হলো শিশুবিষয়ক মাসিক জার্নাল। গবেষণা দলের প্রধান জেনি রাডেস্কি। যিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘মট চিলড্রেনস হসপিটাল’-এর হেলথ সিএস (ক্যাবিনেট সেক্রেটারি) এবং উন্নয়নমূলক আচরণগত শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন। এ গবেষক বলেন, ‘সাময়িক সময়ের জন্য শান্ত রাখতে শিশুর হাতে সেলফোন তুলে দেয়ার ফলে মনে হতে পারে এতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ঘরের কাজ করতে গিয়ে মানসিক চাপ সামাল দিতে এ পন্থা অবলম্বন করেন অভিভাবক। যদি এ অভ্যাস কৌশল নিয়মিত চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর পরিণতি খুব খারাপ হবে।’ জেনি রাডেস্কি আরো বলেন, ‘বিশেষ করে ছেলেশিশুর শৈশবের শুরুতে এসব ডিভাইস তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্নয়ন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের বিকল্প পদ্ধতির সুযোগগুলোকে বিচ্যুত করে ফেলতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিতই বটে।’
নাগরিক হিসেবে রাজধানীর আজকের শিশুরা কতটা অবহেলিত, তা একবার নতুন করে হিসাব কষা দরকার। গত বছরের ২৩ আগস্ট ঢাকা মহানগরীর জন্য প্রণীত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনার (ড্যাপ) উপঅঞ্চলভিত্তিক নাগরিক সুবিধায় বলা হয়েছে, ঢাকার প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলার মাঠসহ জায়গা হতে হবে ন্যূনতম এক একর। ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য একটি ফুটবল খেলার মাঠসহ কলেজ আবশ্যক। সে সঙ্গে মানদণ্ড অনুসারে প্রতি ১২ হাজার ৫০০ মানুষের জন্য এক একর জমি পার্কের জন্য এবং দুই একর জমি খেলার মাঠের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অথচ ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে ওয়ার্ড রয়েছে ১২৯টি, এর মধ্যে ৪১টিতে কোনো খেলার মাঠই নেই। দুই সিটির আয়তন ৩০৫ দশমিক ৪৭ বর্গকিলোমিটার। সে হিসাবে মাঠ দরকার অন্তত ৬১০টি, কিন্তু আছে মাত্র ২৫৬টি। অথচ নগর উন্নয়নে প্রতিনিয়ত হচ্ছে ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, বিশাল বিশাল বাণিজ্যিক ভবন ও ইমারতসহ অবকাঠামোর হাজারটা উন্নয়ন। অথচ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মানসিক উন্নয়ন ও তাদের প্রতি দায়বদ্ধতায় যে বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে কারো যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। নগরকেন্দ্রিক জাঁতাকলে পিষে থাকা বর্তমান প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশে দরকার দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর পরিকল্পনা। না হলে আনন্দ থেকে বঞ্চিত এ প্রজন্মের কাছে আমরা কৈফিয়ত দেব কী...
আনিসুর সুমন: সাংবাদিক