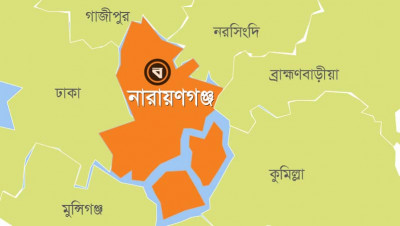ঐতিহাসিকভাবে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ
ও ১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ
রদ—দুটো
ঘটনার বড় ধরনের ভূমিকা
আছে। কলকাতার
চেয়েও ঢাকা
অনেক পুরনো
শহর। কলকাতা
ইস্ট ইন্ডিয়া
কোম্পানির তৈরি।
আর মোগল
আমলের আঞ্চলিক
কেন্দ্র হিসেবে
ঢাকা গড়ে
ওঠে। বস্ত্রসহ
অন্যান্য শিল্প
নিয়ে ঢাকার
শিল্পের বিকাশ।
অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরে ব্রিটিশ সরকার তাদের কাপড়ের বাজার নিশ্চিত করতে এ দেশীয় বস্ত্রশিল্পের ওপর খড়গহস্ত হয়। এ শিল্পের বিনাশের মধ্য দিয়ে ক্রমশ ঢাকার গুরুত্ব কমতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলার পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বও কমে যায়। বিপরীতে উত্থান হতে থাকে কলকাতার। কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়। কলকাতার বিকাশ হতে থাকে, রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্ব বাড়তে থাকে, ঢাকার গুরুত্ব একদম কমে যায়।
পূর্ববঙ্গকে দেখা হতো কৃষিকাজের ভূমি, পশ্চাৎপদ এলাকা হিসেবে। বঙ্কিমচন্দ্র, তারও পরে নীরদ চৌধুরীসহ অনেকের কাছ থেকে এ রকম কথাই আমরা শুনেছি। পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার বাঙালিরাও পূর্ববঙ্গের মানুষদের এভাবে দেখত, বাঙাল পরিচয় তুচ্ছতাচ্ছিল্যের জন্য ব্যবহূত হতো। তবে পূর্ববঙ্গের যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চাইতেন, কলকাতাই ছিল তাদের প্রধান গন্তব্য। কারণ লেখাপড়া শেখা, লেখালেখি করা কিংবা ভালো কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হলে কলকাতায়ই যেতে হতো।
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে পূর্ব বাংলা, বিশেষত ঢাকার প্রভাবশালী অধিবাসীদের প্রবল আগ্রহ ছিল। এমনটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে ঢাকাকে ঘিরে নতুন করে উদ্দীপনা তৈরি হবে এবং তা হয়ও। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা তৎপরতা দেখা যায়। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রবল প্রতিরোধ হওয়ার ফলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। বঙ্গভঙ্গ হওয়া ও রদ হওয়া—দুই ঘটনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক নানা বিষয় দানা বাঁধতে শুরু করে। কারণ বঙ্গভঙ্গের নেপথ্যে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের এবং বঙ্গভঙ্গ রদের পেছনে কলকাতার হিন্দুদের ভূমিকা ছিল—এভাবেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়। যদিও বিষয়টি পুরোপুরি সঠিক নয়। পূর্ব বাংলার অনেক অমুসলিমও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিল আবার কলকাতার অনেক মুসলিমও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে। তার পরও বিষয়গুলো সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়।
তবে রাজনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে ঢাকার কিছু ভিন্ন চিত্র আমরা বিশ শতকের শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাই। যেমন জ্ঞান চক্রবর্তী ঢাকার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বইতে লিখেছেন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনকে ‘সন্ত্রাসবাদী’ তকমা দেয়া হয়েছিল, সেই আন্দোলনে ঢাকার তরুণদের অনেকগুলো গ্রুপ খুব সক্রিয় ছিল। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সবাই ছিল। তাদের মধ্যে থেকেই একটা বড় অংশ পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হয়। এরপর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু জায়গায় তেভাগা আন্দোলন বিস্তৃত হয়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের উত্তরাঞ্চলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেটা আর সামনে এগোতে পারেনি। একটা পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই সামনে চলে আসে।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলায়
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।
১৯৪৭ সালে
ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বাংলা ভাগ
হয়। যারা
প্রথম দফায়
বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা
করেছিল, তাদের
একটা বড় অংশ, বিশেষত
উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের একটা বড় অংশ এ সময়ে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে দাঁড়ায় শক্তভাবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলেও ১৯৪৭
সালে তারাই
বঙ্গভঙ্গের প্রধান
দাবিদার ছিল।
শরৎ বসু,
আবুল হাশিম,
হোসেন শহীদ
সোহরাওয়ার্দী সবাই
চেষ্টা করছিলেন
অখণ্ড বাংলার।
কিন্তু মুসলিম
এলিট ও হিন্দু এলিটদের
পক্ষ থেকে
এর বিরোধিতা
আসে। শেষ
পর্যন্ত বাংলা
ভাগ হয়ে
পূর্ব বাংলা
তৈরি হয় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসেবে। এভাবেই বর্তমান
বাংলাদেশের পূর্বসূরি হিসেবে পূর্ব বাংলার
উদ্ভব।
পূর্ব
বাংলার বাসিন্দাদের যারা রাজনীতির সঙ্গে
যুক্ত হয়েছেন,
তাদের অধিকাংশের
এ সংযোগ
ঘটে কলকাতায়
গিয়েই। তাদের
কেউ ঢাকা
থেকে যাননি,
গেছেন মফস্বল
বা পূর্ব
বাংলার বিভিন্ন
অঞ্চল থেকে।
কেউ গোপালগঞ্জ
থেকে, কেউ বরিশাল কিংবা
কেউ টাঙ্গাইল
বা সিরাজগঞ্জ
থেকে সেখানে
গেছেন। বাংলা
ভাগ হলে, ১৯৪৭ সালের
পরে, সবাই
ঢাকায় চলে এসেছেন। মূলত
ভাষা আন্দোলনের
মাধ্যমে ঢাকার
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বটা
বাড়তে থাকে।
১৯৪৮ সালের
পর শুরু
হওয়া ভাষা
আন্দোলনকে ঘিরে
পূর্ব বাংলার
রাজধানী হিসেবে
এবং নতুন
পর্বের রাজনীতির
কেন্দ্র হিসেবে
ঢাকার উত্থান
হয়।
এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। তখন পূর্ব বাংলায় যারা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, উচ্চ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ভারত-পাকিস্তান ভাগের পর, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে, যাদের একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে চলে যান। হঠাৎ করে তাদের এ দেশত্যাগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শূন্যতা তৈরি করে। তুলনামূলকভাবে তরুণ কিংবা পেশাগতভাবে কম অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পূর্ব বাংলার নেতৃত্বে আসে। বলা যায় যে গোটা পূর্ব বাংলা নবীনদের হাতে চলে আসে।
রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রশাসন সব জায়গায় তখন নবীনদের পদচারণা। শিক্ষকদের জায়গা খালি, অনেক নতুন শিক্ষক তৈরি হয়। প্রশাসনের জায়গা খালি, নতুন কর্মকর্তা দায়িত্ব নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রবীণ শিক্ষক কলকাতায় চলে যান, সেখানে তরুণ শিক্ষকরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এত এত চাহিদার জোগান দেয়া ঢাকা শহরের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিভিন্ন মফস্বল অঞ্চল থেকে আসা নবীনরা। শিক্ষাক্ষেত্রেও ঢাকা কেন্দ্রে চলে আসে। যারা লেখাপড়া করতে চান, তারা ঢাকায় এসে লেখাপড়ার সুযোগ নেন। যারা সরকারি প্রশাসনে যোগ দিতে চান, তাদেরও সে সুযোগ তৈরি হয়। বলা যায়, বাঙালি নব্য বিশেষত মুসলিম মধ্যবিত্তের জন্য একটা নতুন যাত্রা শুরু হয়।
যেমন তাজউদ্দীন আহমদ কাপাসিয়া থেকে এসেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে উঠেছেন। তাকে শহরের কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেতে হয়নি। তখন মফস্বল থেকে যারা এসেছেন তারাই প্রধান। মফস্বল থেকে যারা এসেছেন, তাদের হাতেই রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারাই ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তখন রাজনৈতিক সংগঠনও নতুন করে তৈরি হচ্ছিল—মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ, এরপর আওয়ামী লীগ। যার সভাপতি মওলানা ভাসানী আর সেক্রেটারি শামসুল হক। তারা একে তো এলিটই না আবার ঢাকা শহরে তাদের ভিত না। শেখ মুজিবুর রহমান তখন ছাত্রনেতা হিসেবে খুবই সম্ভাবনাময়, সক্রিয় ও পরিশ্রমী, দ্রুত রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠছেন। ঢাকা শহরে তার যোগাযোগটা কম ছিল। তার যোগাযোগ ছিল গোপালগঞ্জ থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যে তাকে দিল্লি পর্যন্ত যেতে হতো।
পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক বিকাশ শুরু হয়। সে সময় ঢাকার আদি বাসিন্দা, নেতৃত্বের যোগ্য পরিবার খুব বেশি ছিল না। আহসান মঞ্জিলের নবাব পরিবারের বাইরে যারা তাদের সংখ্যাও খুব বেশি ছিল না। জমিদার পরিবারগুলো আগে থেকেই কলকাতায় চলে যায়।
ঢাকা যদি আগে থেকেই কলকাতার মতো গতিশীল শহর থাকত, তাহলে মফস্বলের নেতাদের এসে প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হতো। তা হয়নি। সে সময় ঢাকা ও মফস্বলের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। সড়ক, অবকাঠামো বা সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম কিংবা খুলনা কোনো অংশে কম ছিল না। খুলনা ও যশোরের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগটা আগে থেকেই ভালো ছিল। ফলে মফস্বল থেকে যারা ঢাকায় আসে, তারা খুব একটা দূরত্ববোধ করত না। পূর্ববঙ্গের নতুন যাত্রা শুরু হয়, যেখানে মফস্বল ও রাজধানীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো তফাৎ নেই। বরং মফস্বলই তখন ঢাকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে। রাজধানীকে নতুনভাবে দাঁড় করানো বা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে ভাষা দিতে মফস্বলের অধিবাসীরাই প্রধান ভূমিকা রাখে। কথাবার্তার ধরনকেও প্রভাবিত করল ঢাকার বাইরে থেকে আসা মফস্বলের বাসিন্দারা। পূর্ব বাংলার বক্তৃতার ধরন, লেখালেখির ধরন, স্লোগানের মধ্যকার পার্থক্যগুলো মূলত সে সময়েই এসেছে।
পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় শিল্প-কারখানা ছিল কম। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে প্রধান তিনটি সমুদ্রবন্দর ঘিরে শিল্পায়ন হয়েছিল। আগের শিল্প ধ্বংস হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় এ আমলে আর শিল্পায়ন হয়নি, তবে এখানে পাটের বিস্তৃত ফলন থাকার কারণে একে ঘিরে বড় ব্যবসা তৈরি হয়েছিল। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো, পূর্ব বাংলার নতুন শিক্ষিত শ্রেণী পাট চাষ ও ব্যবসার সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে তাই পাট, পাট চাষ ও পাটচাষী বড় ধরনের এজেন্ডা ছিল। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তের সন্তানদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার বিষয়গুলো পাটের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কারণ পাট ছিল অর্থকরী ফসল।
সে সময় কৃষকদের প্রধান অংশে ধান উৎপাদন করা হতো প্রধানত পরিবারের খাবারের জন্য, বিক্রির জন্য নয়। তাই যারা সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য গ্রামের বাইরে, বিশেষ করে ঢাকায় পাঠাতে চাইত, তাদের জন্য পাট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দরকার ছিল। যারা পাট বেশি চাষ করত তাদের জন্য এটা সহজ ছিল। পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠার সঙ্গে পাটের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্য পাটের প্রসঙ্গটা সবসময় আসে। আমরা ২১ দফা থেকে শুরু করে ষাট ও সত্তরের দশকের আন্দোলনগুলোয় পাটের বিষয়গুলো দেখতে পাই।
ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তান শ্মশান কেন—এ প্রশ্নটা জোরের সঙ্গে সে সময় তোলা হয়েছিল। এর পুরো বয়ানের একটি কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ ছিল পাট। সেই পাটচাষীদের প্রশ্ন রাজনীতির মধ্যে এসেছে। কারণ কৃষকই তখন প্রধান। পঞ্চাশের দশকে শুরু হলেও প্রধানত ষাটের দশকে পাটকে কেন্দ্র করে শিল্পায়ন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনসহ বেশ কয়েকটি সংস্থা তৈরি হয় সে সময়ে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরি হলেও তা পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতেই ছিল।
মওলানা
ভাসানী, আবুল
বাশার, দেবেন
শিকদার, অনিল
মুখার্জি, মণি
সিংহ, আবদুল
হক, মোহাম্মদ
তোহা—তারা
সবাই শ্রমিক
নেতা বা কৃষক নেতা
হিসেবে রাজনীতির
কেন্দ্রে এসেছেন।
ঢাকা শহরে
তারা বড় হননি। কিন্তু
ঢাকার সঙ্গে
তাদের যোগাযোগটা তৈরি হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর। তারা
রাজনৈতিক কাজের
সূত্রেই ঢাকায়
আসেন। ষাটের
দশকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মধ্য
দিয়ে শিল্প
শ্রমিকদের আয়তন
বাড়তে থাকে,
তাদের ঘিরে
যে শ্রমিক
আন্দোলন সংগঠন
হয়, সেখানে
ঢাকার বাইরের
মানুষই নেতৃত্ব
দিয়েছিলেন। মওলানা
ভাসানীর সঙ্গে
যারা কাজ
করতেন, তাদের
মধ্যে মোহম্মদ
তোহা ও আবদুল হক অন্যতম। তারা
মওলানা ভাসানীর
খুঁটি ছিলেন।
একজন শ্রমিক
সংগঠনের নেতা,
অন্যজন কৃষক
সংগঠনের।
নাগরিক, শিল্পকেন্দ্রিক রাজনীতির চেয়ে তখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কৃষকনির্ভর ও মফস্বল থেকে আসা নতুন মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব। আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্যা ও জনগণের দাবি ঢাকার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে যুক্ত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় বড় আকারে বন্যা হয়েছে। তখন বন্যা ছিল একটা বড় ইস্যু। ধানের ন্যায্যমূল্য এবং পাটও একটা বড় ইস্যু। ষাটের দশকের মাঝামাঝির পর থেকে শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল—কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকদের মৈত্রী। কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে মৈত্রী ও যোগসূত্র তখন অনিবার্য ছিল।
ব্রিটিশ আমল থেকে কৃষকদের কাছে পূজনীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন এ কে ফজলুল হক। তার গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রথমকালে শেখ মুজিব যখন তার সমালোচনা করছিলেন তখন তার বাবাই তা করতে তাকে নিষেধ করেছিলেন। এ দেশে মানুষের আস্থা অর্জন একবার করতে পারলে তাকে মানুষ সবসময়ই মাথায় তুলে রাখে। শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের মানুষের এই ভাব ভালোই বুঝতেন, সেজন্য তার বক্তৃতায় একবার বলেছিলেন যে বাংলাদেশের মানুষ এমন যে কেউ যদি তাদের জন্য হাঁটু পানি পর্যন্ত যায়, জনগণ তার জন্য গলা পানি পর্যন্ত যাবে। কিন্তু জনগণ যদি একবার টের পায় যে কেউ তাদের সঙ্গে বেইমানি করছে তাহলে তারা সারা জীবনের জন্য তাকে মুছে ফেলবে।
কৃষক তখন বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে থাকলেও তাদের পক্ষে কাজের কাজ হয়েছে খুবই কম। এখনো নদীভাঙন, ফসলের দাম, বেকারত্ব, শিক্ষা, চিকিৎসা সমস্যার মধ্যে হাবুডুবু খেতে হয় অধিকাংশকে। এ দশে মৌলিক রূপান্তর ছাড়াই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও শিল্প জাতীয়করণ হয়েছে। জমিদার ও শিল্প মালিক চলে যাওয়ার পর শূন্যতা তৈরি হয়, তা পূরণের জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু বড় কোনো সংস্কার করা হয়নি। ফলে এ ঘটনাগুলো মৌলিক পরিবর্তনের ধারা তৈরি করতে পারেনি। জমিদারি উচ্ছেদ হলো কিন্তু ভূমি সংস্কার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ন্যায্যমূল্য—এগুলো ঠিক হয়নি। ১৯৫৪ সালের ২১ দফার মধ্যেও কিন্তু এ দাবিগুলো ছিল।
১৯৫০-এর ভূমি সংস্কারে জমিদারি উচ্ছেদ হয়। এরপর নতুন জোতদারদের প্রভাব বেড়ে যায়। ১০০ বিঘা সিলিং করলেও কয়েক হাজার বিঘা জমির মালিক ছিল এসব প্রভাবশালী লোকেরা। এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে ভূমি সংস্কারের সময় কৃষকের সংজ্ঞা বদলানোর জন্য এ জোতদারদের পক্ষ থেকেই রাজনৈতিক চাপ আসে। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাকের বিবরণীতে বিষয়টির উল্লেখ আছে। তিনি বলছেন, আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। কারণ জোতদাররা অনেক শক্তিশালী। কৃষকদের সংজ্ঞা পাল্টে দেয়া হলে কৃষি সংস্কার আর অগ্রসর হতে পারেনি। বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে। কিন্তু ভূমিহীন কৃষক, মাঝারি কৃষক, গরিব কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আর হয়নি।
আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এ অঞ্চলের নতুন রাজনীতির বিন্যাসে মফস্বলের মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে রাজনীতিতে আসার মধ্য দিয়ে তথাকথিত আশরাফ মুসলমানদের আধিপত্য খর্ব করে তথাকথিত আতরাফ মুসলমানরা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইসলামের মধ্যে শাস্ত্রীয়ভাবে বর্ণপ্রথা নেই, তবে মুসলিম সমাজের মধ্যে নানাভাবে তা কাজ করে; আশরাফ ও আতরাফ বিষয়টি তার মধ্যে অন্যতম। জোতদার, অভিজাত ও পুরনো ধনীরা নিজেদের আশরাফ মুসলিম বলে দাবি করতেন, তারা আবার বাংলা ভাষায় কথা বলতেন না। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উচ্চবিত্ত হিন্দুদের। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মফস্বল থেকে আসা রাজনীতিবিদদের কারণে এ ক্ষমতার কেন্দ্র ভেঙে যায়, আতরাফ মুসলমানদের আধিপত্য তৈরি হয়। তারা মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশরাফ মুসলমানদের আধিপত্য ভেঙে ফেলে। এ তথাকথিত আতরাফ মুসলমানদের দুই প্রধান মুখপাত্র হচ্ছেন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। তখনকার সমাজে প্রধান নেতৃত্বে এ দুজনের প্রবেশ ছিল একটা বড় ধাক্কা। ঢাকার রাজনীতিতে তাদের প্রবল প্রবেশ আশরাফ মুসলমান, জোতদার বা অভিজাত পরিবার ছাড়া অন্যরা নেতৃত্ব দিতে পারবে না এমন বিশ্বাসের অচলায়তন ভেঙে দেয়।
পূর্ববঙ্গের আমলা ও উচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্ত এলিট মুসলিমরা রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের প্রবেশের বিষয়টাকে তাই তখন পছন্দ করেনি। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে এটা আরো বেশি ছিল। বিত্তবান ‘অভিজাত’, ‘আশরাফ’ মুসলমানরা তাকে লুঙ্গি পরা মওলানা ও কাফের মওলানা বলত। শেখ মুজিব সম্পর্কেও অনেক তুচ্ছতাচ্ছিল্য শুনেছি এ কারণেই।
মফস্বল ও মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবার থেকে নেতৃত্বের প্রভাব আমরা ভাষার মধ্যেও দেখতে পাই। মওলানা ভাসানীর ভাষণ বা শেখ মুজিবুর রহমানের কথার মধ্যে প্রমিত বাংলা বা উর্দুকেন্দ্রিক ভাষা নেই। পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষ যেভাবে কথা বলে, তারা যে যে অঞ্চল থেকে এসেছেন তারা সেভাবেই কথা বলতেন। তাদের সম্পর্ক ছিল মাটির সঙ্গে।
কিন্তু
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকার
ক্ষেত্রে মফস্বল
থেকে আসা
নতুন নেতৃত্বকেও শ্রেণীগত টানাপড়েনে পড়তে
হয়। যখন
তারা নেতা
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, তখন তারা
নতুন একটি
শ্রেণীর মধ্যে
যাচ্ছেন, সমাজের
উঠতি অন্যান্য
প্রভাবশালী শ্রেণীর
সঙ্গে নতুন
একটি বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের
যেতে হয়েছে।
তার পুরনো
সম্পর্ক, পুরনো
ক্ষমতার ভিতের
মধ্যেও পরিবর্তন
হয়েছে। নতুন
শ্রেণীর সঙ্গে
বোঝাপড়া করতে
হয়েছে। ফলে
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর উঠতি নব্য
ধনিক শ্রেণীর
সঙ্গে বোঝাপড়া
করায় তারা
আর কৃষক-শ্রমিকদের প্রত্যাশার পথ ধরে চলেননি।
বাংলাদেশে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকরাই প্রধান ভূমিকা পালন করলেও তারা সে স্বীকৃতিটা আজও পায়নি। তাদের যে দাবিগুলো ছিল তার কিছুই পূর্ণ হয়নি। বাংলাদেশ যখন নতুনভাবে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরও নতুন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। নতুন নতুন বিন্যাসের মধ্যে গিয়ে তারা শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। মফস্বল-গ্রাম থেকে আসা মেধাবী পরিশ্রমী ব্যক্তিরা যে কর্মসূচি, প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বে এসেছিলেন, তা থেকে অনেকেই অনেক দূরে সরে গেছেন, নতুন ক্ষমতার বৃত্তে তারা প্রবেশ করেছেন। এটিই নির্মম বাস্তবতা।
আনু মুহাম্মদ: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও সর্বজনকথার সম্পাদক