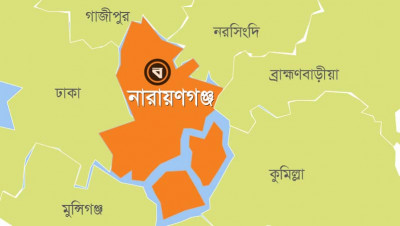১ নম্বর
হলের
(বর্তমান আল-বেরুনী
হল)
৪১৫
নম্বর
কক্ষে
ঢোকার
সময়ই
নিজ
উদ্যোগে
আব্দুর
রব
আমাকে
শিখিয়ে
দিল
কীভাবে
দুই
তালা
দিয়ে
ইন্টারলক
করতে
হয়।
তখন
ইন্টারলক
সম্পর্কে
আমার
কোনো
ধারণাই
ছিল
না।
এ
ব্যাপারে
আমার
মাথার
বুদ্ধি
ছিল
অনেকটাই
সেকেলে।
দরজায়
একটা
তালাই
লাগাব
এবং
দুজন
দুই
কপি
চাবি
এস্তেমাল
করব।
কিন্তু
সেটা
তো
সম্ভব
ছিল
না,
কারণ
দুজনের
কাছেই
একটা
করে
তালা
এবং
একটা
করে
চাবি।
এ
অবস্থায়
আব্দুর
রবের
বিকল্প
উপস্থিত
বুদ্ধি
যে
আমার
চেয়ে
ঢের
উন্নত
মানের
ছিল,
সেটা
ঠাহর
করতে
আমার
লেগে
গেছে
প্রায়
৫০টি
বছর।
তার
চেয়ে
আশ্চর্যজনক
ব্যাপার
হলো,
দুজন
একই
কক্ষে
পাঁচ
বছর
কাটালাম,
অথচ
একটা
দিনও
রুমমেটের
কাছে
জানতে
চাইলাম
না
সে
কোথায়
কার
কাছে
ইন্টারলকিংয়ের
কায়দাটা
রপ্ত
করেছিল।
অনেক
দিন
হলো,
আব্দুর
রবের
সঙ্গে
আমার
কোনো
কথা
হয়নি,
তবু
আশা
করি
আল্লাহর
অশেষ
কৃপায়
সে
সুস্থ
শরীরে
অবসরজীবন
উপভোগ
করছে।
তথাপি
তার
কাছ
থেকে
এ
রহস্যের
গিঁট
এখন
আমি
আর
খুলতেও
চাই
না।
ওই
না-জানাটাই
হোক
আব্দুর
রবের
সঙ্গে
আমার
বাকি
জীবনের
আত্মিক
বন্ধনের
অমূল্য
সূত্র!
জাহাঙ্গীরনগর
বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রথম
বর্ষের
শিক্ষা
কার্যক্রম
শুরু
হয়েছিল
১৯৭১
সালের
১২
জানুয়ারি।
প্রথম
ব্যাচে
চার
বিভাগে,
অর্থাৎ
অর্থনীতি,
ভূগোল,
গণিত
ও
পরিসংখ্যানে
ভর্তি
করা
হয়
খুব
বেশি
হলে
২০০—কেবলই
ছাত্র।
সেবার
কোনো
ছাত্রী
নেয়া
হয়নি।
দ্বিতীয়
ব্যাচে
সাত
বিভাগে
[ওই বছর
চালু
হয়েছিল
নতুন
আরো
তিনটি
বিভাগ—বাংলা,
প্রকৃতিবিজ্ঞান
(Physics) ও
রসায়নশাস্ত্র]
আমরা
ভর্তি
হলাম
আরো
প্রায়
৩৫০
জন।
তার
মধ্যে
ছাত্রী
ছিল
বড়জোর
২০
জন।
আমাদের
অর্থনীতি
বিভাগের
ভাগে
পড়েছিল
মাত্র
তিনজন।
সবচেয়ে
বেশি
মেয়ে
ছিল
বাংলা
বিভাগে
আর
সর্বনিম্ন
সংখ্যা
ছিল
অংকে।
ওই
বিভাগে
আমাদের
বন্ধু
সদা
হাসিমুখ
হামিদা
রহমান
ছিল
সবেধন
নীলমণি।
১৯৭২
সালে
গোটা
বিশ্ববিদ্যালয়ের
মোট
শিক্ষার্থী
ছিল
কমবেশি
৫৫০
এবং
শিক্ষক-শিক্ষিকা
ছিলেন
আনুমানিক
৪০-এর
কোটায়।
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের
সংখ্যা
হতে
পারে
সাকল্যে
আরো
২০০।
ক্লাসরুমের
সব
কয়টাই
ছিল
১
নম্বর
হলসংলগ্ন
বড়
একতলা
দালানটিতে।
এর
উত্তর
পাশে
ছোট
ছোট
একতলা
দুটো
ঘর
কেমেস্ট্রি
ও
ফিজিক্সের
জন্য
নতুন
বানানো
হয়েছিল।
সেখানে
ছিল
তাদের
ক্লাসরুম,
ল্যাব
ও
স্যারদের
অফিস।
মেয়েদের
জন্য
কোনো
আবাসিক
হল
ছিল
না।
তারা
থাকত
শিক্ষকদের
‘বি’ টাইপের
একটি
কি
দুটি
বাসায়।
ছাত্রদের
সবার
আবাসন
ছিল
১
নম্বর
হলের
চারতলা
মূল
ভবনে
এবং
এর
দক্ষিণ-পুব
কোণে
স্থাপিত
রাজারবাগ
পুলিশ
ব্যারাকের
মতন
লম্বা
লম্বা
তিনটি
ঘরে।
প্রান্তিক
গেটের
সোজা
পশ্চিম
বরাবর
রাস্তার
দুই
পাশে
ছিল
শিক্ষক
ও
অফিসারদের
থাকার
‘সি’ টাইপ
কোয়ার্টার
এবং
প্রান্তিক
গেট
থেকে
পুরনো
ক্যাম্পাসে
আসার
পথে
হাতের
বাঁ-দিকে
কাঁঠাল
গাছ
ঘেরা
ছিল
বিশ্ববিদ্যালয়
সমবায়
সমিতির
অফিস,
ন্যায্যমূল্যের
দোকানও
ইউওটিসির
কার্যালয়।
‘প্রান্তিক’ গেটে
ঢাকা-আরিচা
মহাসড়কের
ওপর
‘প্রান্তিক’ দোকান
বসেছে
বেশ
পরে।
আরেকটু
সামনে
গেলে
রাস্তার
একই
দিকে
ছিল
সিনিয়র
প্রফেসরদের
জন্য
দুই
অথবা
তিন
সারিতে
১০/১২টা
‘বি’ টাইপ
কোয়ার্টার।
পরে
কোনো
এক
সময়ে
ওই
‘বি’ টাইপ
কোয়ার্টারগুলোকে
‘এ’-তে
উন্নীত
করা
হয়।
বিশমাইলে
ছিল
তৃতীয়-চতুর্থ
শ্রেণীর
কর্মচারীদের
থাকার
জায়গা।
‘বি’-টাইপ
বাড়িগুলোর
পুব
পাশে
ছিল
টেলিফোন
এক্সচেঞ্জ
ও
মেথরপট্টি।
১
নম্বর
হলের
এক্সটেনশনের
পুব
বরাবর
একটা
ঘরে
ছিল
অগ্রণী
ব্যাংক।
একই
দালানের
পুব
প্রান্তের
ছোট্ট
কামরায়
ছিল
সীমিত
সেবার
জন্য
বাংলাদেশ
ডাক
বিভাগের
একটি
শাখা
অফিস।
তার
দক্ষিণে
আরেকটা
একতলা
ঘরে
ছিল
ইঞ্জিনিয়ারদের
অফিস
কমপ্লেক্স,
তার
দক্ষিণে
এ
রকমই
আরেকটা
একতলা
দালান
ব্যবহূত
হতো
রেজিস্ট্রার,
ডেপুটি
রেজিস্ট্রারসহ
সব
প্রশাসনিক
কার্যালয়
হিসেবে।
উপাচার্যের
বাসা
ও
মূল
অফিস
ছিল
ঢাকায়—ধানমন্ডি
২
নম্বর
সড়কে।
ক্যাম্পাসে
তার
আরেকটা
কার্যালয়
করা
হয়েছিল
ক্লাসরুম
ভবনের
ঈশান
কোণে।
ছাত্রদের
কমনরুম,
টিভিরুম
ও
নামাজের
ঘর
ছিল
১
নম্বর
হলে—ডাইনিং
রুমের
উপরতলায়।
হলের
এক্সটেনশনের
উত্তর
দিকে
ছিল
পরপর
দুটি
ঘর,
প্রথমটায়
ছিল
‘জাকসু’ কর্মকর্তাদের
অফিস
এবং
খেলাধুলার
সাজসরঞ্জামসহ
ফিজিক্যাল
ডাইরেক্টরেট।
পরেরটায়
ছিল
ডাক্তারের
অফিস,
ক্লিনিক
ও
একটা
ছোট্ট
ড্রাগ
স্টোর।
মেডিকেল
কমপ্লেক্সের
সামনে
উত্তর
দিকে
ছিল
খুব
সুন্দর
একটা
তিন
কোনা
ফুলের
বাগান।
সে
সময়
ক্যাম্পাসের
মধ্যে
এটাই
ছিল
সবচেয়ে
বড়
এবং
সাজানো
গোছানো
ফুলবাগান।
বিশ্ববিদ্যালয়ের
পেশাদার
মালিরা
সর্বক্ষণ
এ
বাগিচার
পরিচর্যায়
ব্যস্ত
থাকতেন।
আগাছাবিহীন
বাগানের
ঘাস
যেন
পারস্যের
সবুজ
গালিচা।
বসন্তের
বাতাসে
যখন
লতাপাতা-ফুল
গাছ
দোল
খেত,
মনে
হতো
যেন
ফোটা
ফুলগুলো
চোখ
তুলে
চেয়ে
আছে,
তারা
একযোগে
কিছু
বলতে
চায়।
এটা
ছিল
আমাদের
‘নন্দন কানন’,
কিন্তু
এখানে
গানবাজনা
কিংবা
প্রেম-ভালোবাসা
বিনিময়ের
কোনো
সুযোগ
ছিল
না।
বাগানটির
সব
দিকে
সুদৃশ্য
ও
মজবুত
বাঁশের
বেড়া
থাকায়
ভেতরে
ঘাসে
বসে
আমরা
ফুলের
মেলায়
রঙ-বেরঙের
প্রজাপতি
আর
মৌমাছির
গুঞ্জন
শুনতে
পেতাম
না।
আমাদের
নন্দন
কাননে
উন্মুক্ত
প্রবেশাধিকার
না
থাকায়
তরুণ
প্রেমিক-প্রেমিকাদের
জন্য
নীরস
কাঁঠালতলা
ছাড়া
আর
কোনো
নিরিবিলি
জায়গাও
ছিল
না।
ক্লাসরুম
ভবনের
একটা
রুমে
ছিল
শিক্ষক
ও
অফিসারদের
ক্লাব।
আরেকটা
বড়
রুমে
ছিল
একটি
অস্থায়ী
লাইব্রেরি।
হল
ক্যান্টিনের
পশ্চিম
পাশে
ছিল
একটা
ছোট্ট
ঘর,
ওখানে
ছিল
‘বাসু’র
কনভেনিয়েন্স
স্টোর
এবং
তার
উল্টো
দিকে
ছিল
একটি
লন্ড্রি।
বাসুর
দোকানের
দরজার
দুদিকে
সবসময়
দুটি
জিনিস
ঝুলে
থাকত।
একদিকে
একটি
কাঁচা-পাকা
সবরি
কলার
ছড়ি,
আরেকদিকে
বিড়ি-সিগারেটে
আগুন
ধরানোর
জন্য
জ্বলন্ত
দড়ি।
বাসুকে
একদিন
জিজ্ঞেস
করেছিলাম,
কলা
তো
তুমি
পয়সার
বিনিময়ে
বেচো,
আগুন
তো
কেউ
কিনে
না,
দড়িটা
পোড়াচ্ছ
কেন?
উত্তরে
বাসু
কোনো
কথা
বলেনি,
দিয়েছিল
গালভরা
একরাশ
হাসি।
এ
হাসির
অর্থ
আজও
আমি
উদ্ধার
করতে
পারিনি।
পানি
সরবরাহের
জন্য
একটা
গভীর
নলকূপ,
আর
তার
অপারেটর
থাকতেন
ওই
দূরে,
দক্ষিণ
ক্যাম্পাসে
বটগাছের
তলে।
আমরা
যখন
ভর্তি
হই
তখন
২
নম্বর
হলের
(এখনকার মীর
মশাররফ
হোসেন
হল)
কাজ
চলছে।
আল-বেরুনী
হলসংলগ্ন
খেলার
মাঠটা
শুরু
থেকেই
ছিল।
ব্যস,
তখন
বিশ্ববিদ্যালয়ের
দালানকোঠার
বেশি
আর
কিছুই
ছিল
না।
এই
যে
এত
সামান্য
সুযোগ-সুবিধা
নিয়ে
আমাদের
জীবনের
অতিগুরুত্বপূর্ণ
অধ্যায়ের
সূচনা
হলো,
তাতে
আমাদের
অসুবিধা
হতো
কিন্তু
কোনো
দুঃখ
ছিল
না,
আফসোসও
হতো
না।
এ
ব্যাপারে
অধ্যাপক
আবুল
ফজলের
একটি
তত্ত্ব
আছে,
সে
গল্প
পরে
হবে।
যেসব
স্থাপনার
কথা
বললাম,
তাদেরকে
যুক্ত
করেছিল
লাল
ইট
বিছানো
রাস্তা।
রাস্তার
দুই
পাশে
লাগানো
হয়েছিল
অ্যাকাশিয়া
গাছ
ও
কিছু
শাল
গাছ।
তবে
বিশমাইল
থেকে
মীর
মশাররফ
হোসেন
হল
পর্যন্ত
উত্তর-দক্ষিণ
বরাবর
ক্যাম্পাসের
মূল
সড়ক
ছিল
এর
ব্যতিক্রম।
এর
একটা
বড়
অংশ
ছিল
অসম্পূর্ণ
এবং
কাঁচা।
দক্ষিণ
দিকের
অংশ,
অর্থাৎ
মীর
মোশাররফ
হোসেন
হলের
নিকটবর্তী
প্রায়
১/৪
মাইল
পথ।
সে
অংশে
তখনো
ইট-পাথর
কিছুই
পড়েনি।
শুধু
কি
তাই?
ওই
কাঁচা
রাস্তার
দুই
পাশে
ছিল
লম্বা
ঘাস,
আগাছা
ও
কাঁটাযুক্ত
নানা
জাতের
জংলি
গাছপালায়
ভরা
ঘন
বন।
দিনের
বেলায়ও
একা
সে
পথ
পার
হতে
রীতিমতো
গা
ছমছম
করত!
রাতের
বেলা
শিয়াল
ডাকত
ওখান
থেকেই।
১৯৭০-এর
গোড়ার
দিকে
জাবির
পরিবহন
ব্যবস্থা
ছিল
খুবই
দুর্বল।
লোক
যাতায়াত
ও
মালসামান
টানার
জন্য
গোটা
বিশ্ববিদ্যালয়ে
গাড়ি
ছিল
মাত্র
পাঁচখানা—উপাচার্যের
প্রাইভেট
কার,
সিনিয়র
প্রফেসরদের
ঢাকা
থেকে
আনা-নেয়ার
জন্য
একখানা
বিস্কিট
রঙের
পুরনো
মাইক্রোবাস
এবং
দুখানা
বাস
ও
একখানা
পিকআপ।
বাসের
মধ্যে
একটি
তৈরি
করা
হয়েছিল
ট্রাকের
ইঞ্জিনের
সঙ্গে
বডি
যোগ
করে।
এটা
ছিল
নীল
ও
হালকা
হলুদ
রঙের।
আরেকখানা
ছিল
গাঢ়
সবুজ
ও
বেশ
লম্বা।
নামটা
কে
দিয়েছিল
জানি
না,
তবে
সবুজ
বাসের
‘নিক নেম’
ছিল
‘বোয়িং’।
বোয়িংয়ের
দুই
সাইডে
সাদা
কালির
বড়
বড়
হরফে
লেখা
ছিল
‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়’।
দিনে
তিন-চারবার
রাজধানীর
রাজপথে
চলার
মাধ্যমে
এ
বোয়িং
ঢাকাসহ
সারা
দেশে
জানান
দেয়
জাবির
অস্তিত্বের
কথা।
দেশব্যাপী
নতুন
এ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
নাম
ছড়ানোয়
বোয়িংয়ের
চেয়ে
কার্যকর
ভূমিকা
আর
কেউ
রাখতে
পেরেছিল
বলে
আমার
মনে
হয়
না।
দুই
বাসের
জন্য
দুজন
চালকসহ
পাঁচ-ছয়জন
কন্ডাক্টর-হেলপার
ছিলেন।
তার
মধ্যে
দুজনের
নাম
আজও
আমার
মনে
আছে—আজিজ
ও
চুন্নু।
আজিজ
ছিলেন
ছয়
ফুট
লম্বা
মোটা-তাজা
এবং
খুব
রসিক
স্বভাবের
মানুষ।
ঢাকা
থেকে
আসার
পথে
সাভার
থানা
স্টপ
ছাড়ার
পর
পরই
তিনি
সুর
করে
বলতে
থাকতেন,
‘সাভাইরা বাজার,
সাভাইরা
বাজার...’।
আজিজের
মুখে
সাভাইরা
বাজার,
সাভাইরা
বাজার
শুনতে
কেন
জানি
আমার
খুব
মজা
লাগত!
বাস
কখন
চলবে,
কখন
আস্তে
যাবে
এবং
কখন
থামবে
তা
বোঝাবার
জন্য
‘মোর্স টেলিগ্রাফি’র
মতো
বাসের
ড্রাইভার
ও
হেলপারের
মধ্যে
একটি
সাংকেতিক
ভাষা
চালু
ছিল।
সেটা
বুঝতে
আমার
বেশ
কিছুদিন
সময়
লেগেছিল।
বাসের
গায়ে
ধপাধপ
অনেকগুলো
থাপ্পড়
মারার
মানে
বাস
চলবে,
যখন
থাপ্পড়ের
ফ্রিকোয়েন্সি
কমতে
থাকবে
তখন
আস্তে
যাবে,
আর
জোরসে
একটা
থাপ্পড়
মারার
মানে
বাস
থামবে।
আমাদের
হলজীবনে
খাওয়া-দাওয়াটাও
ছিল
বেশ
মজাদার।
সকালবেলা
ক্যান্টিনে
যেতাম
নাশতা
খেতে।
নাশতার
মেনু
হররোজ
একই,
স্ট্যান্ডার্ড
অর্ডার
ছিল
দুখানা
পরোটা,
তার
সঙ্গে
চায়ের
পিরিচে
এক
পিরিচ
আলু-পটোল
ভাজি
অথবা
বুটের
ডাল।
ডিমের
অমলেট
ও
পোচও
(ফ্রায়েড এগ)
পাওয়া
যেত,
কিন্তু
দামের
কারণে
সেটা
আমরা
হামেশা
খেতে
পারতাম
না।
স্বাদে
নতুনত্ব
আনার
জন্য
বড়জোর
সপ্তাহে
একদিন
ডিম
কপালে
জুটত।
আজীবন
ডিম
আমার
অত্যন্ত
প্রিয়
খাবার।
যখন
দরকার
ছিল,
খেতে
পাইনি।
এখন
সামর্থ্য
আছে
কিন্তু
বাইপাস
সার্জারির
পর
ইদানীং
বউ-ছেলেমেয়ে
ডিমের
অনুমতি
দেয়
না।
ভেবে
রেখেছি
বেহেশতে
গেলে
মহান
আল্লাহর
কাছে
দৈনিক
অন্তত
একটা
করে
ডিম
চাইব।
সে
ডিম
অনন্তকাল
ধরে
একেকদিন
একেক
তরিকায়
তৈরি
হয়ে
একেক
আঙ্গিকে
আমার
সামনে
এসে
হাজির
হবে,
ইনশা
আল্লাহ।
গরিবদের
সাধ্য
না
থাকলেও
বুদ্ধি
ছিল,
আমাদেরই
কোনো
এক
বন্ধু
একসময়
নাশতার
টেবিলে
নতুন
এক
আইটেম
আবিষ্কার
করে
বসল।
পরোটার
সঙ্গে
দুই
চামচ
করে
ভাজি
অথবা
বুটের
ডালের
একটা
নিতে
হতো।
সে
একদিন
বলল,
‘আমাকে এক
চামচ
ভাজি
আর
এক
চামচ
ডাল
মিশিয়ে
দে।’
আস্তে
আস্তে
ক্যান্টিনে
‘ডাল-ভাজির’
মিশেল
বেশ
জনপ্রিয়
হয়ে
উঠল।
পরবর্তী
পর্যায়ে
এই
মিশেলের
নাম
হয়ে
গেল
‘মিকচার’।
এভাবে
পরোটার
সঙ্গে
দুইয়ের
পরিবর্তে
ক্যান্টিনে
পাওয়া
যেত
তিন
পদ—ডাল,
ভাজি
ও
মিকচার।
নাশতার
সময়
চা
কেনাবেচা
হতো
কিনা
মনে
করতে
পারছি
না,
তবে
অন্য
সময়
চা
শুধু
পাওয়াই
যেত
না,
সে
চা
ছিল
খুব
সুস্বাদু!
অনেকক্ষণ
জ্বাল
দেয়া
লিকারে
ঘন
দুধ
ও
চিনিতে
তৈরি
হতো
অপূর্ব
মজাদার
চা!
এছাড়া
দুপুর
১২টা
থেকে
রাত
৯টা-১০টা
অবধি
আলুর
চপ,
শিঙ্গাড়া,
ভাত-তরকারি
ইত্যাদিও
পাওয়া
যেত।
এ
লেখা
আগে
লিখলে
সেদিনকার
ক্যান্টিনে
বিবিধ
খাদ্য-পানীয়ের
দাম
কেমন
ছিল
তা
ঠিক
ঠিক
বলে
দিতে
পারতাম।
এখন
স্মরণশক্তিকে
দোষ
দিয়ে
আর
লাভ
কী,
বয়স
তো
কম
হলো
না।
(চলবে)
আবু এন
এম ওয়াহিদ: অধ্যাপক,
অর্থনীতি
বিভাগ,
টেনেসি
স্টেট
ইউনিভার্সিটি,
যুক্তরাষ্ট্র;
এডিটর,
জার্নাল
অব
ডেভেলপিং
এরিয়াজ