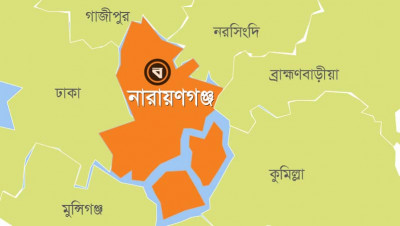বেশকিছু বছর ধরে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে অনেক অভিযোগ শোনা যায়। এর মধ্যে একটি অভিযোগ হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পরও শিক্ষার্থীরা দক্ষতার সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোয় কাজ করতে পারছে না। এক্ষেত্রে দুই ধরনের মত আছে: ১. বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ গবেষণা করে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করা, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মী জোগান দেয়া নয়; ২. বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যাতে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের পাঁচমিশালি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দুটির (প্রশিক্ষণ দেয়া ও গবেষণা করা) একটি কাজও যে পুরোপুরি হচ্ছে না, তা নিয়ে সবাই প্রায় একমত! এই গেল মাত্র একটি অভিযোগ। এছাড়া সেশন জট, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠদান পদ্ধতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই। সমস্যা যেহেতু রয়েছে, তার সমাধান তো চাই। যেহেতু ইউরোপ-আমেরিকার উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে গিয়েও পা পিছলে যাচ্ছে বারবার, সেহেতু ইউরোপ-আমেরিকার সমাধানের দিকে না তাকিয়ে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখা যাক যদি একটি সমস্যার সমাধানও পাওয়া যায়, তাতে মন্দ কী! ভারতে বিভিন্ন শাসকের উত্থান-পতন হয়েছে বারবার। আবার ভৌগোলিক নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও দুটি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিজিতদের সংস্কৃতি অনেক বছর ধরে টিকে থাকা জয়ী শাসকদের সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি ধরে নিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর লক্ষ রেখে লেখার বাকি অংশটুকু এগিয়ে নিয়েছি। তখনকার সময়ে শিক্ষার স্তরবিন্যাস (প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা) এখনকার মতো পুরোপুরি আলাদাভাবে না থাকায় সার্বিক দিকটাই বিবেচনায় নিচ্ছি।
প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে সব ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত আছে শাসক বা শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন। শাসকের পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাসকের অনুসরণ করা ধর্ম ও শাসনকার্য পরিচালনার ভাষা। আর উভয় পরিবর্তনই জীবিকা নির্বাহের উপায়কেও প্রভাবিত করেছে।
উল্লিখিত কালগুলোয় মূলত চারটি বিষয়ে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়: ১. পড়ার বিষয়বস্তু ও এর উদ্দেশ্য; ২. পড়ানোর স্থান; ৩. পড়ানোর ও শেখার পদ্ধতি এবং ৪. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পদ্ধতি।
১৫০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
এ সময় বৈদিক যুগ হিসেবে পরিচিত (সময় নিয়ে মতভেদ রয়েছে)। তখন শিক্ষাদান হতো গুরুকুলে। শিষ্যরা নিজের বাড়ি ছেড়ে শিক্ষা গ্রহণের সময়টুকু গুরুগৃহে কাটাত। আর শিক্ষাগ্রহণ শেষ করে বাড়ি ফিরত। গুরুকুলে দেহ ও মন সতেজ রাখার জন্য কোলাহলমুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান করা হতো। শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার সার্বিক দায়িত্ব ছিল গুরুর ওপর। একইভাবে গুরুগৃহের দেখাশোনা করার দায়িত্ব ছিল শিক্ষার্থীদের ওপর। শিক্ষার্থীদের কোনো বেতন দিতে হতো না। তবে শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে গুরুদক্ষিণা দিতে হতো। সমাজে গুরুদের বিশেষ স্থান থাকার ফলে তাদের জমি থাকত করমুক্ত। রাজা এবং আর্থিকভাবে ধনী ব্যক্তিরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে পাঠ্যক্রম বা অন্য কোনো বিষয়ে শাসকরা কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শারীরিক ও মানসিক গঠন বলবান করা, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতার জগৎ উন্মুক্ত করা।
গুরুকুলে পাঠদান এবং প্রশিক্ষণ দুটি পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেয়া হতো। দর্শনের মতো তত্ত্বীয় বিষয় থেকে শুরু করে কলাবিদ্যা বা হস্তশিল্প শিখে জীবিকা নির্বাহ করার মতো শিক্ষা উভয়ই দেয়া হতো। পাঠদান হতো মূলত মৌখিকভাবেই। পাঠদানের ভাষা ছিল সংস্কৃত। শেখার পদ্ধতি তিনটি স্তরে ভাগ করা ছিল: ১. শ্রবণ, ২. মনন ও ৩. নিদিধ্যাসন। গুরুর দেয়া পাঠ মনোযোগ সহকারে শোনা, সেগুলোর অর্থ নিজ বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা এবং ধ্যান করা। যেহেতু লিখন ব্যবস্থা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল না, মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে শিক্ষার্থীরা যা শুনত, তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করত। তবে গুরু শুধু একনাগাড়ে পাঠদানই করে যেতেন না, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, উদাহরণ দেয়া, রূপকের ব্যবহারও করতেন।
আজকের মতো কাঠামোবদ্ধ লিখিত পরীক্ষা, ফলাফল, ডিগ্রি, সনদ ইত্যাদি ছিল না। আজকের মতো ডিগ্রি দেয়ার প্রথা না থাকলেও যারা একটি, দুটি, তিনটি ও চারটি বেদ পাঠ সম্পন্ন করত, তাদের যথাক্রমে ষেষ্টক, বসু, রুদ্র ও অদিয় বলা হতো। কেউ ভালোভাবে শিখেছে কিনা, তা নির্ণয় হতো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। ফলাফলের ক্রমধারা পদ্ধতি না থাকায় কে এগিয়ে গেল আর কে পিছিয়ে গেল, সে ব্যাপারে মানসিক কোনো চাপ কাউকে জেঁকে ধরত না।
গুরুকুল আজকের যুগের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয় কোনোটির মধ্যেই আলাদাভাবে ভাগ করা যায় না। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা এক সূত্রেই গাঁথা ছিল।
৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে (মতান্তরে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) স্থাপিত হয় তক্ষশীলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বর্তমানে যে হিসাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়, সে রকম কিছু (ডিগ্রি ও সনদ প্রদান, কেন্দ্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থা) না থাকায় তক্ষশীলাকে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে চান না। এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা হোক বা না হোক, তক্ষশীলা নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষকরা তাদের নিজস্ব তত্ত্ব শিক্ষার্থীদের পড়াতেন ও আলোচনা করতেন। হাল আমলের গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় না হলেও তক্ষশীলায় গবেষণা হতো। গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রও ছিল। দেশ-বিদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমাগম ঘটেছিল সেখানে। পরিব্রাজকরাও শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হতেন।
গুরুকুলের পাশাপাশি অনেক গুরু ও জ্যেষ্ঠ শিষ্য মিলে পরিষদ ও সভা বসার প্রচলনও ছিল। তক্ষশীলা সম্ভবত পরিষদের আরেক রূপ। তবে এই প্রথম বোধহয় অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে একসঙ্গে পাঠদান ও পাঠগ্রহণের জন্য কক্ষ করে দেয়া হয়েছিল। সেখানে শিক্ষকদের বাসস্থানও ছিল। দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির পাশাপাশি কলাবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন ছিল।
ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ
এ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। এছাড়া এ সময়ে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদেরও গোড়াপত্তন হয়। ৫০০ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে নালন্দা মহাবিহার। তক্ষশীলার সঙ্গে নালন্দার পার্থক্য ঘটে পরিচালনায়। তক্ষশীলা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে নালন্দার কেন্দ্রীয় পরিচালক ছিলেন, আর তা শিক্ষকদের মধ্যে থেকেই। আর্য শাসনামলের শেষ দিকে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বাড়তে থাকে। পাঠদানের ভাষা সংস্কৃত হওয়ায় সবাই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত না। এছাড়া অনার্যদের শিক্ষা দেয়া হতো না। ফলে বৌদ্ধরা পালি ভাষায় শিক্ষাদান শুরু করে। প্রচলন হয় বৌদ্ধ মঠের। মঠে মূলত বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হতো এবং শুধু বৌদ্ধরাই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারত। বৌদ্ধ দর্শন ছাড়াও হেতু বিদ্যা (ইন্ডাক্টিভ লজিক), ব্যাকরণ, হস্তশিল্প প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠদান ও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। গুরুকুলের মতো সেখানেও শিক্ষাগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মঠেই থাকতে হতো। কেউ কেউ শিক্ষাগ্রহণ শেষে বাড়ি ফিরে যেত। আবার কেউ কেউ সন্ন্যাস নিয়ে এখানেই থাকত। আর্য ও বৌদ্ধদের শিক্ষাদান ও শেখার পদ্ধতির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রেও মেয়েরা মঠে পড়তে পারত না। ফলে তারা বাড়িতেই শিক্ষাগ্রহণ করত।
১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭
সুলতানি আমলের সঙ্গে এ অঞ্চলে শুরু হয় মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন। কালের পরিবর্তনে প্রায় প্রতি গ্রামে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠায় শিক্ষার্থীদের বাসা ছেড়ে সেসব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে থাকতে হতো না। বিষয়বস্তু হিসেবে কোরআন, হাদিস, ইসলাম নির্দেশিত আইন ইত্যাদি ছাড়াও ব্যাকরণ, কবিতা পড়ানো হতো। কলাবিদ্যা, আগের দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বাদ দেয়া হয়। তবে মোগল আমলে এগুলো আবার পাঠ্যক্রমে যুক্ত হয়। যেহেতু পার্সি ভাষায় শাসন ব্যবস্থা চলত, মুসলিমদের পাশাপাশি অন্যরাও সে ভাষা শিখতে শুরু করে। মূলত শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকতে এ ভাষা শেখার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে মিল ছিল এবং শাসককেন্দ্রিক কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরে ছিল। যেমন আকবর বলেছিলেন, শিশুরা যাতে সবকিছু নিজে নিজে শিখতে পারে সেজন্য যত্ন নেয়া হবে, তবে শিক্ষক তাদের অল্প সাহায্য করতে পারেন। মাদ্রাসাগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বর্তমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করা হলেও কিছু মাদ্রাসার শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গেও তুলনা করা হয়।
এ সময়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু অমিল দেখতে পাওয়া যায়: ১. বাসা থেকে দূরে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো না; ২. কেন্দ্রীয় কিছু প্রভাব মাদ্রাসা, মক্তবের ওপর ছিল; ৩. মৌখিক পাঠদান, আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষার আদান-প্রদান হতো। নিদিদ্ধাসন পদ্ধতির কোনো আভাস পাওয়া যায় না; ৪. প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে মিল ছিল। তবে শুধু যে পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে অমিল ছিল তা নয়, মিলও ছিল। যেমন ১. প্রতি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ শুরু হতো (উপনয়ন, প্রব্জা, বিসমিল্লাহ ইত্যাদি); ২. শিক্ষককে তার ভরণ-পোষণের জন্য চিন্তা করতে হতো না। বিত্তশালী ব্যক্তি ও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাই এজন্য যথেষ্ট ছিল এবং ৩. পরিব্রাজককে জ্ঞানের আধার বলে বিবেচনা করা হতো।
এখন পর্যন্ত আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি: ১. এমন বিষয়ে পড়া, যেগুলো সরাসরি জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করবে ২. বিভিন্ন সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান দেয়া যায়, এমন বিষয় পড়া। এগুলোর আবার অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহারিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করেছে। তবে সরাসরি জীবিকা নির্বাহের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে হয় না।
১৭৫৭ সালের পরবর্তী সময়
ইংরেজ শাসনামলে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্ট ধর্মের মিশনারিরা শিক্ষার বিস্তার শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে সরকারি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ইংরেজদের সঙ্গে এল ইংরেজি ভাষা। মিশনারিরা শহরাঞ্চলে ইংরেজি ও গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা প্রদান শুরু করে। গুরুকুল, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান করমুক্ত জমির ওপর ছিল। মিশনারি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং সেসব জমির ওপর কর বসানো শুরু করে ইংরেজরা। কর দিতে না পারলে জমি অধিগ্রহণ করত। ইংরেজি ভাষায় তত্কালীন সরকারি দপ্তরগুলো পরিচালিত হওয়ায় সরকারি চাকরি পেতে এবং দোভাষী হিসেবে কাজ করতে অন্যরা ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবই ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে ওঠে। পড়া, লেখা ও পরীক্ষা দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় শেখা। ডিগ্রি প্রদান, সনদ প্রদান, কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা সবই এ সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল চাকরি করার জন্য মানুষ জোগান দেয়া। দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি যেগুলোর সঙ্গে চাকরি ক্ষেত্রের সরাসরি কোনো সংযোগ নেই, তারা সেগুলো পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দিয়ে দেয়। যুক্ত করে প্রকৌশল বিদ্যা। সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষা চালুর কথা শোনা গেলেও বাস্তবায়ন হয়েছিল তা ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে। আগে শিক্ষার্থীরা বিনা বেতনে পড়তে পারলেও এ সময়ে তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ বেতন দিতে হতো।
যাহোক, সবসময়ই দেখা যাচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহের একটি সম্পর্ক আছে। তবে গবেষণার সংযোগও দেখা গেছে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই। পরীক্ষা, ফলাফল, ডিগ্রি, সনদ না থাকায়ও তখন কোনো সমস্যা হয়নি।
ফিরে তাকাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু ক্ষেত্রের দিকে। বর্তমানের পাঠদানের পদ্ধতি শুধু মৌখিক নয়। সেটা লিখিত ও চিত্রিতও বটে। আর শেখার পদ্ধতি? শোনা/দেখা, লেখা, আর মনে রাখা। আমরা ঠিক এখানেই আটকে আছি। কিছু মনে রাখার জন্য আমাদের বর্তমান কৌশল হলো পড়া, লেখা, আর কিছুদিন পরপর সেগুলো আবার পড়া। অর্থাৎ স্বল্পকালীন স্মৃতিতে কোনো কিছু প্রবেশ করলেও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সেগুলো ধরে রাখা যাচ্ছে না। ছাপা বই, লিখিত পাঠদান পাওয়ার পর আমাদের মুখস্থ করার কাজটা কমে যাওয়ার বদলে যেন বেড়ে গেল। তথ্যগুলো হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না। এ অবস্থায় মনন ও নিদিধ্যাসন এক্ষেত্রে গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল। অথচ হলো উল্টো। শ্রেণীকক্ষে যদিও কেউ কেউ চিন্তা করার কথা বলেন, সেই চিন্তাটা কীভাবে করা হবে, সে বিষয়ে আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের কোনো পাঠ নেই। এ অবস্থায় যা-ই পড়ানো হোক না কেন, তেমন কোনো লাভ হবে না।
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার বিষয়গুলো কী কী? যে যে বিভাগে পড়ছে, সেই বিভাগের কিছু বিষয়, সাথে বাংলা, ইংরেজির একটি/দু’টি বিষয়, আর বিভাগের বিষয়গুলোর সাথে অন্য বিভাগের যেসব বিষয় পড়ার প্রয়োজন হতে পারে তা থেকে কিছু বিষয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগ আছে। সেগুলোও পাশ্চাত্যমুখী। বাকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্ভবত এই বিষয়কে কোন গুরুত্বই দেয় না। ফলে, পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্তি নেই। অথচ দর্শন মননের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।
বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হবে বা হবে না, তার অনেকখানি নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের উপায়ের ওপর। সম্ভবত বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর লক্ষ্যই হলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে চাকরি করা। চাকরিদাতারা আবার বেশির ভাগ চাকরিপ্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে সন্দিহান; নাখোশও বটে। ডিগ্রি, সনদ, ফলাফল কোনো কিছুই আর ঠিকমতো সংকেত দিতে পারছে না। পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন করা হয়, সেগুলোয় প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটে না। ফলে পুরো অবস্থাটাই নড়বড়ে হয়ে আছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়/বিভাগকেই ঠিক করে নিতে হবে তারা প্রশিক্ষণভিত্তিক শিক্ষা দেবে কিনা। একেক বিষয়ের প্রশিক্ষণ একেক রকম। যেহেতু একই সঙ্গে পাঠদান করা ও প্রায়োগিক বিষয় শেখানো একজন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না (যে কারণেই হোক), স্বল্পমেয়াদি একটি সমাধান হতে পারে সহকারী নিয়োগ করা এবং তাদের মাধ্যমে অন্যদের শেখানো। সহকারী নিয়োগ দেয়াও যদি সম্ভব না হয়, প্রতি শ্রেণীতেই কয়েকজন আগ্রহী শিক্ষার্থী থাকেন। তারা নিজেরাই কিছু প্রায়োগিক বিষয় শেখে। দলবদ্ধভাবে এ কাজগুলো করালে বাকিরাও কিছু শিখতে পারবে। এজন্য অবশ্য অন্যদেরও আগ্রহ থাকতে হবে। মানুষ কোনো বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারলে সে বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আগ্রহ তৈরির কাজটা পাঠদানকে আকর্ষণীয় করার মাধ্যমেই করতে হবে। বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিষয় শেখার কাজ সুবিধাজনক হতে পারে অনলাইন কোর্স থেকে। সব বিষয়ে অবশ্য সেটি সম্ভব নয়। তবে ই-লার্নিংয়ের কিছু সুবিধা আছে। প্রশ্নগুলোয় প্রাথমিক থেকে শুরু করে এর প্রায়োগিক বিষয় পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে কে কত মার্ক পেল না পেল, তা নিয়ে সার্টিফিকেটে কিছুই উল্লেখ থাকে না। অর্থাৎ ফলাফল মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। এখানে আবার পরীক্ষার জন্য কয়েক বছর আটকে থাকার (সেশন জ্যাম) সমস্যাও নেই। যখন ইচ্ছা তখনই পাঠ নেয়া যায়।
যাহোক, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখা বিষয় বারবার করা সম্ভব। তবে নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য তো গবেষণারও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পাঠদান, গবেষণা, প্রশিক্ষণ সবকিছুরই প্রয়োজন হবে। সুতরাং কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/বিভাগ কীভাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে চায়, সেটা তাকে আগেই নির্ধারণ করতে হবে। অনেক বছর পরে কেউ যদি এ সময়ের দিকে ফিরে তাকায় হয়তো দেখবে অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত উন্নতির শুরু হয়েছিল এ সময়েই। বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনার দিক থেকে পিছিয়ে আছে অনেকখানি। যদি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে স্বল্প সময়ে স্থানীয় সমাধান খুঁজেই এগিয়ে যেতে হবে। ঘুড়ি যেমন আকাশে উড়লেও তার সুতো আটকে থাকে নাটাইয়ের সঙ্গে, ইউরোপের প্রথম দিকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তেমনি জড়িয়ে ছিল চার্চের সঙ্গে। ইউরোপের ক্ষেত্রে সময় এগিয়ে গেলেও আমরা যেন ক্রমে উল্টো দিকে বয়ে চলেছি। আশ্চর্যজনকভাবে এই ক্ষুদ্র ভাইরাস আমাদের সবকিছু আবার ঢেলে সাজানোর সুযোগ করে দিয়েছে। পরিবর্তন যদি কিছু করতেই হয়, এখনই বোধহয় এর মুখ্য সময়।
সুস্মিতা দত্ত: গবেষক